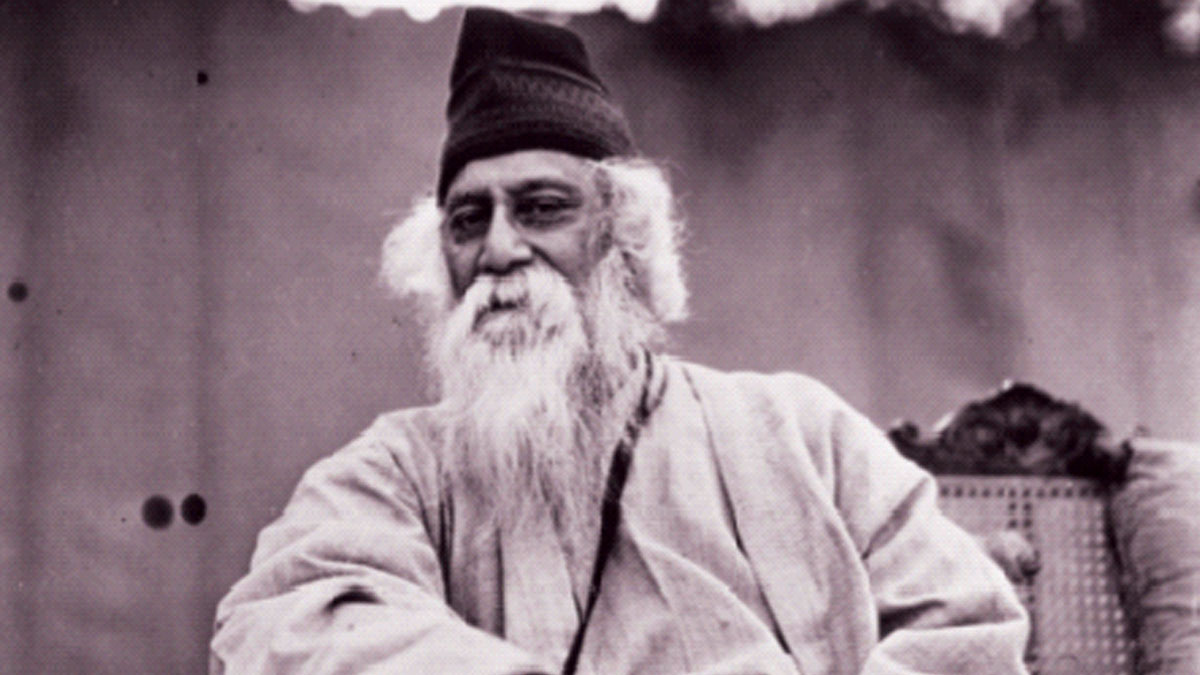সৈয়দ হাসমত জালাল: গত কয়েক বছর ধরে আমাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ‘জাতীয়তাবাদ’ বিষয়টিকে বহুল প্রচারিত হতে দেখা যাচ্ছে৷ কিন্ত্ত রবীন্দ্রনাথ এই ধরনের জাতীয়তাবাদের পক্ষে ছিলেন না৷ জাতীয়তাবাদকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্যে সবসময় অন্য কোনও রাষ্ট্র বা জাতিকে শত্রু মনে করা হয়ে থাকে৷ বিরোধী রাষ্ট্র বা জাতির প্রতি বিদ্বেষ প্রচারের মধ্যে দিয়েই জাতীয়তাবাদ আরও জোরালো হয়ে ওঠে এবং তা ক্রমশ উগ্র জাতীয়তাবাদের রূপ নেয়৷ রবীন্দ্রনাথ কখনোই তা সমর্থন করেননি৷
বস্তুত রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে জাতীয়তাবাদের লক্ষ্য হচ্ছে, দেশের জনপ্রিয় সার্বভৌমত্বকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া৷ জাতীয়তাবাদ এমন একটি ভাবাদর্শ যা একটি জাতি বা জাতি-রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ও ভক্তির উপর জোর দেয় এবং তা অন্যান্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠীস্বার্থকে ছাডি়য়ে যায়৷ ইতিহাসবিদ কার্লটন জে এইচ হায়েস বলেছেন, ‘Nationalism
consists of modern emotional fusion and exaggeration of two very old phenomenon Nationality and Patriotism.’
Advertisement
এই সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ বা দেশপ্রেমে বিশ্বাস করতেন না রবীন্দ্রনাথ৷ ১৯০৪ সালে ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর ‘দেশের কথা’ প্রবন্ধে খুব স্পষ্টভাবেই তিনি এ বিষয়ে তাঁর ভাবনার কথা জানিয়েছেন— ‘স্বাদেশিকতার ভাবখানা এই যে, স্বদেশের ঊর্ধ্বে আর কিছুকেই স্বীকার না করা৷… যেখানে স্বদেশের স্বার্থ লইয়া কথা সেখানে সত্য, দয়া, মঙ্গল সমস্ত নিচে তলাইয়া যায়৷ স্বদেশীয় স্বার্থপরতাকে ধর্মের স্থান দিলে যে ব্যাপারটা হয় তাহাই প্যাট্রিয়টিজম শব্দের বাচ্য হইয়াছে৷’
Advertisement
যে আত্মীয়-সম্পর্কের বন্ধনকে ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তি বলে মনে করতেন রবীন্দ্রনাথ, সেই আত্মীয়তার বিকাশই ছিল রবীন্দ্রনাথের কাছে ধর্ম৷ তাই তিনি মানুষকে এক সূত্রে বাঁধার কথা বলেছেন, বলেছেন দেশের হূদয়কে এক করার কথা৷
‘দেশের কথা’তেই তিনি বলেছেন, ‘ন্যাশনালত্বের সুবিধার খাতিরে মনুষ্যত্বকে পদে পদে বিকাইয়া দেওয়া, মিথ্যাকে আশ্রয় করা, ছলনাকে আশ্রয় করা, নির্দয়তাকে আশ্রয় করা প্রকৃতপক্ষে ঠকা৷… মনুষ্যত্বের মঙ্গলকে যদি ন্যাশনালত্ব বিকাইয়া দেয়, তবে ন্যাশনালত্বের মঙ্গলকেও একদিন ব্যক্তিগত স্বার্থ বিকাইতে আরম্ভ করিবে৷’ কী আশ্চর্য অমোঘ এই কথা৷ আমাদের দেশের আজকের পরিপ্রেক্ষিতে কথাগুলি প্রবল সত্য ও বাস্তব হয়ে উঠেছে৷ বিভিন্ন ‘মিথ্যা’, ‘ছলনা’ ও ‘নির্দয়তা’কে আশ্রয় করে মনুষ্যত্বের অবমাননা ঘটানো হচ্ছে এবং জাতির মঙ্গল বিক্রি হয়ে যাচ্ছে ‘ব্যক্তিগত স্বার্থে’৷
১৯০৮ সালে আনন্দমোহন বসুকে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ‘যদি প্যাট্রিয়টিজমকেই চরম করে তুলি তবে সে প্যাট্রিয়টিজম একটা ঘোরতর অন্ধতা; আমাদের দেশের হাঁচি টিকটিকি, ওলাবিবি ঘেঁটুপূজার মতই অন্ধতা৷ প্রভেদ এই যে, এই অন্ধতার উপর সভ্যদেশের ছাপ মারা আছে— এই অন্ধতা বড় নাম ধরে আমাদের বড় রকম করে ভোলাতে পারে৷’ তিনি আরও লিখেছেন, ‘দৈশিকতা (প্যাট্রিয়টিজম) আমাদের চরম আশ্রয় দিতে পারবে না, আমি মনুষ্যত্বকে বরণ করে নিয়েছি— আমি হীরের মূল্যে কাচ কিনব না— দৈশিকতা যে মনুষ্যত্বকে লঙ্ঘন করবে এত আমি জীবনে ঘটতে দিতে পারব না৷’
রবীন্দ্রনাথের দু’টি উপন্যাসের কথা এখানে উল্লেখ করতেই হয়৷ ১৯১০ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ‘গোরা’ ও ১৯১৬ সালে প্রকাশিত ‘ঘরে বাইরে’৷ ‘গোরা’ উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র গোরার মধ্যে দিয়ে তিনি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের হিন্দুত্ববাদী সংস্কার থেকে বিশ্বমানবতায় উত্তরণ দেখিয়েছেন৷ জাতীয়তাবাদ শব্দটি কেবল হিন্দুত্বের আতিশয্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষের মানবিক বন্ধনই যে দেশ গঠনের মূল ভিত্তি, এ কথাই বলেছেন তিনি৷ তাই এই উপন্যাসে দেখতে পাই, গোরা যখন তার প্রকৃত জন্মপরিচয় জানতে পারে যে, সে আসলে আইরিশ বাবা-মায়ের সন্তান, তখন সমস্ত দ্বিধা সংশয় ঝেডে় ফেলে সে বলতে পারে, ‘আজ আমি ভারতবর্ষীয়৷ আমার মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই৷ আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন৷’ জাতি-ধর্ম-বর্ণের উপরে তিনি তুলে ধরেছেন মানবতা ও বিশ্বমানবধর্মকে৷
‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসটি এই সময় পড়লে সন্দীপ চরিত্রের কথা শুনে চমকে উঠতে হয়৷ এ তো আজকের জাতীয়তাবাদী কোনও রাজনৈতিক নেতার চরিত্র, যারা ধর্মীয় বিদ্বেষ ছডি়য়ে শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাতেও দ্বিধা বোধ করে না৷ এই উপন্যাসের অন্য চরিত্র নিখিলেশের মতে, তারা দেশকে শুধুমাত্র দেশ হিসেবে জেনে সেবা করতে উৎসাহ পায় না৷ তারা ‘চিৎকার করে মা বলে, দেবী বলে মন্ত্র পডে়, যাদের কেবলই সম্মোহনের দরকার হয়, তাদের সেই ভালোবাসা দেশের প্রতি তেমন নয়, যত নেশার প্রতি৷’ এই নেশা রাষ্ট্রক্ষমতার নেশা, ধর্মীয় আফিমের নেশা৷ নিখিলেশ আরও বলে, ‘ভয়ের শাসনের সীমা কোন পর্যন্ত, সেইটের দ্বারাই দেশের মানুষ কতটা স্বাধীন, জানা যায়৷… মানুষ নিজে কী কাপড় পরবে, কোন দোকান থেকে কিনবে, কী খাবে, কার সঙ্গে বসে খাবে, এ-ও যদি ভয়ের শাসনে বাঁধা হয়, তাহলে মানুষের ইচ্ছাকে একেবারে অস্বীকার করা হয়৷ সেটাই হল মানুষকে মনুষ্যত্ব থেকে বঞ্চিত করা৷’ নিখিলেশের এই কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে এই সময় আমাদের দেশে৷ কোনও কোনও সম্প্রদায়ের মানুষের খাদ্য ও পোশাক-আশাকের জন্য তাদের শুধু বিপন্ন হতে হয় তা-ই নয়, তাদের মৃতু্যর ঘটনাও ঘটেছে৷
আবার দেখতে পাচ্ছি, ১৯২১ সালে জগদানন্দ রায়কে এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন, ‘Nationalism হচ্ছে একটি ভৌগোলিক অপদেবতা, পৃথিবী সেই ভূতের উপদ্রবে কম্পান্বিত– সেই ভূত ছাড়াবার দিন এসেছে৷’ ওই একই সালে সি এফ এন্ড্রুজকে লেখা চিঠিতে তিনি বলছেন, ‘I love India, but my India is an idea and not a geographical expression. Therefore, I am not a patriot. I shall ever seek my compatriots all over the world.’ রবীন্দ্রনাথের কাছে দেশপ্রেম আসলে মানবপ্রেম এবং তিনি নির্দ্বিধায় ঘোষণা করেছেন বিশ্বভ্রাতৃত্বের কথা৷
মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয় সম্বন্ধ স্থাপনই চিরকাল ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান চেষ্টা ছিল, এই ছিল রবীন্দ্রনাথের ভাবনা৷ তাই তিনি সমাজের সঙ্গে সমাজের, পল্লীর সঙ্গে পল্লীর, সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্প্রদায়ের, দেশের সঙ্গে দেশের হূদয় একই সূত্রে বাঁধা থাকবে বলে বিশ্বাস করতেন৷ তাঁর এই ভাবনাকে তিনি বাস্তবায়িত করতে সচেষ্টও হয়েছিলেন৷ শ্রীনিকেতনে, শিলাইদহে, সাহজাদপুরে তার নিদর্শন আমরা দেখেছি৷ স্বনির্ভর পল্লিসমাজ গঠন, জীবিকাভিত্তিক সমবায়নীতি, কুটিরশিল্প ও ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা ইত্যাদি প্রকল্পগুলি তার অন্যতম৷ তিনি মনে করতেন, ‘প্রয়োজনের সম্বন্ধকে আমরা হূদয়ের সম্বন্ধ দ্বারা শোধন করিয়া লইয়া তবে ব্যবহার করিতে পারি৷’
‘কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা/ দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে, সমুদ্রে হল হারা’— এটাই ভারতবর্ষের প্রকৃত সত্তা, প্রকৃত ইতিহাস৷ চিরকালই সহনশীলতা, তিতিক্ষা, ধৈর্য এসবই ছিল ভারতবর্ষের অন্তরের ধন৷ তাই দেশের মানুষকে, তাদের হূদয়কে এক করার ক্ষেত্রে তিনি যে-কোনোরকম বলপ্রয়োগ, হিংসা ও আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে ছিলেন৷ তাই ‘এক দেশ, এক জাতি, এক ধর্ম’ জাতীয় যে-কোনও কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে ছিল তাঁর অবস্থান৷ ভারতবর্ষের বৈচিত্র্যকেই তিনি মনে করতেন এ দেশের সম্পদ৷ রবীন্দ্রনাথের এই আদর্শই আজ আমাদের ‘আমরা’ এবং ‘ওরা’ এই বিভাজনের ঊর্ধ্বে উঠে মানুষকে আপন ভাবতে শেখায়৷ সমস্ত বৈচিত্র্যকে ধ্বংস করে ‘হিন্দি, হিন্দু, হিন্দুস্তান’ জাতীয় নীতিকে প্রত্যাখ্যান করতে শেখায়৷
১৯৩০ সালে ‘রাশিয়ার চিঠি’-তে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, ‘চিরকালই মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে তাদেরই সংখ্যা বেশি, তারাই বাহন; তাদের মানুষ হওয়ার সময় নেই; দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত, সবচেয়ে কম খেয়ে, কম পরে, কম শিখে, বাকি সকলের পরিচর্যা করে; সকলের চেয়ে বেশি তাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশি তাদের অসম্মান৷’ তাঁর এই ভাবনার প্রতিফলন অনেক আগেই দেখা গিয়েছিল তাঁর ‘গীতাঞ্জলি’ কাব্যগ্রন্থের ‘অপমানিত’ কবিতায়– ‘হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান/ অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান৷/ মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে,/ সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,/ অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান৷’
সম্প্রতি মহামারীর সময় আমরা দেখেছি, আমাদের দেশের হাজার হাজার শ্রমিক হেঁটে ঘরে ফিরছেন৷ ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, রোদে পুডে় কতজন প্রাণ হারিয়েছেন৷ তাদের জন্য কোনও পরিবহন, খাদ্য বা জলের ব্যবস্থাও ছিল না৷ দেখেছি, হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত-শ্রান্ত শ্রমিকেরা ট্রেনলাইনে ঘুমিয়ে পডে়ছে৷ আর মালবাহী ট্রেন চলে গেছে তাদের ঘুমন্ত শরীরের উপর দিয়ে৷ চারদিকে ছডি়য়ে পডে়ছে তাদের ছিন্নভিন্ন শরীর আর রক্তমাখা শুকনো রুটি৷ কোথায় তাদের মানুষের অধিকার! মনে পডে় ওই কবিতার পরবর্তী পঙক্তিগুলি— ‘মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে/ ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে৷’ এই জাতপাত ধর্ম সম্প্রদায়-শাসিত সমাজে প্রতিদিনই আমরা দেখি মনুষ্যত্বের চরম অবমাননা৷ আর তখন মনে পডে় রবীন্দ্রনাথকেই৷
এই সময়ের একটি বড় সমস্যা হলো, জাতীয়তাবাদের নামে ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িক হিংসা-বিদ্বেষ৷ এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন রবীন্দ্রনাথ৷ ১৯০৬ সালে শান্তিনিকেতনে এক অভিভাষণে বেদনাহত রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ‘এ কি হল ধর্মের চেহারা? এই মোহযুদ্ধ ধর্মবিভীষিকার চেয়ে সোজাসুজি নাস্তিকতা অনেক ভালো৷ ঈশ্বরদ্রোহী পাশবিকতাকে ধর্মের নামাবলী পরালে যে কী বীভৎস হয়ে ওঠে তা চোখ খুলে একটু দেখলেই বেশ বোঝা যায়৷’ ‘আমরা’ ও ‘তোমরা’, মানুষের মধ্যে এই বিভাজন রাজনীতি ও ধর্মের মিশ্রণে তৈরি হয়েছে৷ এর বিপদ রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন৷ ধর্মকে উপলক্ষ্য করে যে অসহিষ্ণুতার আবহ গোটা দেশ জুডে় দেখা যাচ্ছে, তার একেবারে বিপরীত প্রান্তে দাঁডি়য়ে যে রবীন্দ্রনাথ, তাঁকে নতুন করে চেনার এটাই বোধহয় সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ সময়৷
মানবিক শিক্ষা, জ্ঞান ও সাধনার দ্বারাই এই ধর্মবিকারকে প্রতিহত করা সম্ভব৷ ‘ধর্মমোহ’ কবিতায় তিনি লিখেছেন, ‘হে ধর্মরাজ, ধর্মবিকার নাশি/ ধর্মমূঢ়জনেরে বাঁচাও আসি/ যে পূজার বেদী রক্তে গিয়েছে ভেসে/ ভাঙো, ভাঙো, আজি ভাঙো তারে নিঃশেষে,/ ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো/ এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো৷’ জ্ঞান ও শিক্ষা চর্চার কারণেই উনিশ শতকের বাংলায় যে জাগরণ ঘটেছিল, সেই জ্ঞানচর্চার পরিবেশ ও মুক্তচিন্তার প্রকাশ আজ বিভিন্ন কারণে সংকুচিত৷ আর তারই সুযোগে অলস মস্তিষ্কে ঢুকে পড়ছে রাজনৈতিক ধর্মতন্ত্র থেকে উৎসারিত ঘৃণা ও বিদ্বেষ৷ রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, প্রতিটি মানুষের ‘আমার ধর্ম’ বলে একটা জিনিস আছে৷ কিন্ত্ত সে তা স্পষ্ট করে জানে না৷ সে নিজেকে বৈষ্ণব, শাক্ত, মুসলমান, খ্রিস্টান ইত্যাদি মনে করে৷ এই বাহ্যিক পরিচয়টাই তার কাছে এত বড় হয়ে ওঠে যে, তার নিজের ভেতরের ধর্ম আর তার চোখে পডে় না৷ ফলে তার পুজো, সাধনা সবই ব্যর্থ হয়৷ সে ভুলে যায় তার ভেতরের ব্রহ্মশক্তিকে, যে শক্তি প্রতিটি মানুষের মধ্যেই আছে৷ আর এভাবেই সে চলতে শুরু করে ধর্মের ভুল পথে৷
১৯১১ সালে ‘ধূলামন্দির’ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ‘ভজন পূজন সাধন আরাধনা সমস্ত থাক পডে়/ রুদ্ধ দ্বারে দেবালয়ের কোণে কেন আছিস ওরে?/… নয়ন মেলে দেখ দেখি তুই চেয়ে/ দেবতা নাই ঘরে৷’
তাহলে দেবতা কোথায়! ‘তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে করছে চাষা চাষ/ পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ, খাটছে বারোমাস৷’ তাঁর সেই কথারই প্রতিধ্বনি শুনি ১৯৩১ সালে হেমন্তবালা দেবীকে লেখা তাঁর চিঠিতে— ‘আমার ঠাকুর মন্দিরেও নয়, প্রতিমাতেও নয়, বৈকুণ্ঠেও নয়— আমার ঠাকুর মানুষের মধ্যে৷’ তিনি আরও বলেছেন, ‘আমাকে কোনো সম্প্রদায়ে বা কোনো দেশখণ্ডে বদ্ধ করে দেখো না৷ আমি যাঁকে পাবার প্রয়াস করি সেই মনের মানুষ সকল দেশের সকল মানুষের মনের মানুষ, তিনি স্বদেশ স্বজাতির ঊর্ধ্বে৷’
অধিকাংশ মানুষই এভাবে ভাবতে পারে না৷ হিন্দু হোক, মুসলমান হোক কিংবা খ্রিস্টান অথবা যে-কোনও সম্প্রদায়ের মানুষ হোক, বাহ্যিক আচার আর বিধানসর্বস্বতাই তাদের কাছে ধর্ম৷ রবীন্দ্রনাথ একেই বলেছেন ধর্মতন্ত্র, মানবের নিত্য ধর্মের সঙ্গে এর কোনও যোগ নেই৷ আর তাই এত ব্যবধান, এত বিভাজন৷ এর থেকে মুক্তির উপায় পরস্পরের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়, দেখা সাক্ষাৎ, মেলামেশা৷ পারস্পরিক অপরিচয়ের দূরত্ব যত বেশি হবে, অনৈক্য ততই প্রবল হয়ে উঠবে৷
রবীন্দ্রনাথের এই ধর্মবোধ ও সমাজ-ভাবনার জন্য তাঁকে প্রবল বিরোধিতা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ সহ্য করতে হয়েছে৷ কিন্ত্ত তিনি তাঁর আদর্শে অবিচল থেকেছেন৷ বরং তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর এই বোধকে আরও গভীরভাবে প্রচার করতে সচেষ্ট থেকেছেন৷ মানবতার এই আদর্শকে তিনি ধর্মের ঊর্ধ্বে তো বটেই, স্থান দিয়েছেন দেশেরও ঊর্ধ্বে৷ জাত-ধর্মে বিদীর্ণ এই দেশে, এই বিশ্বে তাঁর ‘মানুষের ধর্ম’ই হতে পারে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ মুক্তির পথ৷
Advertisement