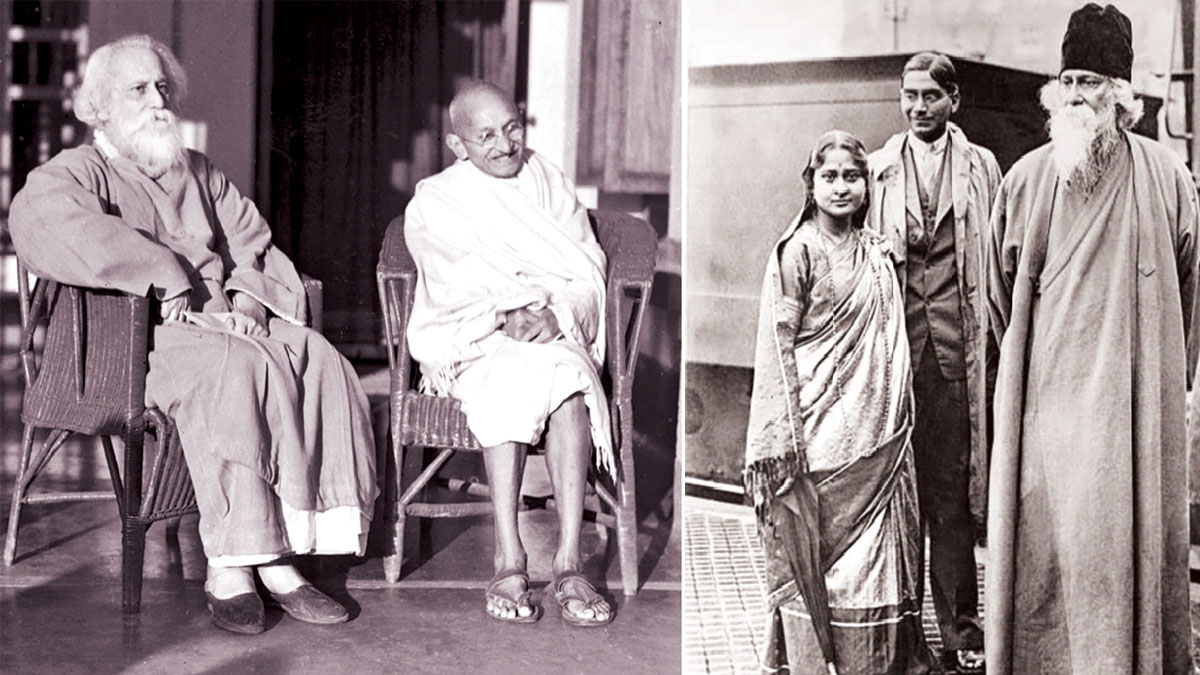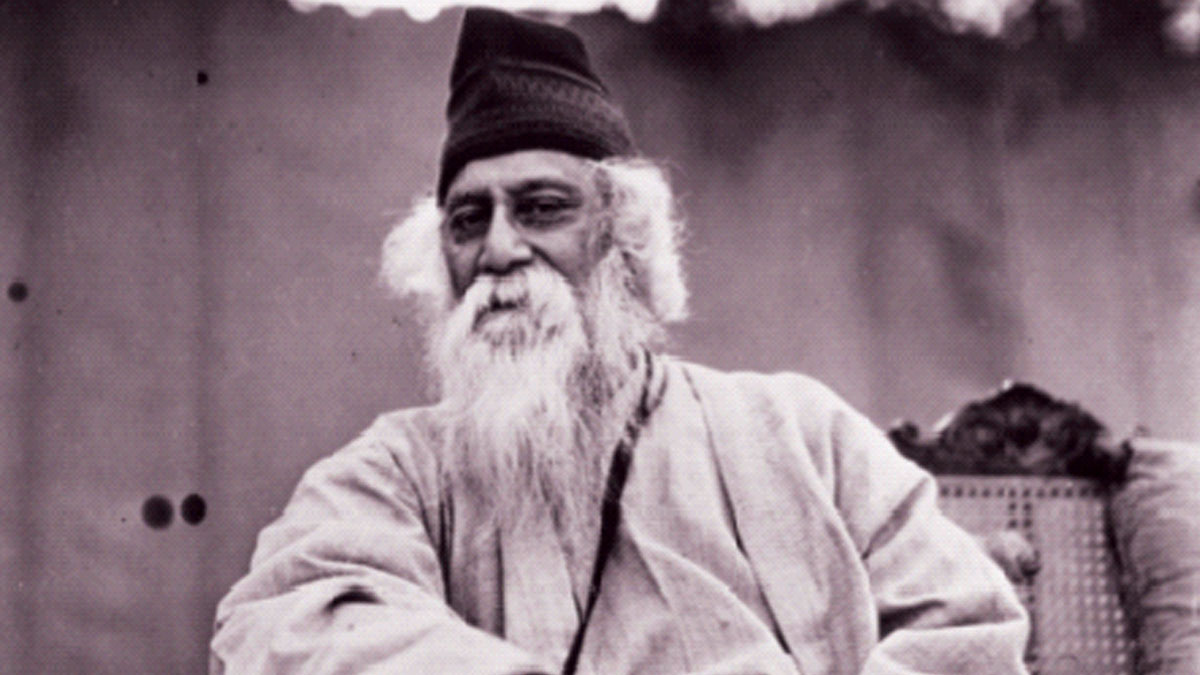সুস্মিতা মুখার্জী চট্টোপাধ্যায়
‘হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি,
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।
ধরায় আছে যত মানুষ শত শত
আসিছে প্রাণে মোর হাসিছে গলাগলি।
এসেছে সখাসখী বসিয়া চোখাচোখি,
দাঁড়ায়ে মুখোমুখি হাসিতে শিশুগুলি।
এসেছে ভাইবোন পুলকে ভরামন,
ডাকিছে ‘ভাই ভাই’ আঁখিতে আঁখি তুলি।’…
Advertisement
রবীন্দ্রচেতনায় যখন এই বিশিষ্ট উপলব্ধি ঘটেছিল, তখন পারিপার্শ্বিক বাস্তব সামাজিক ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ছোটোখাটো সংঘাত বিরোধের কোনো বিরাম ছিল না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চৈতন্য সবরকম ধর্মীয় তথা সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণ গণ্ডি ছাড়িয়ে বিশ্বমানবলোকের সঙ্গে আপন আত্মীয়তা বিস্তারেই সর্বাধিক আগ্রহ বোধ করেছিল। রবীন্দ্রনাথের এই বিশিষ্ট চেতনা মানস পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে বিবর্তনের যে রূপ নিয়েছিল সেখানেও আমরা সাম্প্রদায়িকতার স্পর্শমুক্ত একটি বিশ্বমানবিক আবেদনে তাঁকে সমৃদ্ধ হতে দেখেছি।
Advertisement
বর্তমান ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতাকে সমানভাবে প্রতিরোধের জন্য, সামাজিক পরিবর্তন ঘটানোর জন্য অন্যান্যদের তুলনায় একালের শ্রেষ্ঠ মানবদরদী, সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদবিরোধী, বিচ্ছিন্নতাবাদবিরোধী রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। সাম্প্রদায়িকতাবাদ দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা এবং তার বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করতে হবে রাজনীতির ক্ষেত্রে এবং চিন্তা মনন ও বুদ্ধির ক্ষেত্রে। রবীন্দ্র জীবনদর্শন বা রবীন্দ্রকাব্যের সাধনা কোনো সম্প্রদায় বা সম্প্রদায়গত দেবতার সাধনা নয়। তাঁর ভাবসাধনায় বৈষ্ণব সহজিয়া, বাউল-কীর্তনীয়া, হাফিজ সাদী, উপনিষদ, লোক-সংস্কৃতি একই আধারে বিরাজিত থাকে। তাঁর জীবনচেতনা আর রসতৃষ্ণা সত্যানুসন্ধানে স্বতোৎসারী। তাঁর স্বধর্ম ও স্বাজাত্যবোধ সাম্প্রদায়িকতার সীমা অতিক্রম করে ব্যক্তিপ্রতিভার বিচিত্র বিকাশে আত্মপ্রতিষ্ঠ। তাঁর ‘ভারততীর্থ’ কবিতায় শক-হুন-পাঠান-মোগল একদেহে লীন হয়েছে। তাঁর ধর্মবোধ জীবনবোধের নামান্তর— সাম্প্রদায়িকতাবিহীন চিন্তার প্রকাশ।
ভারতবর্ষের যে দুর্ভাগ্যজনক বেদনার অভিঘাতে তার ইতিহাসের পৃষ্ঠা আজ রক্তাশ্রুলিপ্ত, শিহরিত, সেই দুর্ভাগ্যজনক বেদনাটি হল বোধবুদ্ধিহীন সাম্প্রদায়িকতা। সেই সাম্প্রদায়িকতার কোনো মানবিক মূর্তি নেই, নেই মানবিক বোধশক্তিসমৃদ্ধ হৃদয়, নেই যুক্তিবিচার সম্পন্ন মেধা। সেইজন্য তা পৈশাচিক, পাশবিক— হিংস্র বর্বরতার নামান্তর।
রবীন্দ্রনাথ সত্য-শিব-সুন্দরের পূজারী। ধর্ম রবীন্দ্র-ভাবনায় কোনো সাম্প্রদায়িক তকমা নয়, ধর্ম রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে, মননে শ্রেয় বোধের মন্ত্রে পরিশোধিত সত্য, সুন্দর ও মানবিক মঙ্গল বিধায়ক এক সজীব ও সুমহৎ চেতনা। তাই সর্বকালিক, সর্বভূমিক মানুষের ধর্ম হল মানবধর্ম। লৌহ-কাঠিন্য নয়, কল্যাণ-নিষিক্ত নমনীয়তা— সৃষ্টিশীল নীতি ও সজীব ন্যায় চেতনাই ধর্ম। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, ধর্ম যখন স্বার্থসিদ্ধি সন্ধান করে, খোঁজে বিত্তবৈভব, তখন তা আর ধর্ম থাকে না। অধর্মের বিষাক্ত লালায় সিক্ত হয় তার সর্বাঙ্গ। তখনই ধর্মের নামে কদর্য সাম্প্রদায়িকতা ফুঁসে ওঠে, বিকৃত ধর্মের অস্ত্রাঘাতে মানবধর্মের সর্বাঙ্গ থেকে রক্ত ক্ষরিত হয়। সে মানব সভ্যতার এক চরম দুঃসময়।
ধর্ম আমাদের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ আবশ্যক সন্দেহ নেই, কিন্তু মন্দিরে বা শাস্ত্রে, প্রতিমায় বা প্রতীকে দেবতার অন্বেষণ নিরর্থক। দেবতা মানুষের মধ্যেই বিরাজমান, আর সেই বিশ্বাসই তাঁর বাউলসংগীতে ব্যক্ত। এই মানবপ্রেমই সকল ধর্মের সারকথা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন…
‘তাই তোমার আনন্দ আমার পর
তুমি তাই এসেছ নীচে।
আমার নইলে ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হত যে মিছে।’
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আমাদের ‘মনের মানুষ’ রয়েছে আমাদেরই অন্তরে, কিন্তু বাইরের আকর্ষণে আমরা সে কথা ভুলে যাই। আমাদের আঘাতে, আশায় এবং ভালোবাসায় যে রয়েছে আমাদেরই কাছে, সেই মনের মানুষের প্রতি আমরা দৃষ্টিপাত করি না।
‘আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে
দেখতে পাইনি।
বাহির পানে চোখ মেলেছি
হৃদয়পানে চাইনি।’
দেবালয় যে দেবতার আবাস নয়, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যে দেবতাকে পাওয়া যায় না, বাউল সম্প্রদায়ের এই বিশ্বাসের প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছিল।
মন্দিরে আগত পুণ্যার্থীর উদ্দেশে কবি বলেছেন,
‘অন্ধকার লুকিয়ে আপন মনে
কাহারে তুই পূজিত সংগোপনে,
নয়ন মেলে দেখ দেখি তুই চেয়ে
দেবতা নাই ঘরে।’
যে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান আপন হৃদয়ে সে ঈশ্বরের আরাধনার জন্য মন্দির যাওয়া অর্থহীন, যেখানে তথাকথিত ‘স্তবের বাণীর আড়াল’ দিয়ে আমরা দেবতাকে ঢেকে রাখি, তাঁর পূজার ছলে আমরা তাঁকেই ভুলে থাকি। তাই কবি বলেন,
‘কাজ কি আমার মন্দিরেতে আনাগোনায়
পাতব আসন আপন মনের একটি কোনায়।’
সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন, ‘এই কি ধর্মের চেহারা? এই মোহমুগ্ধ ধর্ম বিভীষিকার চেয়ে সোজাসুজি নাস্তিকতা অনেক ভালো।’ তিনি অনুভব করলেন যে, ধর্ম নয়, অনুষ্ঠানগত আনুগত্যই ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে ক্রমশ সত্য হয়ে উঠেছে।
জন্মসূত্রে প্রাপ্ত কোনো ধর্মমতের প্রশ্নহীন অনুমোদনের পথ অনুসরণ করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ধর্ম সম্পর্কিত বিশিষ্ট প্রত্যয়ে উপনীত হননি, তাঁর আপন গোষ্ঠীর মানুষের কাছে পরম সত্য বলে প্রতিভাত কোনো ধর্মমতকেও তিনি নির্বিচারে অনুসরণ করেননি। উনিশ শতকে যে পরিবার উপনিষদে উচ্চারিত ঋষিবাক্য অনুসরণে ধর্মসংস্কারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল সে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও তিনি ব্রাহ্মধর্মের আকর্ষণে চিরকাল আবদ্ধ থাকেননি।
রবীন্দ্রনাথের ধর্মচর্চা অথবা ধর্ম বিষয়ক পড়াশোনা শুরু হয়েছিল ছোটবেলাতে তাঁর পিতার হাত ধরে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পুত্রদের বেদ এবং উপনিষদের শ্লোকগুলো আবৃত্তি করাতেন। রবীন্দ্রনাথের বাবা ছিলেন ব্রাহ্ম আন্দোলনের পুরোধা। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই স্মরণ করেছেন যে, ধর্মকে মহর্ষি নিজের সংসারের মধ্যে কখনও শাসনের বস্তু করেননি। কোনো বিশেষ মতকে অভ্যাস বা অনুশাসনের দ্বারা তিনি আরোপ করতে চাননি। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজনীন মানসিকতা সুস্পষ্টভাবে গড়ে ওঠার পটভূমির একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে রবীন্দ্রজীবনে মহর্ষির প্রভাব উল্লেখযোগ্য। একদিকে উপনিষদ, ইতিহাস, ভূবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান আর একদিকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং ভগবতী দেবী— এঁদের জীবনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব রবীন্দ্রচিত্তে জাতিগত, ধর্মগত, সম্প্রদায়গত বন্ধনমুক্তির অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে নিরন্তর। তাই পরিণামে রবীন্দ্রনাথকে আমরা দেখতে পেলাম আন্তর্জাতিক মানবতার এক বিশাল প্রতিমূর্তি হিসেবে।
কেউই বলবেন না যে, রবীন্দ্রনাথ একজন নির্ভেজাল নাস্তিক ছিলেন বা আদর্শগতভাবে তিনি ছিলেন বামপন্থী। কোনো না কোনোভাবে ঈশ্বর বিশ্বাস তাঁর কবিতায় এবং গানে খুব স্পষ্টভাবেই অভিব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু এ সবই ছিল তাঁর ব্যক্তিগত এবং অন্তর্জীবনে দ্বন্দ্ব অথবা দ্বন্দ্বটা শিক্ষানীতির মরমিয়া উপলব্ধি, যা রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধি, উজ্জ্বল সমাজচেতনা এবং বিশ্ববোধকে কোনোভাবেই ব্যাহত করতে পারেনি। মানুষের জীবন সামাজিক, ধর্মীয়, আঞ্চলিক, রাজনৈতিক এবং অন্যান্য সমজাতীয় নীচাশয়তার কারণে কীভাবে নিজের, অপরের এবং সকলের সর্বনাশ ডেকে আনছে তার সুনিপুণ বিশ্লেষণ রবীন্দ্রনাথ তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত বলিষ্ঠ ভঙ্গিমায় উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর রচনাগুলিই হচ্ছে তাঁর বুদ্ধিবাদিতার জগৎ, যেখানে রবীন্দ্রনাথ ভাবাবেগের কাছে আত্মসমর্পণ করেননি, বরং ইতিহাস ও বিজ্ঞাননির্ভর জীবন্ত প্রত্যয়কেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন সাহিত্যিক তথ্য-প্রমাণের মাধ্যমে।
রবীন্দ্রমানসের এই দিকটির মাধ্যমেই রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পেয়েছে, যে ব্যক্তিত্ব জাতীয়তা, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় বিশ্বাস প্রভৃতি নিয়ে গড়ে ওঠা যাবতীয় সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে। প্রকৃতপক্ষে এইসব রচনায় রবীন্দ্রনাথ অনবদ্য কাব্যসুষমামণ্ডিত যুক্তিবাদিতার মাধ্যমে আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন জীবনে প্রকৃত সুখ ও শান্তি পেতে গেলে কীভাবে আমাদের ওই সব সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে আন্তর্জাতিক, ধর্মনিরপেক্ষ, পরমতসহিষ্ণু, চর্যাচর্য জীবনধারা গ্রহণ করা উচিত। জগৎ সংসারে যে সুখশান্তি সহজ ও সুনিশ্চিতভাবেই আমাদের প্রাপ্য, আমাদের নিজস্ব অহংকৃত আত্মস্ফীতি এবং অপরিমিত আত্মশ্লাঘার তাড়নায় জীবনে সেই সবকিছুর প্রবেশাধিকারের পথ আমরাই রুদ্ধ করে দিই। আমরা বুঝিও না যে, এটা আমাদের কত বড়ো ভুল।
ধর্ম আমাদের ধারণ করে আছে— এই অর্থে ধর্ম সম্পর্কে আমাদের কাতরতা যে অমূলক, তা রবীন্দ্রনাথ কৌতুকের মাধ্যমে বুঝিয়েছেন এইভাবে যে, যা আমাদের ধারণ করে তাই চূড়ান্ত সত্য হতে পারে না। আমরা গাড়িতে উঠলে সেই গাড়িও আমাদের ধারণ করে। কিন্তু তাই বলে গাড়ির সেই ধারণ করাটা আমাদের কাছে চূড়ান্ত সত্য হওয়া উচিত নয়। সেই গাড়িতে প্রয়োজন অনুসারে আমাদের ঢুকতে হয়, বেরুতে হয়, দুর্ঘটনায় পড়ে কাতর হলে লাফিয়ে পড়তে হয়, এমন কি প্রয়োজনে গাড়ি বেচে দিতে হয়। অর্থাৎ গাড়ির ভিতরে চিরকাল বসে থাকা কিছুতেই সঠিক কাজ বলে পরিগণিত হতে পারে না। ঠিক তেমনই ধর্মের একদেশদর্শী, অনুদার এবং অন্য ধর্মের পক্ষে দুঃখদায়ক অনুশাসনগুলি যদি আমরা অনন্তকাল ধরে মেনে চলি, মনের মধ্যে প্রশ্রয় দিই, তবে সেও হবে বিরাট ভুল। এবং এর ফলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিও গড়ে উঠবে না। রবীন্দ্রনাথের মতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সৃষ্টি ও রক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়— বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক হৃদয়ের সংযোগ সৃষ্টি করা।
আমাদের গ্রামীণ জনসমাজে আর্থ-সামাজিক প্রয়োজনেই দরিদ্র ও নিম্নবর্গীয় হিন্দু-মুসলমান সাধারণ মানুষ বাধ্য হয়েই একে অপরের সহায়ক হিসেবে জীবনযাপন করে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। ফলে উভয়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কোনো অভাবই নেই, এমনকি অনেক সময় এই পারস্পরিক সংমিশ্রণের ফলে সমন্বয়ী ধর্ম সৃষ্টির প্রচেষ্টাও দেখা গেছে এদের মধ্যে। তাঁর হিন্দু মুসলমান: ‘কালান্তর’-এ তিনি লিখেছেন— যে বুদ্ধিতে এই সামঞ্জস্যসাধনের প্রক্রিয়াটি সাধারণ মেহনতি মানুষের মধ্যে সক্রিয় থাকে, তা কোনো ধর্মীয় বুদ্ধি নয়, তা ‘ধর্মবুদ্ধি’। রবীন্দ্রনাথ এই ধর্মবুদ্ধির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, ‘মানুষ বলেই মানুষের যে মূল্য, সেটিকেই সহজ প্রীতির সঙ্গে স্বীকার করাই প্রকৃত ধর্মবুদ্ধি।’
রবীন্দ্ররচনাগুলি পর্যবেক্ষণ করলে রবীন্দ্রনাথের এই চিন্তাধারার অভিব্যক্তিকে লক্ষ্য করা যায় তাঁর বিভিন্ন রচনায়। কয়েকটি রচনা লক্ষ্য করলেই আমরা রবীন্দ্রনাথের এই মানসিকতার স্পষ্ট রূপটি পেয়ে যাই।
‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসের নিখিলেশের নজর ছিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রজাদের স্বার্থ রক্ষা করা। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের দায়িত্ব সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের উপরই ন্যস্ত, প্রবলই দুর্বলকে রক্ষা করার ব্যাপারে দায়বদ্ধ— এই স্বাভাবিক বোধ যাদের নেই, তারা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মর্যাদা থেকে ভ্রষ্ট। এই চেতনা নিখিলেশের মধ্যে ছিল, ছিল গোরারও। এইভাবেই রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে তাঁর আদর্শ চরিত্রগুলির মাধ্যমে।
‘বিসর্জন’ নাটকে রবীন্দ্রনাথের এই ব্যক্তিত্বই প্রকাশিত হয়েছে। এই নাটকে শেষ পর্যন্ত দেখা গেল রঘুপতির ধর্মান্ধতার বলি রঘুপতি নিজেই। ধর্মান্ধ অহংকারের তাড়নায় তিনি বুঝতেই পারেননি যে, তাঁর মানবপ্রকৃতিকে তিনি অস্বীকার করেছেন। ফলে প্রকৃতির প্রতিশোধে জয়সিংহের আত্মহত্যার পর তাঁকে চতুর্দিকে শূন্য দেখতে হল, যেহেতু, ‘পিতা’ সম্বোধনের উপর তাঁর যে মানব অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল, জয়সিংহের মৃত্যুতে তা ধূলিসাৎ হয়ে গেল। পক্ষান্তরে গোবিন্দমাণিক্য এই নাটকে প্রারম্ভিক দুঃখ-কষ্ট পারিবারিক ও রাজনৈতিক অশান্তি সত্ত্বেও পরিশেষে, ধর্মান্ধতার পরাভব ঘটিয়ে জয়লাভ করলেন তাঁর মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং ধর্মীয় উদারতার জন্য।
‘চতুরঙ্গ’ উপন্যাসে জগমোহনের মুখ দিয়েও এই ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের অনুশীলিত মানসিকতা প্রকাশিত হয়েছে। জগমোহন শচীশকে একদিন বলেছিলেন, ‘দেখ্ বাবা, আমরা নাস্তিক, সেই গুমরেই আমাদিগকে একেবারে নিষ্কলঙ্ক নির্মল হইতে হইবে। আমরা কিছুকে মানি না বলিয়াই আমাদের নিজেকে মানিবার জোর বেশি।’ রবীন্দ্রসাহিত্যে এই উক্তিটির অপরিসীম দ্যোতনা। যারা ঈশ্বর বিশ্বাসী, তাদের পক্ষে অন্যায় করে ক্ষমা প্রার্থনা করার একটা উপায় আছে এবং ঈশ্বর বিশ্বাসের জোয়ারে তাদের চারিত্রিক দোষ ত্রুটি অনেকাংশে ঢাকা পড়ে যায়। কিন্তু নাস্তিকদের এইসব সুযোগ সুবিধা নেই, উপরন্তু সাধারণের চেয়ে ব্যতিক্রমবিশিষ্ট হওয়ায় তাদের নিন্দুক সমালোচকের সংখ্যাও বেশি। সুতরাং তাদের নিষ্কলঙ্ক থাকতেই হয় এবং তার নাস্তিকতার গৌরব রক্ষায়।
তাঁর ‘আত্মপরিচয়’ গ্রন্থে তিনি বলেছেন— ‘সকল মানুষেরই আমার ধর্ম বলে একটা বিশেষ জিনিস আছে। কিন্তু সেটিকেই সে স্পষ্ট করে জানে না। সে জানে আমি খ্রীস্টান, আমি মুসলমান, আমি শাক্ত, আমি বৈষ্ণব ইত্যাদি।’ আসলে মানুষের জীবনদর্শন বা চরিত্র, যা তার ব্যক্তিত্বের ভেতর থেকে জেগে ওঠে তাই ধর্ম। রবীন্দ্রনাথের ধর্ম হল ‘মানুষের ধর্ম’।
রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি, তাই সাহিত্যিক রূপায়ণের মাধ্যমে যতদূর সম্ভব তিনি তাঁর আন্তর্জাতিক মানবতার বাণীকে সর্বোচ্চ সম্মানে সম্মানিত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর ‘বনবাণী’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ‘মধুমঞ্জরী’ শীর্ষক কবিতাটির ভূমিকায় কবি বলেছিলেন, ‘এ লতার কোনো বিদেশী নাম নিশ্চয়ই আছে— জানিনে। আমাদের দেশের মন্দিরে এই লতার ফুলের ব্যবহার চলে না, কিন্তু মন্দিরের বাইরে যে দেবতা মুক্তস্বরূপ আছেন তাঁর প্রচুর প্রসন্নতা এর মধ্যে বিকশিত।’ আসলে ধর্মের সত্য রূপের যাঁরা সন্ধান করেছেন তাঁরা সকলেই যুগে যুগে, দেশে দেশে একই কথা বলেছেন। তাঁরা সকলেই ধর্মকে শাস্ত্র এবং আচারসর্বস্বতার বন্ধন থেকে মুক্ত করে সর্বমানবের কল্যাণময় পথে পরিচালিত করতে চেয়েছেন। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক এবং মুসলিম প্রসঙ্গ রবীন্দ্রকাব্যে যথেষ্ট না হলেও গৌণ নয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক আলোচনায় তাঁর বিশেষ মানসিকতার ও পরিবর্তিত মানসিকতার স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। অবশ্য বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন ও তৎপরবর্তীকালে বক্তৃতা ও প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কিত ধারণার অনেক পরিণত রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। মূলত রবীন্দ্রনাথের ঘটনাপ্রধান রচনাতেই মুসলিম প্রসঙ্গ আনীত হয়েছে এবং এই জাতীয় কবিতাগুলির অধিকাংশই সংকলিত হয়েছে ‘কথা ও কাহিনী’ কাব্যে। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন, পৌরাণিক যুগের কৃষ্ণ যে ধর্ম প্রচার করেছিলেন, সে ধর্ম পুরোহিতশাসিত শাস্ত্রসিদ্ধ বিধানের অমোঘতা মেনে নেয়নি। রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন—
‘পথের ধূলায় বক্ষ পেতে রয়েছে যেই গেহ
সেই তো তোমার গেহ।’
বিধাতা যখন তাঁর শুচিবসন ত্যাগ করে সকল কর্মে সর্বমানবের মধ্যে বিরাজমান, তখন মানুষের ধর্মও সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তার আবেদন বিশ্বজনীন। ধর্মের আবেদন যখন বিশ্বজনীন না হয়ে সাম্প্রদায়িক হয়ে ওঠে, তখন সাম্প্রদায়িক দেবতা বিদ্বেষবুদ্ধির অহংকারের অবজ্ঞাপরতার, মূঢ়তার দৃঢ় আশ্রয় হয়ে দাঁড়ায়, শ্রেয়ের নামাঙ্কিত পতাকা নিয়ে অশ্রেয় জগৎব্যাপী অশান্তির প্রবর্তন করে— স্বয়ং দেবত্ব অপমানিত হয়ে মানুষকে অবমানিত ও পরস্পর ব্যবহারে আতঙ্কিত করে তোলে। সাম্প্রদায়িক রূপে দেবতার প্রকাশ তাই মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।
রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে হিন্দু-মুসলমান উভয়েই ‘ভারতভাগ্যের শরিক’। উভয় সম্প্রদায়ের সমকক্ষতা, ঐক্য একমাত্র সম্ভব শিক্ষার প্রসারের দ্বারা। শিক্ষার মাধ্যমে বৌদ্ধিক ও আত্মিক উন্নতি এবং মনুষ্যত্বের উদ্বোধন ঘটে। আজ যখন সাম্প্রদায়িক শক্তি সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে, বিভক্ত করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে, তখন রবীন্দ্রনাথের প্রদর্শিত পথে ভারত ইতিহাসের শরিকদের মিলিত হতে হবে। আর এই মিলন বিচ্ছিন্নতাবাদ, মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিরুদ্ধে একান্ত প্রয়োজন। সর্বাঙ্গীণ সামাজিক দায়বদ্ধতাকে স্বীকার করে সমস্তরকম মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিত করতে হবে বৃহৎ ও ব্যাপক মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতায়।
পৃথিবীর ইতিহাসে মানব-ভাগ্যে দুঃসময় বহুবার ঘনিয়ে এসেছে। পৌত্তলিকদের সঙ্গে খ্রিস্টানদের, খ্রিস্টানদের সঙ্গে ইহুদিদের, পৌত্তলিকদের সঙ্গে মুসলমানদের, মুসলমানদের সঙ্গে খ্রিস্টানদের, মোগলদের সঙ্গে পাঠানদের সংঘাতে এবং সংঘর্ষে বিশ্ব ইতিহাসের পাতা হয়েছে রক্তরঞ্জিত। ভারতে আর্য-অনার্য, হিন্দু-বৌদ্ধ, হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব সংঘাতে সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। যেখানে বিচিত্র উপকরণের সমাবেশ যত বেশি, সেখানেই অজ্ঞাতার অভিশাপে দ্বন্দ্ব-সংঘাতও তত বেশি।
রবীন্দ্রনাথ ইতিহাস বিশ্লেষণ করে দেখেছেন যে, মানুষের এই স্বাভাবিক ধর্মবুদ্ধিকে বিনষ্ট করতে চায় প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম, যেহেতু প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে অবলম্বন করে চিরকালই কিছু প্রতিষ্ঠানপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি নিজস্ব কায়েমি স্বার্থকে চরিতার্থ করার সুযোগ পায় এবং মানুষের স্বাভাবিক ধর্মবুদ্ধি জাগ্রত থাকলে তা বাধাগ্রস্ত হয়। এইজন্য ইতিহাসের প্রতিটি বিপ্লবে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মবিরোধিতা বা ধর্মবিদ্বেষ বিপ্লবীদের একটা মুখ্য চালিকাশক্তি হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় রয়েছে এর প্রতি সমর্থন : ‘ইতিহাসে বারে বারে দেখা গেছে যখন কোনো মহাজাতি, নবজীবনের প্রেরণায় রাষ্ট্রবিপ্লব প্রবর্তন করছে, তার সঙ্গে সঙ্গে প্রবলভাবে প্রকাশ পেয়েছে ধর্মবিদ্বেষ। দেড় শত বৎসর পূর্বেকার ফরাসী বিপ্লবে তার দৃষ্টান্ত দেখা গেছে। সোভিয়েত রাশিয়া প্রচলিত ধর্মতন্ত্রের বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর। সম্প্রতি স্পেনে এই ধর্মান্ধের আগুন উদ্দীপ্ত।’
রবীন্দ্রনাথ এখানে স্পষ্টই ধর্মবিরোধিতার অনুকূলে কথা বলেছেন, ধর্মনিরপেক্ষতার চেয়ে যা অনেক বলিষ্ঠ এবং কার্যকরী। নিরপেক্ষতায় প্রবলের প্রবর্তনা থেকে যায়, কিন্তু বিদ্বেষে প্রবলের প্রবলতাকে অস্বীকার করা হয় এবং তার সাম্প্রদায়িক বিষদাঁতকে উন্মূলিত করে ফেলা সম্ভব হয়। সাম্প্রদায়িকতা দূরীকরণে রবীন্দ্রনাথের এই পরামর্শ তাঁর বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়, বহুদর্শী সমাজসচেতনতা এবং সর্বোপরি তাঁর বিশ্ববোধ থেকেই উদ্ভূত।
রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়লে অন্তরে, চেতনায় ঈশ্বরের নবজাগরণ হয়। সেই জ্ঞান যদি আমরা উপভোগ করতে পারি তাহলেই শান্তি, একতা এবং ভালোবাসার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক হয়ে উঠবে ভারতবর্ষ। তিনি বুঝেছিলেন, ধর্মের অচলায়তন ভেঙে ফেলার সময় হয়েছে। ধর্মমোহে উৎসাহিত সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ থেকে স্বদেশকে মুক্ত করার কঠিন সংকল্পে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সকল মানুষকে কবি আহ্বান করেন সংগ্রামের পথে, ধর্মকারার প্রাচীরে সম্মিলিত আঘাত হানতে—
‘যে পুজার বেদি রক্তে গিয়েছে ভেসে
ভাঙো ভাঙো, আজি ভাঙো তারে নিঃশেষে —-
ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো,
এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক জ্বালো।’
ভারতবর্ষ মানবমিলনের এক বিচিত্র কারখানা। নানা ধর্ম, নানা বর্ণ এবং নানা মানুষের ধারা এক বিচিত্র সঙ্গমে সম্মিলিত হয়ে মানব ঐক্যের এক আদর্শ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এখানে। সাম্প্রদায়িকতা তাই ভারতের আদর্শের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধপন্থী। ‘ভারতবর্ষের ইতিহাস’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, বিধাতা ভারতবর্ষের মধ্যে বিচিত্র জাতিকে টানিয়া আনিয়াছেন।… ঐক্যমূলক যে সভ্যতা মানবজাতির চরম সভ্যতা, ভারতবর্ষ চিরদিন ধরিয়া বিচিত্র উপকরণে তাহার ভিত্তি নির্মাণ করিয়া আসিয়াছে। পর বলিয়া সে কাহাকেও দূর করে নাই, অনার্য বলিয়া সে কাহাকেও বহিষ্কৃত করে নাই, অসংগত বলিয়া সে কিছুকেই উপহাস করে নাই। ভারতবর্ষ সমস্তই গ্রহণ করিয়াছে, সমস্তই স্বীকার করিয়াছে।… পরকে আপন করিতে প্রতিভার প্রয়োজন। অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিবার শক্তি এবং অন্যকে সম্পূর্ণ আপনার করিয়া লইবার ইন্দ্রজাল, ইহাই প্রতিভার নিজস্বতা। ভারতবর্ষের মধ্যে সেই প্রতিভা আমরা দেখিতে পাই।… ভারতবর্ষ কিছুকেই ত্যাগ করে নাই এবং গ্রহণ করিয়া সকলই আপনার করিয়াছে।’
রবীন্দ্রনাথ তাঁর মানবজীবনের যে গোত্রপরিচয় এখানে দিচ্ছেন, তার মধ্যে কোনো খণ্ডতার বোধ নেই। এর মধ্যে কোনও বিশেষ দেশ, বিশেষ জগৎ, বিশেষ ধর্মের স্থান নেই। এই পরিচয় অখণ্ড, আন্তর্জাতিক। এই জন্যই উপনিষদের যুগের বুদ্ধিজীবীদের কল্পনা এবং এ যুগের বৈজ্ঞানিকদের ব্যাখ্যার প্রভাবে তিনি বিশ্বাস করতেন যে, দেশ, জাতীয়তা, ধর্ম প্রভৃতি নিয়ে যে বিভাজন বিশ্ব মানবসমাজে ঘটানো হয়েছে তা মিথ্যা এবং অমূলক। মানুষের পরিচয় একটাই, এবং তা সে এই বিশ্বের মানুষ। এই ধারণাটি রবীন্দ্রনাথের কাছে একটি জীবনগত প্রত্যয়ে পরিণত হয়েছিল, তাই তিনি স্বদেশি যুগের জাতীয়তাবাদী পরিমণ্ডলের মাঝেও অকাতরে বলতে পেরেছিলেন, আমার দেশজননী এই দেশের মাটি, স্বরূপত যা বিশ্বময় এবং বিশ্বব্যাপী বিশ্বজনের আশ্রয়ের আঁচল সে মাটিতে সম্প্রসারিত। সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যের কোথাও আমরা এমন কিছুর সন্ধান পাই না, যা রবীন্দ্রনাথের এই জীবনগত প্রত্যয়ের পরিপন্থী। মানুষের জীবনদর্শন যে দু-একটি ধ্রুবকের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে, রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববোধ তারই প্রমাণ।
‘বিশ্বজনের পায়ের তলে ধূলিময় যে ভূমি
সেই তো স্বর্গ ভূমি।
সভায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি
সেই তো আমার তুমি।’
Advertisement