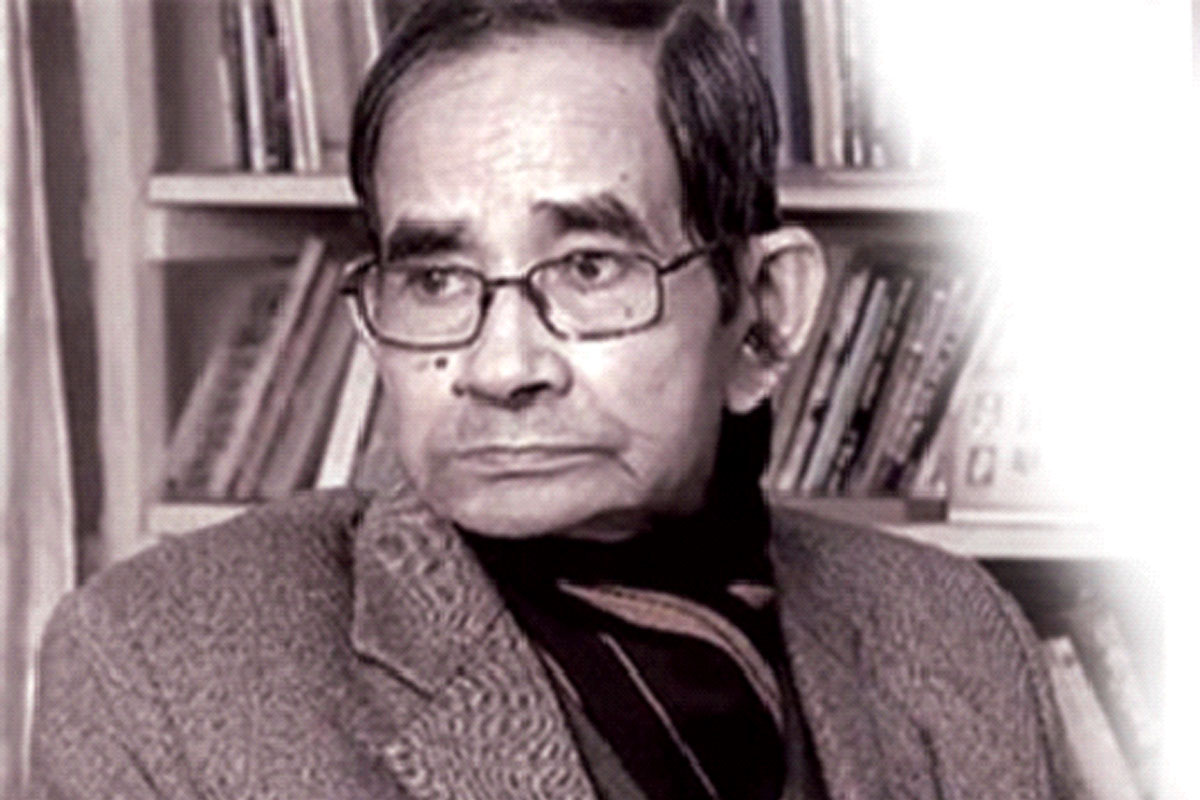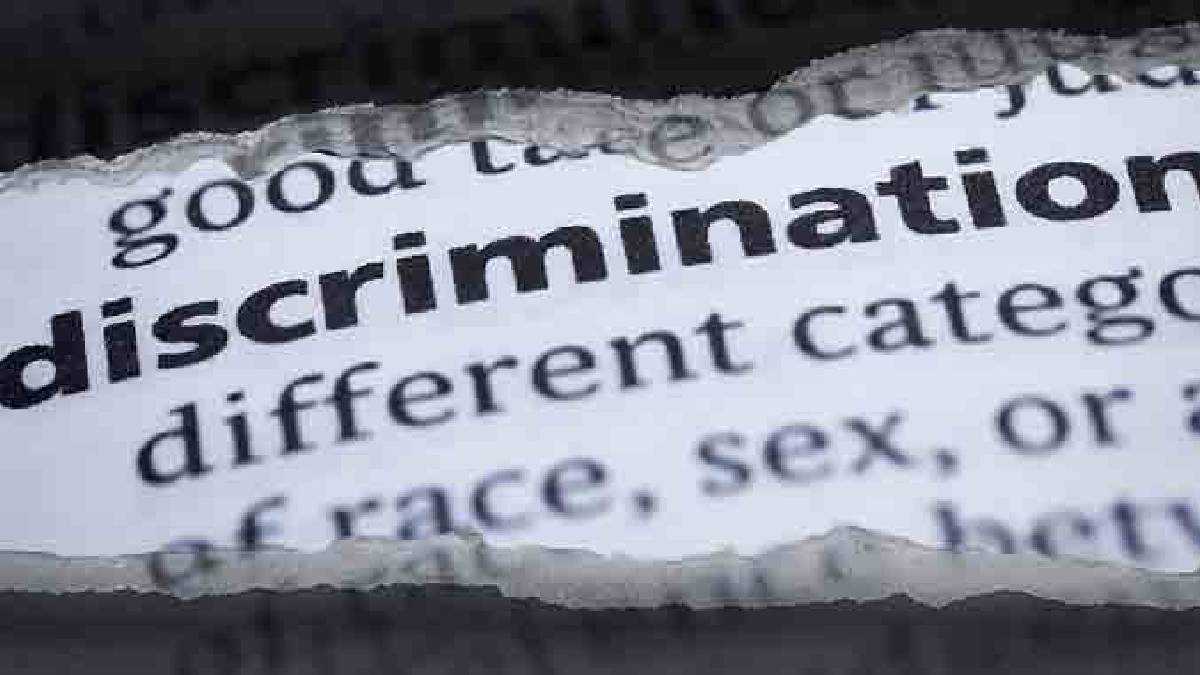হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
পূর্ব প্রকাশিতর পর
বিনয় সরকার বহু দেশ পর্যটন করেছেন, বহু ভাষা আয়ত্ত করেছেন, বহু বিদ্যা অর্জন করেছন। যখন যেখানে নতুন কিছু দেখেছেন, নতুন চিন্তা নতুন কর্মোদ্যম মনকে আকৃষ্ট করেছ তখনই তা শিক্ষিত বাঙালির গোচরে আনবার চেষ্টা করেছেন। আমাদের ছাত্রাবস্থায় বহু পত্রপত্রিকায় বিনয় সরকার রচিত ‘বর্তমান জগৎ’ শীর্ষক বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে দেখেছি। তথ্যনিষ্ঠ সুলিখিত সে সব প্রবন্ধ তখন শিক্ষিত সমজে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। পরে তাঁর ‘বর্তমান জগৎ’ প্রব্ধাবলির এক সুবৃহৎ সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল। এমন বিষয় কমই ছিল যে বিষয় নিয়ে তিনি ভাবেন নি, লেখেন নি। ধন বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, রাষ্ট্র বিজ্ঞান এবং মানব সভ্যতার ইতিহাস চর্চাই সমধিক প্রাধান্য লাভ করেছে; তাহলেও শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং সাহিত্য বিষয়েও কিছু কম লেখেন নি। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বিবেকানন্দের এবং বিনয় সরকারের রচনা রীতিতে একটি লক্ষণীয় সাদৃশ্য আছে—একটি যেন অতি নিকট আত্মীয়তার সম্পর্ক, ইংরেজিতে যাকে বলে family likeness। দুজনের একজনও মামুলি কথা কখনো বলেন নি, মামুলি ভাষাও কখনো ব্যবহার করেন নি। দুজনেই লিখেছেন কথা বলার ভঙ্গিতে— ছাপার অক্ষরে কথা নয়, মৌখিক ভাষায় কথা। ভাষার ব্যাপরে বিনয় সরকার বিবেকানন্দের চাইতেও বেপরোয়া। একটু নমুনা দিলেই কথাটা মালুম হবে।
Advertisement
নজরুলের কাব্য সম্বন্ধে প্রশংসাসূচক আলোচনা করতে গিয়ে বিনয় সরকার বলছেন— ‘‘নজরুল কাব্যের প্রথম মুদ্দা বিপ্লব, আর দ্বিতীয় মুদ্দা ভালোবাসা।…ভালোবাসাটা যে শারীরিক চিহ্ন—একথা কবিতায়, নাটকে, নভেলে লিখতে হাত কাঁপে, মুখ শুকিয়ে আসে—বুক ফেটে যায়। যদি বা দু-একজন লিখলে, তার সমালোচকেরা এই মামুলি রক্তমাংসের স্বধর্মটিকে নিঙেড়-শুকিয়ে একটা তথাকথিত আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কেঠো তক্তায় নিয়ে ঠেকাবেই ঠেকাবে। …বাঙালী জাতের আবহাওয়ায় নজরুলের পক্ষে ভালোবাসার কবি হওয়া খুবই বাহাদুরির কাজ। অতিমাত্রায় বেহায়া এবং ঠোঁটকাটা না হ’লে নজরুলের পক্ষে অনেক কবিতাই প্রকাশ করা সম্ভব হতো না।’
Advertisement
এ-ই ছিল তাঁর কথা বলার এবং লেখার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গি। এ ছাড়া তিনি তাঁর লেখায় হিন্দি, উর্দু, এমন কি ফারসি শব্দ অকাতরে ব্যবহার করতেন। তখনকার কোন কোন সমালোচক বলেছেন, বিনয় সরকার বাংলা ভাষার জাত মেরে দিচ্ছেন। জাত কি এমন ঠুনকো জিনিস যে ঐটুকুতেই জাত মারা যাবে? বিশেষ করে, বিদেশী শব্দের সংমিশ্রণে ভাষার জাত যায় না, জোর বাড়ে।
ইংরেজিতে বলে—Style is the man। খুব খাঁটি কথা—লেখকের ব্যক্তিত্বটিই তাঁর স্টাইল হয়ে দেখা দেয়। বিবেকানন্দ বা বিনয় সরকারের লেখা পড়লে মনে হবে, একটা গোটা মানুষ কথা বলছেন এবং সে মানুষটি পাঠকের সুমুখে দাঁড়িয়ে সোজাসুজি তাকে উদ্দেশ করেই কথা বলছেন। সত্যি বলতে কি, যে লেখায় ব্যক্তিত্বের প্রকাশ নেই যে লেখা গতানুগতিক, তাতে লেখকের নিজস্বতার ছাপ নেই এবং সেই হেতু সে লেখায় কোন স্টাইল নেই। যে মানুষটি স্টাইলিস্ট তিনি আর পাঁচ জনের মতো নন, তিনি একেবারে পঞ্চম। স্টাইল স্বভাব-সিদ্ধ জিনিস, সেটা অনুকরণ-সাধ্য নয়।
বিবেকানন্দ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন, কথা বলেছেন উদাত্ত কণ্ঠে। সে কণ্ঠ, সে ভাষা অপরকে আদৌ মানাবে না। স্টাইলের রূপভেদ আছে—যাঁর প্রতিভা যেমন, তাঁর প্রকাশভঙ্কি তেমন। কেউ কলকণ্ঠ, কেউ মৃদুকণ্ঠ। বলা বাহুল্য, সাহিত্য প্রচারকের কাজ করে না, সে পরিবেষক, পরিবেষণ করে রস. কাজেই সাহিত্য বেশির ভাগ সময়েই মৃদুভাষী। গলা উঁচু করতে গেলে প্রচারের ভঙ্গি এসে যায়, তাতে রসভঙ্গ হবার আশংকা থাকে। রসের কথা চেঁচিয়ে বলতে হয় না, রসিয়ে বলতে হয়। ঐ রসিয়ে বলার মধ্যেই স্টাইল। যাঁরা সার্থক রসস্রষ্টা তাঁরা সকলেই স্টাইলেরও স্রষ্টা। শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, তারাশংকর, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়— প্রত্যেকেরই প্রকাশ ভঙ্গিতে নিজস্বতার ছাপ আছে। একটু লক্ষ্য করলেই চেনা গলার আমেজ পাওয়া যায়। (ক্রমশ)
Advertisement