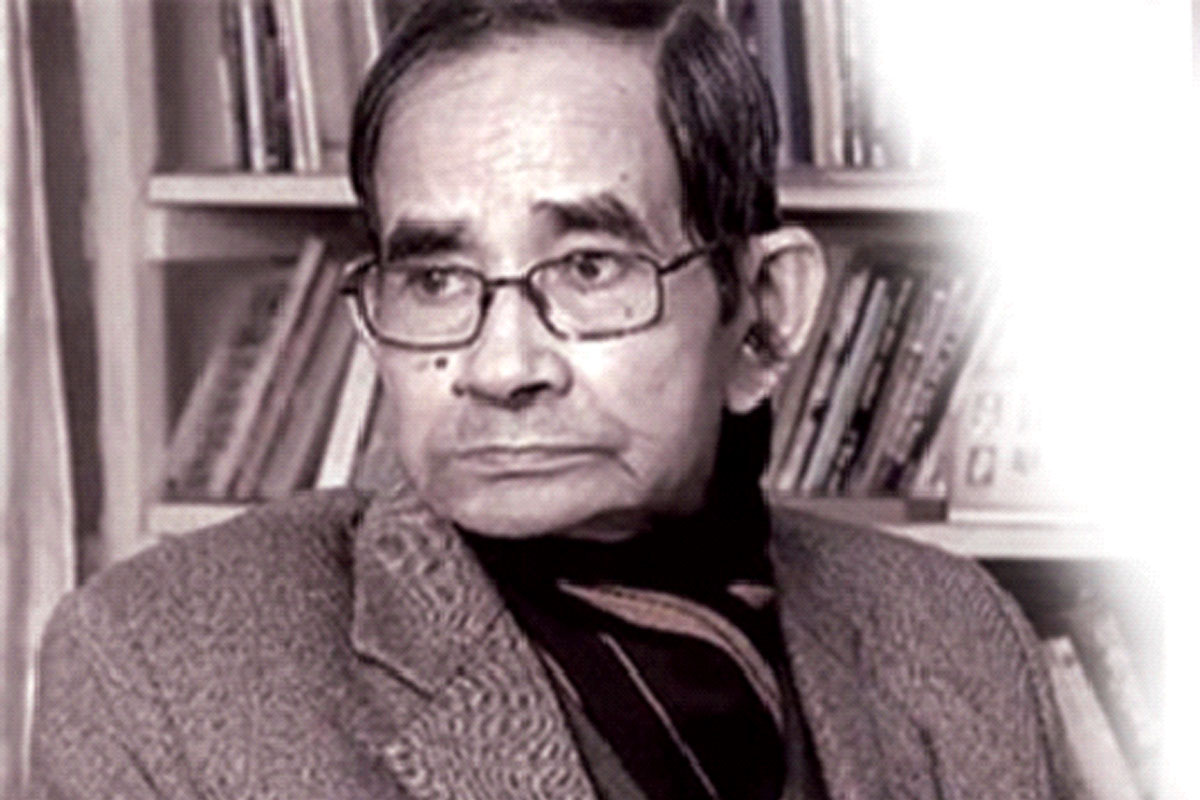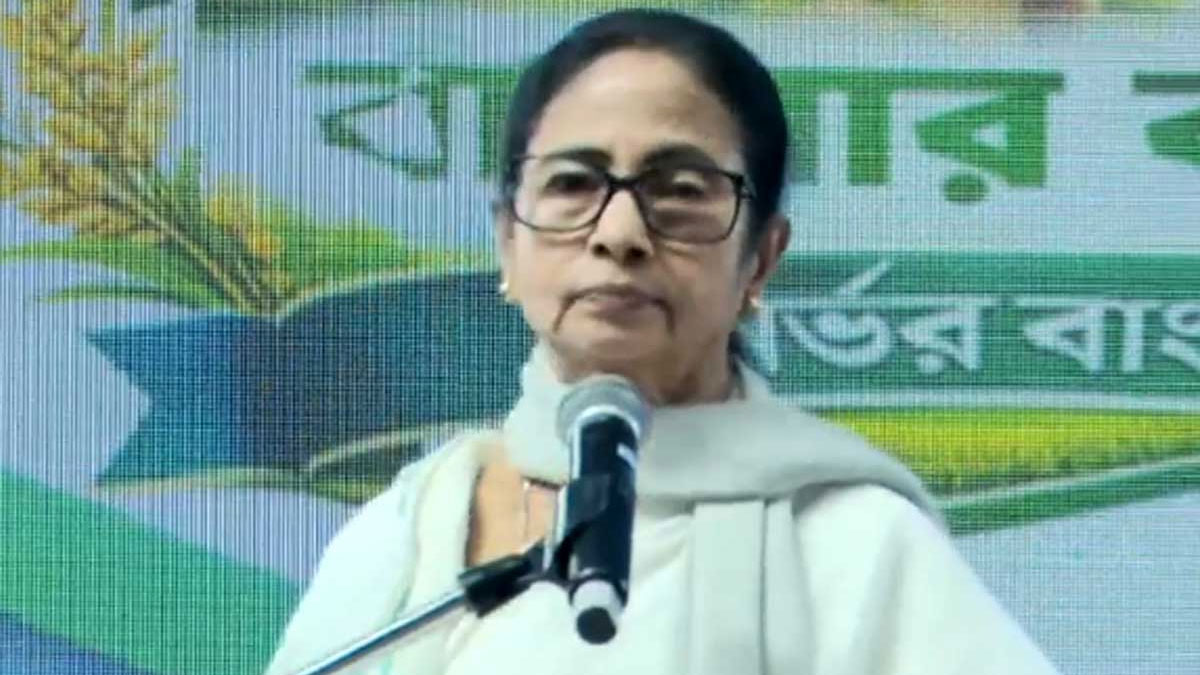হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
পূর্ব প্রকাশিতর পর
Advertisement
তাঁরা শরৎচন্দ্রের ভাষাকেই অনুকরণসাধ্য ও অনুকরণযোগ্য মনে করেছেন। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক অনুজরা ভাষার দিক থেকে সকলেই তাঁর অনুগামী। অবশ্য প্রতিভাবান সার্থক লেখকদের নিজস্ব কিছু ঢং বা বৈশিষ্ট্য থাকবেই। তা মেনে নিয়েও বলতে বাধা নেই যে তারাশংকর থেকে শুরু করে আশাপূর্ণা দেবী পর্যন্ত অদ্যাবধি আমাদের গল্প উপন্যাস যে ভাষায় লেখা হয়ে আসছে সে ভাষার বুনিয়াদটা শরৎচন্দ্রই গড়ে দিয়েছেন। কোনো কোনো লেখক বাক্যালাপে আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ করে কিঞ্চিৎ নতুনত্বের সঞ্চার করেছেন। তাছাড়া শরৎচন্দ্র লিখেছেন প্রধানত সাধু ভাষায়। আজকাল সকলেই লিখেছেন চলিত ভাষায়। তবে ঐ যে বলেছি, শরৎবাবুর গল্প যেমন ঘরোয়া, তাঁর ভাষাও তেমনি ঘরোয়া। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে ঐ ঘরোয়া ভাষার ব্যাকারণটুকুই সাধু ভাষার, আচরণটি চলিত ভাষার। বাংলা গদ্যের উপরে শরৎচন্দ্রের প্রভাব কত বড়, তার প্রমাণ যে সে-প্রভাব এখনও বিদ্যমান।
Advertisement
সবুজপত্রের পরেই ‘কল্লোল’-এর আবির্ভাব। এও সেই যৌবন-জলতরঙ্গেরই কল্লোল। কল্লোল-গোষ্ঠী বয়সে নবীন, ভাবনায় চিন্তায়ও। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি নতুন, লিখনভঙ্গি আরোই নতুন। সত্যি বলতে কি, তাঁরা বাংলা সাহিত্যের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। বাংলা গদ্যের উপরেও তার প্রভাব কিছু কম নয়। কল্লোলগোষ্ঠী আসরে নেমেছিলেন পূর্বগামীদের বিরুদ্ধে একটা নালিশ নিয়ে। তাঁদের প্রধান অভিযোগ ছিল, পূর্বসুরিরা সাহিত্যকে অতি সম্ভ্রান্ত এবং উচ্চ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের মধ্যেই আবদ্ধ রেখেছেন। সাধারণ মানুষ তাঁদের সাহিত্যে অবহেলিত এবং উপেক্ষিত। বলা বাহুল্য তাঁদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রসাহিত্যকে তাঁরা অভিজাত আখ্যা দিয়ে জাতে ঠেলেছিলেন।
কিন্তু ভুললে চলবে না যে গল্পগুচ্ছের গল্পে রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম নিম্ন-মধ্যবিত্তের জীবন নিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন, গ্রাম্য গার্হস্থ্য জীবনের ছবি এঁকেছেন। এমন কি নিম্নতম শ্রেণীর ছিদাম রুই আর তার বউ চন্দরার মর্মান্তিক কাহিনী রবন্দ্রনাথই সর্বাগ্রে আমাদের শুনিয়েছেন। তবে নবীনদের মতে, রবীন্দ্রনাথ পথ দেখালেও সে পথে তিনি বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেননি। তাঁর অভিজাত জীবনের বেড়া ডিঙিয়ে শহরের ক্লেদাক্ত বস্তি জীবন বা গ্রামের দুঃসহ দুঃস্থ জীবনের প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করা তাঁর পক্ষে সম্ভবই ছিল না। নবীনেরা প্রত্যক্ষদর্শীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। দুর্গত বঞ্চিতদের জীবনকে তাঁরা কাছে থেকে দেখবার জানবার চেষ্টা করেছেন, দরদি মন দিয়ে তাদের সম্বন্ধে লিখেছেন এবং সে কাজ তাঁরা কৃতিত্বের সঙ্গেই করেছেন। ‘কল্লোল, ’কালিকলম’ গোষ্ঠী সাহিত্যকে সকল প্রকার কৌলীন্যবোধ থেকে মুক্ত করতে চেয়েছেন। এক সময়ে বিষয়বস্তু সম্পর্কেও অনেক লেখকের মনে কিছু শুচিবাই ছিল। তাঁরা সকল জিনিসকে সাহিত্যের মর্যাদা দিতে রাজি ছিলেন না। নবীনেরা কোন ব্যাপারেই সাহিত্যের এক্তিয়ার বহির্ভূত মনে করতেন না। ভাষার বেলায়ও তাঁদের কোনো শুচিবাই ছিল না। সকলেই সুশিক্ষিত, সকলেই ভালো বাংলা লিখেছেন। ভাষা অবশ্যই রবীন্দ্র-গদ্য-অনুসারী। কিন্তু কথাবার্তার বেলায় অনেক সময় আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেছেন। তারাশংকরের গল্পে এখানে ওখানে বীরভূমি কথার ব্যবহারে কাহিনী এবং ভাষা দু-ই অধিকতর প্রাণবন্ত হয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মা নদীর মাঝি’ গ্রন্থে সমস্ত বাক্যালপই পূর্ববঙ্গের (ঢাকা জেলার) গ্রাম্য ভাষায় লেখা। মানিকবাবু খুবই শক্তিমান লেখক কিন্তু উক্তরূপ ভাষা প্রয়োগের নতুনত্বের চমক যতখানি, শক্তিমত্তার পরিচয় ততখানি নয়। এর ফলে ভাষার শক্তিবৃদ্ধি কিছু হয় নি; বরং তারাশংকরবাবু এবং অন্যান্য কোনো কোনো লেখক যে বিশেষ বিশেষ চরিত্রের মুখে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার করেছন তাতে একদিকে যেমন একটু বাস্তবতার সুর লেগেছে, অপরদিকে তেমনি ভাষার বর্ণাঢ্যতা বেড়েছে।
প্রত্যেক ভাষায় ইডিয়ম বলে একটা জিনিস আছে। অশিক্ষিত সাধারণ মানুষদের জীবনযাত্রা, তাদের অভ্যাস বিশ্বাস, নানা সংস্কার, তাদের বাচনভঙ্গি এবং অশিক্ষিতপটুত্ব সম্বলিত তাদের রসালাপ— এই সমস্ত মিলিয়ে ঐ ইডিয়মের জন্ম।
(ক্রমশ)
Advertisement