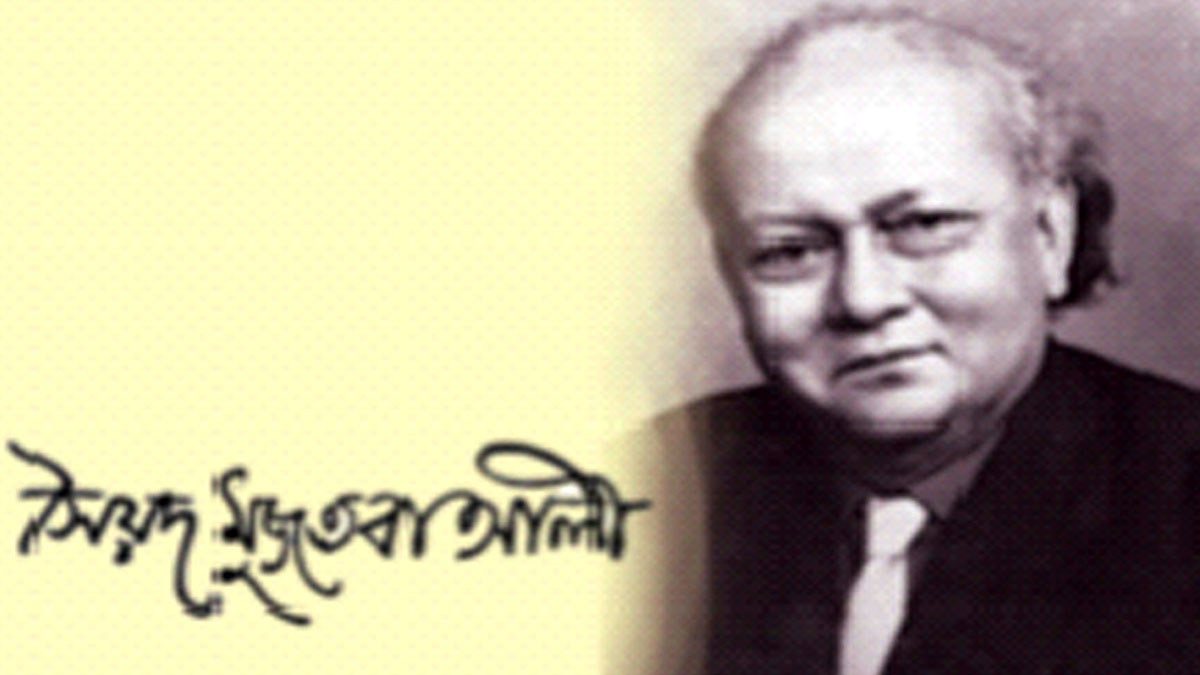পূর্ব প্রকাশিতর পর
পরবর্তী যুগে তিনি কুরানের শেষ অনুচ্ছেদ ‘আমপারা’ বাঙলা ছন্দে অনুবাদ করেন— হালে সেটি প্রকাশিত হয়েছে। সে পুস্তিকাতে তাঁর গভীর আরবী জ্ঞান ধরা পড়ে না— ধরা পড়ে তাঁর কবিজনোচিত অন্তর্দৃষ্টি এবং আমপারার সঙ্গে তাঁর আবাল পরিচয়। বিশেষ করে ধরা পড়ে, দরদ দিয়ে সৃষ্টিকর্তার বাণী (আল্লার ‘কালাম’) হৃদয়ঙ্গম করার তীক্ষ্ণ এবং সূক্ষ্ণ প্রচেষ্টা।
Advertisement
এরই উপর আমি বিশেষ করে জোর দিতে চাই। ফার্সী তিনি বহু মোল্লা-মৌলবীর চেয়ে কম জানতেন, কিন্তু ফার্সী কাব্যের রসাস্বাদন তিনি করেছেন তাঁদের চেয়ে অনেক বেশী। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই অনেক সংস্কৃত ব্যাকরণবাগীশদের চেয়ে কম সংস্কৃত জানতেন, কিন্তু তিনি লিরিকের রাজা মেঘদূতখানা জীবন এবং কাব্য দিয়ে যতখানি গ্রহণ করতে পেরেছিলেন ততখানি কি কোনো পণ্ডিত পেরেছেন? বহু লোকই বাঙলা দেশের মাটি নিখুঁতভাবে জরিপ করেছে, কিন্তু ঐ মাটির জন্য প্রাণ তো তারা দেয়নি। কানাইলাল, ক্ষুদিরাম ভালো জরিপ জানতেন একথাও তো কখনো শুনিনি।
Advertisement
কাজী রোমান্টিক কবি। বাঙলা দেশের জল-বাতাস, বাঁশ-ঘাস যে রকম তাঁকে বাস্তব থেকে স্বপ্নলোকে নিয়ে যেত, ঠিক তেমনি ইরান-তুরানের স্বপ্নভূমিকে তিনি বাস্তবে রূপানতরিত করতে চেয়েছিলেন বাঙলা কাব্যে। ইরানে তিনি কখনো যাননি, সুযোগ পেলেই যে যেতেন, সে কথাও নিঃসংশয়ে বলা যায় না (শুনেছি, পণ্ডিত হয়েও ম্যাক্সম্যূলার ভারতবর্ষকে ভালবাসতেন এবং তাই বহুবার সুযোগ পেয়েও এদেশে আসতে রাজী হননি।) কিন্তু ইরানের গুল্-বুল্বুল্, শিরাজী-সাকী তাঁর চতুর্দিকে এমনই এক জানা-অজানার ভুবন সৃষ্টি করে রেখেছিল যে, গাইড-বুক টাইমটেবিল ছাড়াও তিনি তার সর্বত্র অনায়াসে বিচরণ করতে পারতেন। গুণীরা বলেন, প্রত্যেক মানুষেরই দুটি করে মাতৃভূমি—একটি তাঁর আপন জন্মভূমি ও দ্বিতীয়টি প্যারিস। কাজীর বেলা বাঙলা ও ইরান। কীটস বায়রনের বেলা যে রকম ইংল্যাণ্ড ও গ্রীস।
আরবভূমির সঙ্গে কাজী সায়েবের যেটুকু পরিচয়, সেটুকু প্রধানতঃ ইরানের মারফতেই। কুরান শরীফের ‘হারানো ইউসুফের’ যে করুণ কাহিনী বহু মুসলিম অমুসলিমের চোখের জল টেনে এনেছে তিনি কবিরূপে তার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন ফার্সী কাব্যের মারফতে।
‘দুঃখ করো না, হারানো য়ুসুফ / কাননে আবার আসিবে ফিরে। / দলিত শুষ্ক এ-মরু পুনঃ / হয়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে।। / ইউসুফে গুম্গশতে বা’জ্ আয়দ ব্ কিনান্ / গম্ ম্-খূর। / কুল্বয়ে ইহ্ জান্ শওদ্ রূজি গুলিস্তান্ / গম ম্-খুর।।’
কাজী সায়েবের প্রথম যৌবনের রচনা এই ফার্সী কবিতাটির বাঙলা অনুবাদ অনেকেরই মনে থাকতে পারে। ‘মেবার পাহাড়, মেবার পাহাড়ে’র অনুকরণে ‘শাতিল আরব শাতিল আরব’ ঐ যুগেরই অনুবাদ।
কোনো কোনো মুসলমান তখন মনে মনে উল্লসিত হয়েছেন এই ভেবে যে, কাজী ‘বিদ্রোহী’ লিখুন আর যা-ই করুন, ভিতরে ভিতরে তিনি খাঁটি মুসলমান। কেনো কোনো হিন্দুর মনেও ভয় হয়েছিল (যাঁরা তাঁকে অন্তরঙ্গভাবে চিনতেন তাঁদের কথা হচ্ছে না) যে, কাজীর হৃদয়ের গভীরমত অনুভূতি বোধ হয় বাঙলার জন্য নয়— তাঁর দরদ বুঝি ইরান-তুরানের জন্য। পরবর্তী যুগে— পরবর্তী যুগে কেন, ঐ সময়েই, কবিকে যাঁরা ভালো ক’রে চিনতেন, তাঁরাই জানতেন, ইরানী সাকীর গলায় কবি যে বার বার শিউলির মালা পরিয়ে দিচ্ছেন তার কারণ সে তরুণী মুসলমানী ব’লে নয়, সে সুন্দরী ইরানের বিদ্রোহী কবিদের নর্ম সহচরী ব’লে— ইরানের বিদ্রোহী আত্মা কাব্যরূপে, মধুররূপে তার চরম প্রকাশ পেয়েছে সাকীর কল্পনায়।
(ক্রমশ)
Advertisement