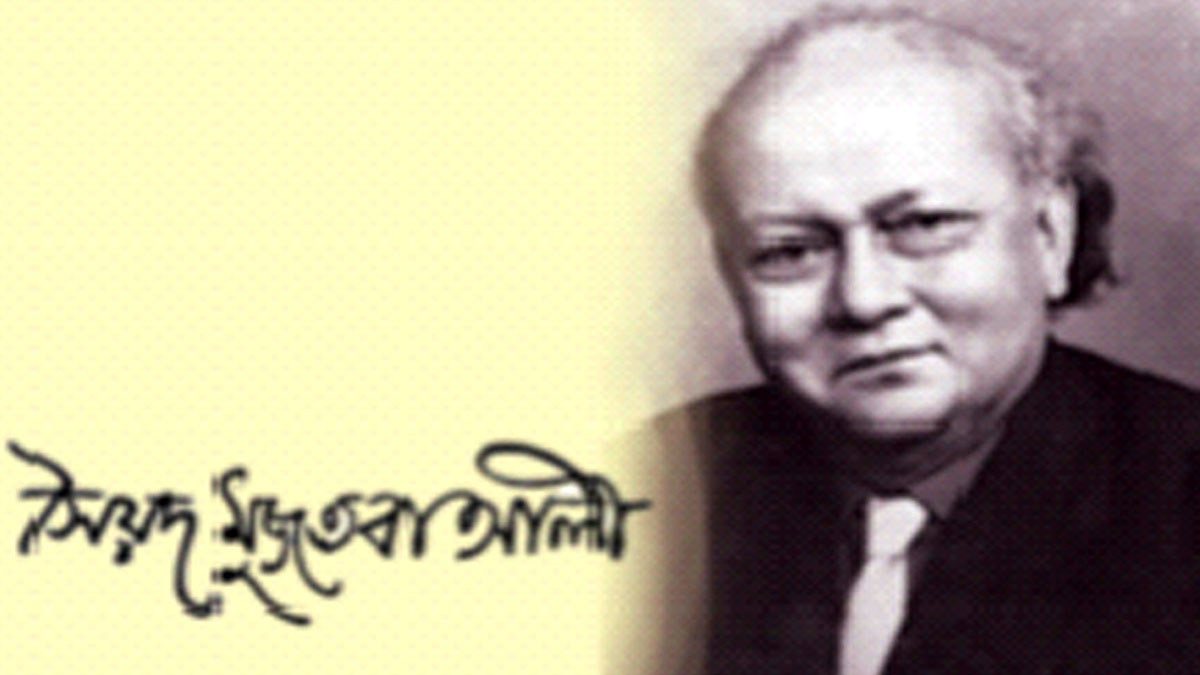পূর্ব প্রকাশিতর পর
এবং সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও জেনে যাই যে, একে আর কখনও ভুলব না। তাই তাঁর পাত্রপাত্রী দেশে কালে সীমাবদ্ধ নয়। দসতেয়ফস্কির চাষা কভাস ভদ্কা না খেলেও সে রুশ চাষা; তলস্তয়ের চাষা অন্তহীন স্তেপের উপর দিয়ে ভেঙে চলেছে বরফের পাথার, সরাইয়ে ঢুকেসে তার চামড়ার ছেঁড়া ওভারকোট স্টোভের পাশে শুকোতে দেয়, আইকনের সামনে বিড়বিড় করে সে মন্ত্র পড়ে ডান হতের তিন আঙুলে ডাইনে থেকে বাঁয়ে ক্রস্ করে, কিন্তু বারবার ভুলে যাই সে বাঙালী চাষা নয়। অবাক হয়ে ভাবি, বসিরুদ্দি, পাঁচু মোড়ল, নিজনি নভ্গরদের দিকে চলেছে কেন?
মহাভারতের পরেই উয়োর অ্যাণ্ড পীস্!
Advertisement
তুর্গেনেফ দসতেয়ফস্কির মতো প্রত্যেক চরিত্রের গোপনতম অন্ধকারে বিদ্যুল্লেখা দিয়ে আলোকিত করতে চান না। তার কারণ বোধহয় তুর্গেনেফ নখ্-শির, আপাদমস্তক ভদ্রলোক। কোনো ভদ্রলোক পরিচিত অপরিচিত কারও গোপন চিঠি পড়ে না—হাতে পড়লেও, কারও হাতে ধরা পড়ার ভয় না থাকলেও। ঠিক তেমনি তার চরিত্রের গোপন দুর্বলতা তার অজানাতে সে জানতে চায় না, প্রকাশ করতে তার মাথা কাটা যায়—সে তো দুশমনের কাজ, গোয়েন্দার ব্যবসা। ভদ্র তুর্গেনেফ তাঁর নায়কনায়িকার দিকে তাকান শিশুর মতো সরল চোখে; তারা কথাবার্তায়, আচার-ব্যবহারে যতখানি আত্মবিকাশ করে তাতেই তিনি সন্তুষ্ট, তাঁর পক্ষে সেই যথেষ্ট। শার্লক হোমসের মতো আতশী কাচ দিয়ে তিনি তার জুতোর দাগ পরীক্ষা করেন না, পোয়ারোর মতো তাকে ক্রস-এগজামিনেশনের ঠেলায় কোণ-ঠাসা করে অট্টহাস্য করে ওঠেন না, ‘ধরেছি, ধরেছি, তোর গোপন কথা কতক্ষণ লুকিয়ে রাখবি, বল্!’
Advertisement
অথচ শিশুর কাছে কেউ কোন জিনিস গোপন রাখে না। কবি মাত্রই শিশু। তার চোখে ছানি পড়েনি। প্রতিমুহূর্তে সে এই প্রাচীন ভুবনকে দেখে নবীন রূপে।
রুশদেশে পুশকিনের পর যদি কোনো কবি জন্মে থাকেন, তবে তিনি তুর্গেনেফ। তলস্তয় কবি সৃষ্টিকর্তা হিসেবে, আবিষ্কর্তারূপে, আর তুর্গেনেফ কবি অন্য অর্থে। পৃথিবীতে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু কুৎসিত, কিংবা যার দিকে কারও দৃষ্টি যায় না এসব-কিছু তিনি প্রকাশ করেছেন তাঁর কবিত্ব দিয়ে। তিনি অন্য কবির মতো অবাস্তবকে বাস্তব করেন না, বাস্তবকে অবাস্তব করেন না। বাস্তব অবাস্তব দুইই তাঁর কবি-মনের স্পর্শ পেয়ে আপন আপন সীমা ছাড়িয়ে তৃতীয় সত্তায় পরিণত হয়। ঘৃত-প্রদীপ শুষ্ক কাষ্ঠ দুইই তাঁর কবিত্বশিখার পরশে আগুন হয়ে জ্বলে ওঠে। কিংবা বলব, শীতের শিশির যেমন তার শুভ্র পেলব আস্তরণ দিয়ে মধুর করে দেয় সদ্য-ফোটা ফুলকে, শুকনো পাতার অঙ্গ থেকে ঘুচিয়ে দেয় তার সর্ব কর্কশতা। ওপারের ঝাউবন, এপারের কাশ, ঘাস, সর্বোচ্চ শাল-বকায়ন থেকে আরম্ভ করে রাস্তার পাশে নয়ানজুলি—সবাই যেন সূক্ষ্ণ মসলিনের অঙ্গাভরণ পরে সৌন্দর্যের গণতন্ত্রে কৌলীন্য পেয়ে গিয়েছে।
(ক্রমশ)
Advertisement