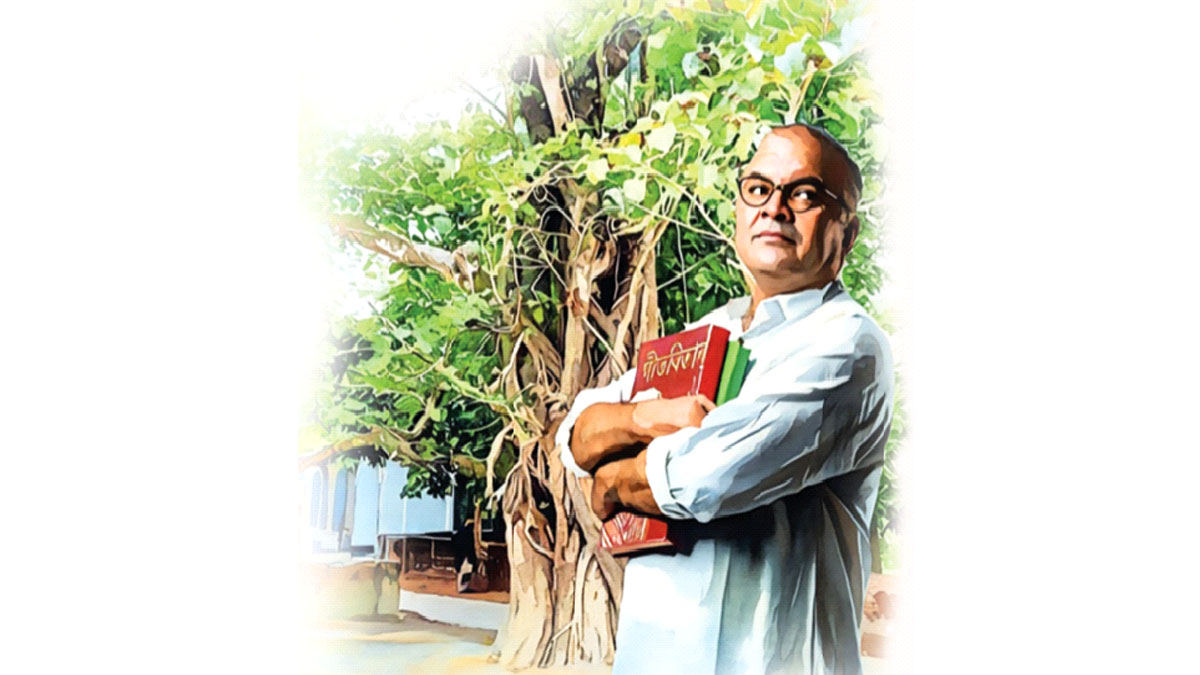কৃষ্ণা রায়
সাবিত্রীবাই ফুলে। বাঙালি সমাজে নেহাতই অচেনা এক নাম। সীতা, দ্রৌপদী, কুন্তীর মত স্মরণযোগ্য পৌরাণিক নারী তিনি নন, আবার ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের সঙ্গে কোথাও জড়িয়ে নেই তাঁর নাম। আদতে তিনি উনিশ শতকে মহারাষ্ট্রের এক পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর নারী, একটি শূদ্র পরিবারের বধূ, আর মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত সমাজ– সংস্কারক মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলের সার্থক সহধর্মিণী। কিন্তু স্বামীর পরিচয়ে নয়, ভারতে নারী শিক্ষার ইতিহাসে তিনি নিজেই নিজের পরিচয় তৈরি করে গেছেন। বিগত ২০১৪ সালের ৯ই অগাস্ট মহারাষ্ট্রের পুণা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম হঠাৎ বদলে গিয়ে হল সাবিত্রীবাই ফুলে পুণে ইউনিভার্সিটি।
Advertisement
কিন্তু কে এই সাবিত্রীবাই ফুলে? উত্তরে বলা যায়, তিনি উনিশ শতকের ব্রিটিশ শাসিত ভারতে প্রথম শিক্ষয়িত্রী, যিনি নিম্নবর্ণের অত্যাচারিত, বঞ্চিত নারীদের চোখে শিক্ষার আলো জ্বেলে দেওয়ার সাহস দেখিয়েছিলেন। প্রান্তিক জনজীবনের সামাজিক অধিকার আর নারীর স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছেন সারাজীবন। মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য যেমন একের পর এক স্কুল খুলেছেন, প্রয়োজনীয় ও যুগোপযোগী বিষয়ে পাঠ দান করেছেন, তেমনি তাদের সামাজিক-মানবিক অধিকার, জীবনের মান উন্নয়নের স্বার্থে গড়ে তুলেছেন মহিলা সেবা মন্ডল। আর অজস্র ধরণের সামাজিক কুপ্রথা, অপপ্রথার বিরুদ্ধে বারে বারে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। অথচ ভারতে শিক্ষাচর্চার ইতিহাসে তিনি তেমন ভাবে উচ্চারিত নন। যে সাহসে ভর করে অশিক্ষা-কুসংষ্কার ঘেরা আঁধার-মোড়া সময়ে অন্ত্যজ সমাজে তিনি শিক্ষার জোয়ার এনেছিলেন, পশুর অধম জীবন যাপনে বাধ্য এবং অভ্যস্ত নারীর কানে মানব অধিকারের বার্তা শুনিয়েছিলেন, শাস্ত্র ঘোষিত পাপের কথা নস্যাৎ করে তাদের শিক্ষার অধিকারে প্রাণিত করে জীবনে আলোর খবর দিয়েছিলেন, সেই সাহসের অনেকটাই যুগিয়েছিলেন ছিলেন তাঁর আধুনিকমনা স্বামী, যিনি নিজেও জাতিভেদ প্রথা ও হৃদয়হীন ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রের বিরুদ্ধে জীবন ভোর আন্দোলন করে গেছেন। ভারতীয় সমাজ সাবিত্রীবাইয়ের মহতী কর্মধারা সম্বন্ধে খুব বেশি ওয়াকিবহল নয়। অথচ উনিশ শতকের না্রী সাবিত্রী শুধু নিজে কষ্ট করে শিক্ষিত হননি, সমাজের তুমুল বিরোধিতা উপেক্ষা করে সেই শিক্ষা অন্যদের দিয়েছেন, সেই শিক্ষার অধিকারে সমাজ-কৃত অত্যাচার অসম্মানকে উপেক্ষা করে সোজা পথে এগিয়ে গেছেন, মূক মেয়েদের কন্ঠ হয়ে উঠেছেন। সেই অর্থে তিনি একজন মৌলিক নারীবাদী। দুর্ভাগ্যক্রমে নারীবাদের ইতিহাস আলোচনায় ভারতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায় বারে বারে মেরি উলস্টোনক্রাফটের নাম উচ্চারণ করলেও সাবিত্রীবাইকে তেমনভাবে স্মরণ করেন না।
জন্মেছিলেন ১৮৩১ সালের ৩ জানুয়ারি। মহারাষ্ট্রের পশ্চিম ভাগে সাতারা জেলার একটি ছোট্ট গ্রাম, নাম নয়গাঁও। পুণা শহর থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে এই নয়গাঁও গ্রামটি সাতারা আর পুণা (বর্তমানের পুণে) রোডের মধ্যে পড়ে। সে গ্রামে ব্রাহ্মণদের দাপট ছিল যথেচ্ছ। গরীব চাষী খান্ডোজি আর মা লক্ষ্মী বাইয়ের প্রথম সন্তান সাবিত্রী। ছোট থেকেই সে ভারী বুদ্ধিমতী আর বড়ই হুঁশিয়ার। সব কিছু জেনে বুঝে না নিলে তার যেন শান্তি নেই। গরীব শূদ্র পরিবারের মেয়েদের ইস্কুলে পাঠানোর নিয়ম নেই। কিন্তু মেয়ের যে চারপাশের জগত নিয়ে বড়ই কৌতুহল। বড়দের মুখে গল্প শোনে, তাদের গাঁয়ের থেকে দূরে অনেক বড় বড় শহর আছে। কিন্তু সাবিত্রী তো কোথাও যেতে পারে না। ভাইয়েরা গাঁয়ের স্কুলে যায়, তার বেলাতেই যত বারণ। বাড়িতে বসে মায়ের কাছে শিখতে হয় রান্নার কাজ, ঘরকন্নার কাজ। গাঁয়ের বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধুলো, হাসি, গল্প, পুকুরের জলে সাঁতার কাটা সবই তার দিব্যি লাগে। বয়সে ছোট হলেও সাবিত্রী বোঝে সমাজে উঁচুতলার মানুষ, মানে গোঁড়া ব্রাহ্মণেরা তাদের খুব ঘৃণা করে। তারা নাকি নিচু জাতের। জাত কীকরে উঁচু -নিচু হয়, ছোট্ট সাবিত্রী বোঝে না। তাদের গাঁয়ে আছে আরো অনেক জাতের মানুষ– মাহার, মাংগ, ছাম্বার, ভাঙ্গি, ঢেড। তারা নাকি সবাই ছোট জাতের। বড় জাতের মানুষ শুধু ওই ব্রাহ্মণেরা। তাদের হাঁটবার পথ দিয়ে সাবিত্রী আর তার বন্ধুরা হাঁটতে পারে না। ব্রাহ্মণদের কথামত তাদের সমাজের লোকেরাও বলে, মেয়েরা ইস্কুলে পড়াশুনো শিখতে গেলে পাপ হবে।
Advertisement
সালটা ছিল ১৮৪০। সেকালের নিয়ম অনুযায়ী নয় বছরের সাবিত্রীর সঙ্গে তেরো বছরের জ্যোতিরাওয়ের বিয়ে হয়ে গেল। জ্যোতিরাওদের পারিবারিক পেশা ছিল সবজির। পারিবারিক পদবী গোরহে। পেশোয়া সম্প্রদায়ের ফুলের যোগানদার হয়ে ওঠার সুবাদে তারা পরিচিত হতে লাগল গোরহে থেকে ফুলে। সাবিত্রীর জীবনের মূল সূত্র গড়ে উঠেছে তার স্বামীর জ্যোতিরাও ফুলের অবদানে। জ্যোতিরাও অনুভব করেছিল, তার অক্ষরজ্ঞান-হীন বালিকা-বৌটি লেখাপড়া শিখলে দারুণ খুশি হবে। তাই নিজে ইস্কুলে গিয়ে যা কিছু শিখেছে, বাড়ি ফিরে বৌকে সেগুলোই শিখিয়ে দেয়। স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে সাবিত্রীও ছয় বছর ধরে বাড়িতেই পড়াশুনো করেছে। যে সময় মেয়েদের গরু-ছাগলেরও অধম ভাবা হোত, দিবারাত্র গৃহশ্রমিক আর যৌনশ্রমিকের অতিরিক্ত কিছু ভাবা হত না, সমাজে মানুষ হিসেবে কোন ভূমিকা স্বীকৃত ছিল না, সেই দুঃসময়ে তরুণ স্বামী জ্যোতিরাও তার বালিকা স্ত্রীকে ঘরের কাজ থেকে কিছু সময়ের জন্য অব্যাহতি নিয়ে পাঠে-লেখায় মনোনিবেশ করার আদেশ দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, উনিশ শতকের কুসংষ্কার আচ্ছন্ন মহারাষ্ট্রে একটি তথাকথিত নিম্নবর্গের যুবক, নিজের স্ত্রীর শিক্ষার দায়িত্ব তুলে দিলেন অনাত্মীয় দুই যুবকের হাতে। স্ত্রীকে পড়তে পাঠালেন পুণেতে মিসেস মিশেলের নরম্যাল স্কুলে, পরে শিক্ষিকা হওয়ার প্রশিক্ষণ নিতে পাঠালেন আহমেদনগরে আমেরিক্যান মিশনারিদের প্রতিষ্ঠানে। ১৮৪৬-৪৭ সালে সাবিত্রী স্কুলের তৃতীয় এবং চতুর্থ বর্ষের পরীক্ষায় কৃত্কার্য হলেন। এরই পরিণতিতে হয়ে উঠলেন ভারতের প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক, দেশীয় নারী-শিক্ষিকা। খ্রিশ্চান মিশনারিদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এক পরিচয় নিয়ে। এবং অবশ্যই অন্তঃপুরের বাইরে এসে প্রকাশ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। স্কুলে পড়াতে যাওয়ার পথে স্থানীয় মানুষেরা তার দিকে ছুঁড়ে দিয়েছে গোবর, পাথর, মাটির ঢেলা। সাবিত্রী বিচলিত হন নি। সমাজে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির কন্যা সাবিত্রীর মধ্যে ছিল এক আশ্চর্য তেজ। উদারচেতা স্বামীর সাহচর্যে এসে শিক্ষাদানকে জীবনের পরম ব্রত বলে মেনেছিলেন। শিক্ষার মাধ্যমে নারীর প্রতি সমাজের বুকে ঘটে চলা অজস্র অর্থহীন অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোকে মানব জীবনের সারসত্য বলে বিশ্বাস করেছেন। প্রায় দেড়শ বছরের বেশি আগেকার সময়ে সাবিত্রীর দেখানো শিক্ষা পদ্ধতি আজো কত প্রাসঙ্গিক, কয়েকটি নমুনা দিলেই বোঝা যাবে। অধুনা প্রচলিত শিক্ষা সহায়ক বিভিন্ন উদ্দীপক, যেমন সর্ব শিক্ষা অভিযান, শিক্ষার অধিকার সংক্রান্ত আইন, মিড ডে মিল, ইত্যাদিকে মোটেই আধুনিক ভাবনার ফসল বলা হয়ত যাবে না, কারণ ইতিহাসের তথ্য বলছে, এসবের অনেকাংশই সাবিত্রীর কালেই সূচনা হয়েছিল। এমনকি গরীব শিক্ষার্থীদের স্কুলছুট এড়াতে তিনি স্টাইপেন্ড বা জলপানি দেওয়ার কথা ভেবেছিলেন। ছাত্রীদের উৎসাহ দিয়েছিলেন, স্কুলের প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশান অনুষ্ঠানে ব্যক্তিগত উপহারের পরিবর্তে স্কুলের জন্য গ্রন্থাগারের ব্যবস্থার জন্য আবদার জানাতে। এই সাবিত্রী সর্বার্থেই এক মরমী শিক্ষয়িত্রী, উনিশ শতকের আঁধারে, আলো হাতে পথচলা এক ক্লান্তিহীন যাত্রী।
ব্যক্তিগত জীবনে সাবিত্রী ছিলেন সহজ জীবনাচরণে বিশ্বাসী। শিক্ষাব্রতী এই নারী আটপৌরে জীবনে আর পাঁচটি গৃহবধূর মতই ছিলেন সহজ, অনাড়ম্বর। সাজপোশাকে পারিপাট্য-বিমুখ সাবিত্রীর কপাল জুড়ে আঁকা থাকত বিরাট কুমকুমের টিপ, অলংকারহীন দেহে থাকত শুধু একটি মঙ্গলসুত্র আর কালো সুতো, পুঁতি দিয়ে গাঁথা একটি কন্ঠবেষ্টনী। মাঝারি চেহারার সাবিত্রী দেখতে ছিলেন বেশ সুশ্রী, স্বভাবে ধীর স্থির, শান্ত। লোকে তাঁকে রাগতে দেখেনি। সারাক্ষণ ঠোঁটের গোড়ায় লেগে থাকত একটুকরো অধরা, রহস্যময় হাসি। বাড়িতে অতিথি সমাগম হলে তাঁর আনন্দের সীমা থাকত না। নিজে উদ্যোগ নিয়ে তাদের জন্য সুখাদ্য রান্না করতে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। স্বামীর সঙ্গে দীর্ঘ একান্ন বছরের দাম্পত্য জীবনও পালন করেছেন নিরবচ্ছিন্ন শ্রদ্ধায়, বিশ্বাসে। দায়ে-অদায়ে পারস্পরিক সাহচর্যে, ভালবাসায়, আজীবন তাদের মনের বন্ধন ছিল সৌন্দর্যময়, সুগভীর। স্বামীর সমাজ উন্নয়নের লক্ষ্যে ও ব্রতে যথার্থ সহযোগী ছিলেন সাবিত্রী। ভারতে নারী শিক্ষার দুই অগ্রপথিকের দাম্পত্য জীবনও ছিল পারস্পরিক সমমর্মিতায় ভরা।
নিঃসন্তান জ্যোতিরাওয়ের জীবনে এক সময় পারিবারিক তথা সামাজিক চাপ প্রবল হয়ে দেখা দিল। সন্তান লাভের জন্য তাঁকে আবার বিবাহ করতেই হবে। জ্যোতিরাও এমন কাজে পা বাড়াতে নারাজ। এতে তাঁর জীবন সঙ্গীর অসম্মান হবে। সাবিত্রীও তখন যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। সমাজের নির্দয় ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করে নিঃসন্তান সাবিত্রী অনাথ আশ্রম স্থাপনে আগ্রহী হয়েছেন। তাঁর মাতৃত্ব এই সামাজিক দায়িত্বের মধ্যে আনন্দের, তৃপ্তির পথ খুঁজে নিয়েছে। আশে পাশের এলাকার শিশুদের প্রায়ই তাঁর নিজের বাড়িতে খাবার খেতে নিমন্ত্রণ করতেন। এইসব শিশুদের সান্নিধ্যে তাঁকে খুব সুখী মনে হত। আত্মহত্যা করতে উদ্যত এক অন্তঃসত্ত্বা ব্রাহ্মণ-বিধবার প্রাণ বাঁচিয়ে তার জারজ সন্তানকে দত্তক নিয়েছিলেন সেই ১৮৭৪ সালে। মায়ের মমতায় পালিত এই পুত্র পরিণত জীবনে হয়েছিল চিকিৎসক। এই পুত্রের বিবাহের ব্যবস্থা করেছিলেন, যা ছিল প্রকৃতপক্ষে আরেকটি সমাজ সংষ্কার, আন্তঃজাতি বিবাহ।
এই অবসরে সাবিত্রীর এই কল্যাণমূলক কাজের একটি উল্লেখ করতেই হয়। ১৮৭৫-৭৬ সালে পশ্চিম মহারাষ্ট্রে এক ভয়ানক খরা দেখা দিয়েছিল। এই বিয়োগান্ত মুহূর্তে লোভী, অসাধু সুদখোর মহাজনেরা সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। গরীব চাষীদের খাবার আর সাহায্যের বিনিময়ে তাদের কাছে প্রতারণার টোপ ফেলত। সাবিত্রীর নেতৃত্বে সত্যশোধক সমাজের স্বেচ্ছাসেবীরা তাদের ত্রাণের কাজে এগিয়ে এল, তাদের প্রাণ এবং সম্পত্তি বাঁচানোর কাজে সর্ব শক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সুদখোর মহাজনেরা বিপদ বুঝে এদের বিরুদ্ধে প্রশাসনের কাছে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করল, এরা নাকি দাঙ্গা বাঁধানোর কাজে নেমে পড়েছে। স্বেচ্ছাসেবীদের পুলিশ অ্যারেস্ট করল। এই ঘৃণ্য ঘটনার প্রতিবাদে সাবিত্রী প্রতিনিধি জড়ো করে, নেত্রীর ভূমিকা নিয়ে, স্থানীয় কালেক্টারের অফিসে গিয়ে সবিনয়ে অসাধু মহাজন এবং পুলিশ প্রশাসনের অসৎ-ব্যবহারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করলেন। সাবিত্রীর স্পষ্ট ও ঋজু কথায় এবং ঘটনার সত্যতা যাচাই করে কালেক্টার সাহেব বিচলিত হলেন। স্বেচ্ছাসেবীদের তৎক্ষণাৎ মুক্তি দিলেন। সাবিত্রীর সাহস ও দায়িত্ব বোধের প্রচুর প্রশংসা করে ব্যক্তিগত ভাবে কালেক্টার সাহেব, নিজেও এই ত্রাণের কাজে এগিয়ে এলেন।
সাবিত্রী ছিলেন মনে প্রাণে কবি। মারাঠী ভাষার প্রথম স্বীকৃত মহিলা কবি। যে সব সমাজ সচেতন মানুষ জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে মুখর হয়েছেন, সাবিত্রীর কবিতা তাঁদের বিশেষ ভাবে প্রেরণা জুগিয়েছিল। মাত্র তেইশ বছর বয়সে, ১৮৫৪ সালে প্রকাশ পায় তাঁর লেখা কবিতার বই ‘কাব্যফুলে (Poetry’s Blossoms)’। সময়ের মাপকাঠিতে এই বইয়ের প্রকাশ নিঃসন্দেহে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। উনিশ শতকের মধ্যভাগে মহারাষ্ট্রে কোন মহিলাকে প্রকাশ্যে কিছু বলতে শোনা যেত না, তাদের লেখালেখি তো স্বপ্নের বিষয়। সাবিত্রীর জীবনীকার এম জি মালি তাঁকে ‘The mother of modern Marathi poetry’ বলে উল্লেখ করেছেন। সাবিত্রীর মানস প্রকৃতিতে যে বহুবিধ আলোছায়া ছিল, তারই প্রকাশ ঘটেছে তাঁর কবিতায়। সচেতন ভাবেই তিনি কবিতা রচনায় প্রথাগত মারাঠী রচনার ভঙ্গিকে (‘অভঙ্গ’) আশ্রয় করেছেন। এই অভঙ্গ হল প্রকৃতপক্ষে একটি লোক-সাহিত্যের রূপ, যার মাধ্যমে ঈশ্বরকে নিবেদন করে প্রশংসাসূচক গান লেখা বা করা হয়। বইটিতে রয়েছে এক চল্লিশটি কবিতা। প্রকৃতি, জাতিভেদ প্রথার মত সামাজিক সমস্যা, জাতিভেদ জনিত দাসত্ব থেকে মুক্তি, শিক্ষা, ঐতিহাসিক সত্য সবই তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু হয়েছে। উপদেশমূলক কবিতা রচনায়ও তাঁকে সমান স্বচ্ছন্দ মনে হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে কবিতার ভাষা সহজ, নিরলঙ্কার। সাবিত্রীর কবিতা তাঁর জীবন বোধের পরিচায়ক। হিন্দু সমাজ জীবনের আদি নিয়ন্ত্রক মনুকে নিয়ে কবিতায় তাঁর ভাষা বেশ তির্যক।
যারা মাঠে কাজ করে, ফসল ফলায়
মনু বলেন, তারা ভোঁতা
বস্তুত ব্রাহ্মণদের জন্য নির্দিষ্ট এটিই হয়ে আছে
মনুস্মৃতি বলে, মাঠে শ্রম দিও না।
স্বামীকে লেখা সাবিত্রীর ব্যক্তিগত চিঠিগুলির ঐতিহাসিক মূল্য কম নয়। এগুলি শুধু চিঠি নয়, সাহিত্যমূল্যেও বিরল এক সম্পদ। সে সময় মহারাষ্ট্রের প্রান্তিক সমাজে মেয়েদের চিঠি লেখা একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা, স্বামীকে লেখা তো দূরস্থান। কুড়ি বছর সময় কালে স্বামীকে লেখা তিনটি চিঠির হদিশ পাওয়া যায়, এগুলি লেখা হয়েছিল অটুর এবং নয়গাঁও থেকে। এই সব চিঠি থেকে সমকালের নারীর যাপনচিত্র এবং অভিজ্ঞতার তথ্য পাওয়া যায়। স্বামী জ্যোতিরাওয়ের চারটি ভাষণ তথা বক্তৃতার সংকলন সম্পাদনা করেও প্রকাশ করেন সাবিত্রী।
সারাজীবন বিচিত্র বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন সাবিত্রী। শিক্ষাদান, সদাচারণ, নেশা, ঋণ গ্রহণে বিশেষ উৎসাহ, এ ধরনের বহুবিধ বিষয়ে। ১৮৯২ সালে সাবিত্রীর নিজের বক্তৃতার এই সংকলন প্রকাশিত হয় ‘Speeches of Matoshree Savitribai’ শিরোনামে, বরোদার বতসল প্রেস (Vatsal Press )থেকে।। একই বছর প্রকাশিত হয় ভবন কাশি সুবোধ রত্নাকর, (The Ocean of Pure Gems)। এটি একটি অন্যরকম গ্রন্থ। ভারতের ইতিহাস বিশেষত মারাঠা জাতির ইতিহাস এবং জ্যোতিরাওয়ের জীবন-কথা একাধিক কবিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। জ্যোতিরাওয়ের মৃত্যুর পর, ১৮৯১ সাল থেকে লেখা শুরু করেন। ৫২টি কবিতা দিয়ে সাজানো এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছ স্বামী জ্যোতিরাওয়ের কিছু গদ্য। মারাঠী কবিতার জগতে এই বইটিকে যথেষ্ট শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়।
১৮৯৭ সালে সারা পৃথিবী এক বিশেষ রোগের দাপটে নাজেহালহল, তার নাম বিউবোনিক প্লেগ। রোগের তৃতীয় ঢেউ ভয়ংকর ভাবে আছড়ে পড়ল মহারাষ্ট্রের নালাসোপারা অঞ্চলে। মাত্র এক বছর আগে দেশে ভয়ংকর খরা দেখা দিয়েছিল আর তারপরে আবার এক বিপর্যয়। পুণা শহরে প্রতিদিন শ’য়ে শ’য়ে লোক মারা যাচ্ছে। শহরে মহামারি লেগেছে। ব্রিটিশ শাসকেরা বিধান দিলেন জাতি হিসেবে সমাজের উচ্চ মার্গে অবস্থানকারী চিকিৎসকেরা সব জাতি-সম্প্রদায়ের রোগীদের চিকিৎসা করবেন। কিন্তু সমাজে উঁচু জাতের চিকিৎসকেরা শূদ্র অথবা দলিত সম্প্রদায়ের মানুষকে স্পর্শ করতে অথবা তাদের চিকিৎসা করতে রাজি হলেন না। সাবিত্রী সমাজসেবায় ব্যস্ত হলেন। স্বাভাবিক ভাবেই মহামারির সময় রোগীদের সেবার জন্য তিনি যশোবন্তকে সঙ্গী করলেন, তাকে অনুরোধ করলেন কাজ থেকে ছুটি নিয়ে আসতে। তৈরি করলেন একটি হাসপাতাল বা ক্লিনিক, পুণে শহরের বাইরে খোলামেলা জায়গায় হাডাস্পার-এ। রোগটি সংক্রামক জেনেও নিজেও খুঁজে খুঁজে মৃতপ্রায় রোগীদের হাসপাতালে নিয়ে আসেন, তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। একদিন খবর পেলেন দলিত মাহার গোষ্ঠীর পান্ডুরং বাবাজি গাইকোয়াড় এর ছেলে মুন্ডাহা গ্রামের বাইরে প্লেগে আক্রান্ত হয়েছেন। শোনামাত্র সাবিত্রী ছুটলেন সেখানে। ছেলেটিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসতে হবে। কোথাও কোনও সাহায্য না পেয়ে, নিজেই কোলে-পিঠে করে দশ বছরের অসুস্থ বাচ্চাটিকে হাসপাতালে ফিরলেন। শিশুটি সে যাত্রা রেহাই পেল কিন্তু তিনি নিজে সেই ভয়ংকর রোগের কবলে পড়লেন। বয়স তখন মাত্র ছেষট্টি। কত কাজের স্বপ্ন সাজিয়ে রেখেছিলেন। সব অসমাপ্ত রেখে শূদ্র ঘরের বীরাঙ্গনাটি ১৮৯৭ সালের ১০ মার্চ রাত নটার সময় তাঁর পার্থিব জীবনের ছন্দ চিরকালের জন্য থামাতে বাধ্য হলেন।
সাবিত্রীর মৃত্যুর পর দীনবন্ধু পত্রিকায় সেই খবর অত্যন্ত দুঃখ ও অনুশোচনা সহকারে প্রকাশিত হল। বলা হল, যাঁরা ঝাঁসির রাণি লক্ষ্মীবাইয়ের বীরত্ব, রণ-কৌশলের প্রশংসা করেন, আত্মজকে নিজের পিঠে চাপিয়ে যুদ্ধ করার কথা গৌরবের সঙ্গে স্মরণ করেন, তাঁরা কিন্তু ভুলে থাকেন আরেক মহিয়সীর কথা, যিনি প্লেগে আক্রান্ত অন্যের অসুস্থ বাচ্চাকে পিঠে চাপিয়ে সুস্থ করার চেষ্টায় আক্ষরিক অর্থে মরণপণ করেছিলেন।
১৮৪৮ সাল থেকে ১৮৯৭ সাল, প্রায় পঞ্চাশ বছর মানব-সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। তাই সাবিত্রীদের মৃত্যু হয় না। পার্থিব জীবনের ওপারে রয়ে যায় এক চিরকালীন অমর্ত্য জীবন। এ দেশের প্রতিটি মেয়ের লেখায়, চিন্তায়, কাজে রয়ে গেছেন সাবিত্রীবাই ফুলে। উনিশ শতকের অন্ধকার প্রহরে যে মানুষ মেয়েদের চোখে আলো ধরে দিয়ে তাদের শিক্ষিত, শক্তিময়ী করে আলোকিত সমাজের সূচনা করেছিলেন, তাঁকে ভুলে যাওয়া তো অপরাধ।
Advertisement