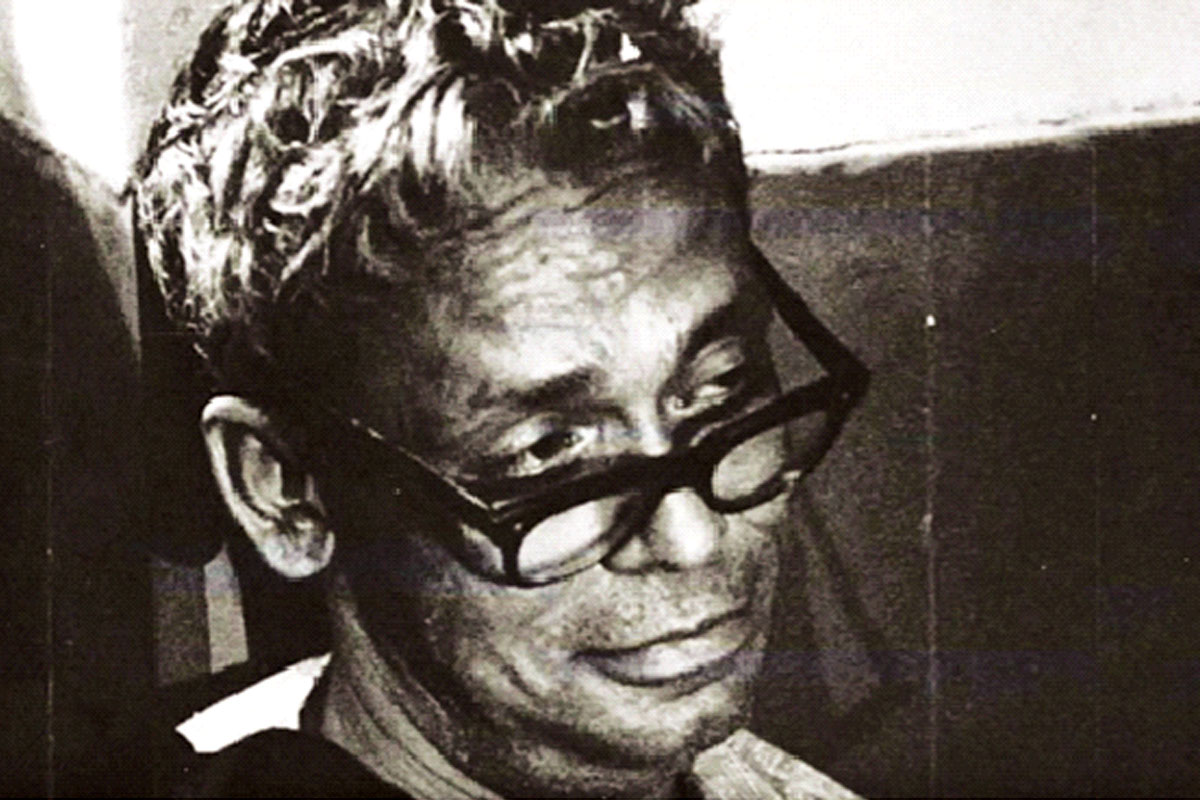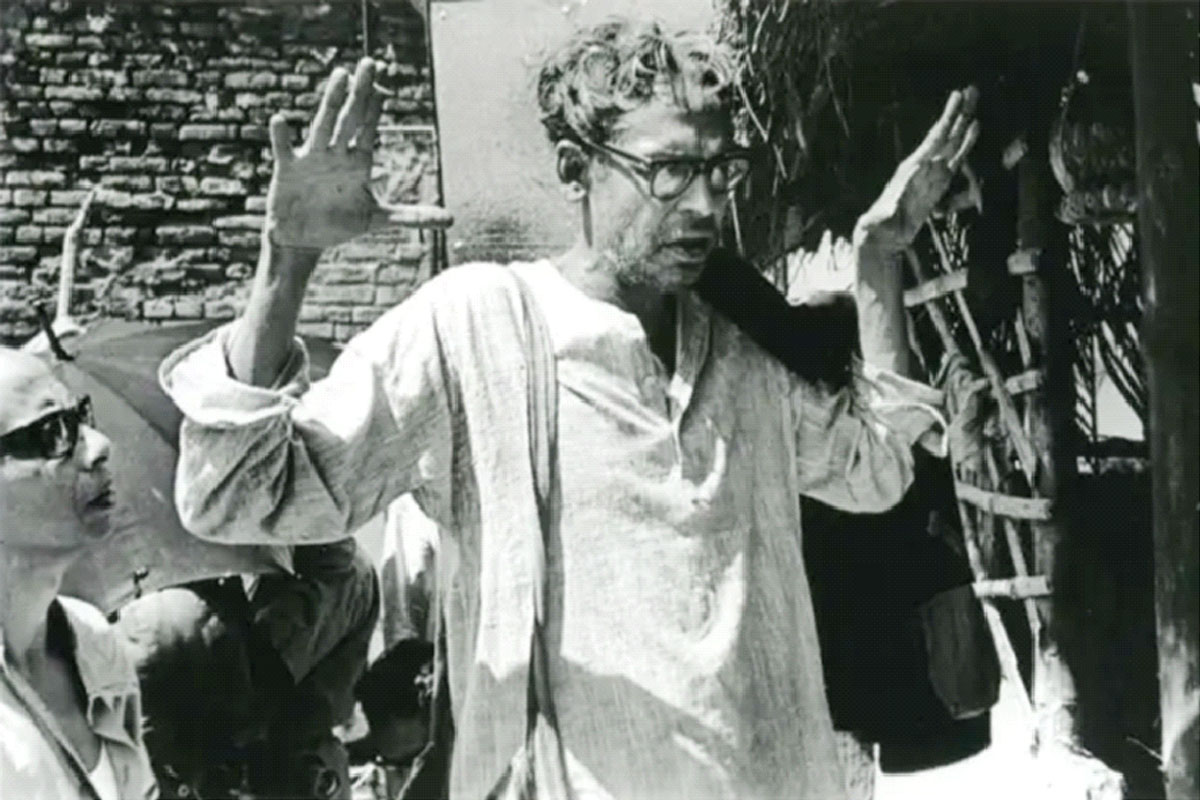সুব্রত রায়
ঋত্বিক ঘটকের জন্ম শতবর্ষে তাঁকে ও তাঁর শিল্পকর্মকে আবার নতুন করে মূল্যায়ন করার সময়। তাঁর কোমল গান্ধার ছবিতে ঋষি চরিত্রের মুখে একটি সংলাপ ছিল, নেতাদের সম্মান করা উচিত, আর টাইম টু টাইম তাদের পেছনে লাথি মারা উচিত। বর্তমান উত্তাল রাজনৈতিক আবহে এই ধরণের উক্তি যে কত প্রাসঙ্গিক তা আর নতুন করে বলার মতো কিছু বিষয় নয়।এটা একধরনের স্পর্ধা যা ঋত্বিক ঘটকেই মানায়। আবার যখন তিনি বলেন, সিনেমার থেকে বেটার কোন শিল্প মাধ্যম পেলে আমি সিনেমাকে লাথি মেরে চলে যাব।আবার যখন তিনি বলেন সিনেমাতে বিষয়ের যুগ শেষ হয়ে গেছে এসেছে বক্তব্যের যুগ।তখন চলচ্চিত্র সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব চিন্তা ভাবনার একটা সুষ্পষ্ট ছাপ আমরা দেখতে পাই।
Advertisement
এ এক অলৌকিক সমাপতন।১৯২৫ -এর যে হেমন্তের দিনে ঋত্বিক ঘটক জন্ম নিচ্ছেন ঢাকা শহরে,প্রায় তখনই সের্গেই আইজেনস্টাইন তাঁর কারুবাসনা ছড়িয়ে দিচ্ছেন মস্কো শহরে যুদ্ধজাহাজ পটেমকিনের সমবয়স্ক।তাই হয়তো ওডেসা সিঁড়ির বৃত্তান্তের মতোই তাঁরও জীবনবৃত্তান্তে রক্ত আর স্বপ্ন মিলেমিশে মৃত্যুকে ছলনা করে যায়।ঋত্বিক ঘটক প্রয়াত হন ১৯৭৬ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি।ঋত্বিক ঘটককে তাঁর স্বদেশবাসী প্রায় নিশ্চিত ভাবেই তাঁর পূর্বসূরি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাইকেল মধুসূদন দত্তের সঙ্গে একই বন্ধনীভুক্ত দেখতে চায়।তাঁর কর্মজীবনকে ধ্বংসের সারমর্ম হিসাবে বর্ণনা করা হলে আমরা বুঝে নেওয়ার অবসর কম পাই যে পশ্চিমের তারকোভস্কির মতো তিনি এখানে হাতে গোনা মাত্র কয়েকটি ছবির সূত্রেই হয়ে উঠেছেন আধুনিক চৈতন্যের অংশ।তাই যতটা তাঁর অতিরিক্ত মদ্যপান বিষয়ে আলোচনা হয়,ততটা আলোচনা হয় না তাঁর ছবিগুলি নিয়ে।
Advertisement
ঋত্বিক ঘটকের প্রথম ছবি নাগরিক (১৯৫২)।কিন্তু ছবিটি মুক্তি পায় পরিচালকের মৃত্যুর পরে।।অনেকে বলে থাকেন নাগরিক যদি ১৯৫২ সালে মুক্তি পেত,তবে ঋত্বিক এই উপ মহাদেশে পথিকৃতের সম্মান পেতেন।নাগরিক ঋত্বিকের প্রথম ছবি,কিন্তু এটি তত গুরুত্বপূর্ণ ছবি নয়,যা ঋত্বিকের মেধার বিচ্ছুরনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। তার দ্বিতীয় ছবি অযান্ত্রিক (১৯৫৮)। এটি ঋত্বিকের একমাত্র ছবি যা সর্বজন প্রশংসিত। এ ছবির নায়ক বিমল ছোটনাগপুর অঞ্চলে জগদ্দল নামে একটি পুরোনো শেভ্রল গাড়ি নিয়ে ভাড়া খাটে।জগদ্দল ছাড়া বিমলের দুনিয়ায় আর কেউ নেই।জগদ্দল তার মা,প্রেমিকা ও সঙ্গিনী। জীবনের লক্ষণ হলো মৃত্যু।বিমলকেও শেষমেশ জগদ্দল এর মৃত্যু মেনে নিতে হয়। খন্ড খন্ড ভাবে গাড়িটি বিক্রি হয়ে যায়। ছবির শেষে একটি শিশুর হাতে গাড়িটির হর্ন শুধু বাজতে থাকে।এটাই জীবনের ধর্ম। একটি প্রজন্ম শেষ হয়ে যায়,আরেকটি প্রজন্ম শুরু করে।তাঁর সবথেকে বিখ্যাত পর্যায় ‘মেঘে ঢাকা তারা’(১৯৬০),’কোমল গান্ধার’(১৯৬১), ‘সুবর্নরেখা’ (১৯৬২)।ছবির গল্পের অংশ নড়বড়ে, আরোপিত ও ভঙ্গুর। তিনি জানতেন শিল্প আপাত সত্যের প্রতিরূপ নয় বরং তা আমাদের পৌঁছে দিতে পারে প্রকৃত সত্যের কাছাকাছি।তাই এই অসম সাহসী পরিচালক দাবী করতে পারেন তাঁর ক্ষেত্রে সেন্টিমেন্টাল মেলোড্রামাটাও একটা ফর্ম। আর একটা কথা বলা যেতে পারে মেঘে ঢাকা তারা ছবিতে আমরা দেখি নীতা যখন পরিবারের দায়িত্ব নেয় তখন পুরুষ তান্ত্রিক সমাজ তা মেনে নিতে পারে না।তাই তার বিসর্জন অনিবার্য হয়ে পড়ে।তাই তার মুখে দাদা আমি বাঁচতে চাই এই সংলাপটি আসলে একধরনের আর্তনাদ। এই ছবিটি ঋত্বিকের সবথেকে জনপ্রিয় ছবি। ঋত্বিক ঘটকের পরবর্তী ছবি কোমল গান্ধার(১৯৬১)। চলচ্চিত্র কাহিনীর প্রয়োজনে তাই অনাস্থা জানিয়ে নিজেই হয়ে উঠল প্রবন্ধ ধর্মী। এই ছবিতে শাখা বিস্তার করেছে দেশবিভাগ।সঙ্গে আছে নাট্য আন্দোলন ও তার নানা স্তর নিয়ে একধরনের পরীক্ষা।এর সঙ্গে আছে অনসুয়া ও ভৃগুর সম্পর্ক। পরের ছবি সুবর্নরেখা (১৯৬২), যা একটি মহাকাব্যিক ছবি। যেখানে নতুন ভারতের সন্ধান করা হয়ে থাকে। এই তিনটি ছবিই আসলে দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে করা। কারন ঋত্বিক দেশভাগকে একেবারেই মেনে নিতে পারেননি। কিন্তু এর সঙ্গে এ কথাও সত্যি যে ঋত্বিক ঘটক তাঁর ছবিতে মিথ ও মিথলজিকে রিওয়ার্ক করিয়েছেন। তাই তাঁর ছবির চরিত্রদের নাম কখনো নীতা, সীতা বা অভিরাম। তাই তিনি বলেছিলেন দেশীয় ঐতিহ্য ও মহাকাব্য না জানলে তাঁর ছবি বুঝতে পারা বা অনুভব করা কঠিন হয়ে পড়বে। কারন তিনি যত বড় চিত্রপরিচালক, তার থেকে অনেক বড় একজন দার্শনিক। তাই তাঁর ছবি গুলোতে অনেক গুলো লেয়ার থাকে। দর্শক তাঁর ছবি সেই সময় বুঝতে পারেনি তার কারণ দর্শক সেই সময় ওই ধরনের ছবি বোঝার জন্য নিজে তৈরি ছিল না। এই হতাশা ও রাগের কারনে তাঁর ব্যাক্তি জীবন মোটেই সুস্থির ছিল না। একধরনের অস্থিরতা তাঁকে প্রতিনিয় কুরে কুরে খেত। কিন্তু তাঁর ছবির মধ্যে কোনরকম অসংলগ্নতা ছিল না। এটা আমাকে আজও ভাবায়। এই কারনেই তিনি জিনিয়াস।
ঋত্বিকের শেষ ছবি ‘যুক্তি তক্কো আর গপ্পো’ (১৯৭৩) এখানে নীলকণ্ঠ বাগচী কে তো আমার ঋত্বিকের অল্টার ইগো বলেই মনে হয়। ঋত্বিক সমগ্র জীবন ও রাজনীতিকে টেনে আনেন অণুবীক্ষনের নীচে। তাঁর মৃত্যুর পর ক্রমশ স্বদেশ ও বিদেশে ঋত্বিক চর্চার প্রসার ঘটেছে। এই চর্চাকে আমরা যতটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো সিনেমা নামক মাধ্যমটি ততটাই সম্প্রসারিত হতে পারবে। চলচিত্রের যে একটা নিজস্ব ভাষা আছে তা এইসব পরিচালকেরা বারবারই আমাদের মনে করিয়ে দেন। আর এটা যে শুধুমাত্র বিনোদন ও বাণিজ্যের উপকরণ নয়, আরও বেশি কিছু তা আমাদের মনে করিয়ে দেয়। আপেক্ষিক সাফল্য ও ব্যার্থতার থেকেও যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল ঋত্বিক চলচ্চিত্র কে একটি চিন্তনীয় বিষয় হিসাবে সকলের সামনে তুলে ধরলেন। ঋত্বিককে কোট করে বলতে হয়’, ভাবো ভাবো ভাবা প্র্যাক্টিস কর।
Advertisement