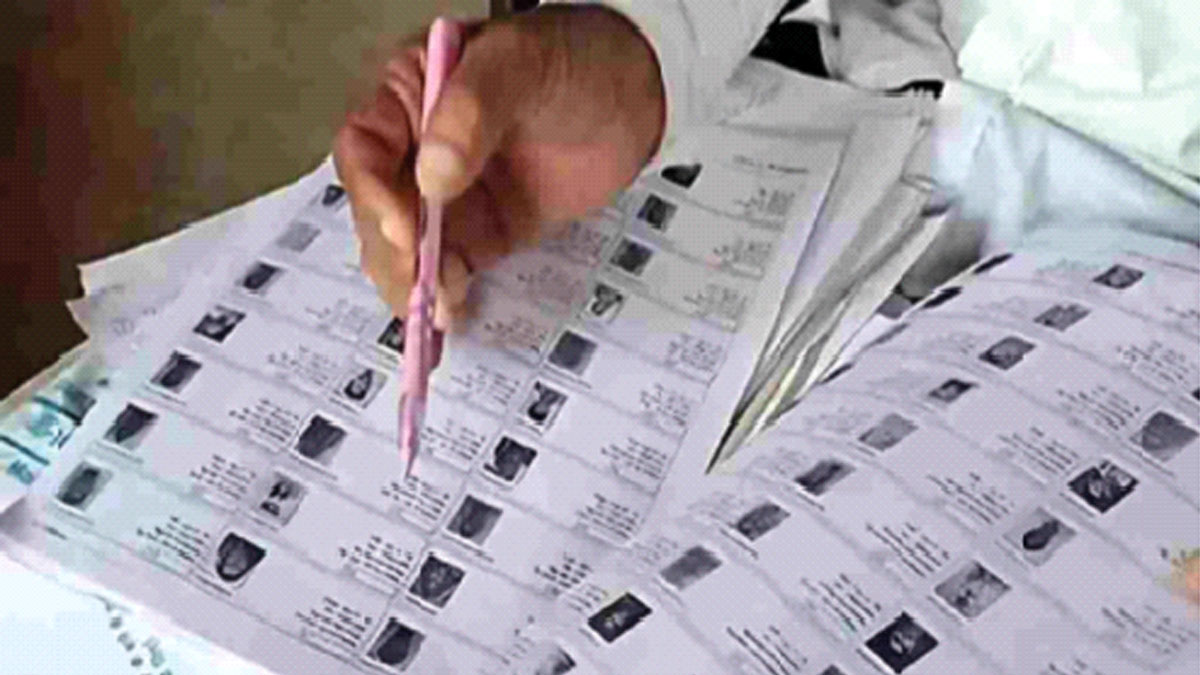রানা ঘোষদস্তিদার
সময়াভাবে অনেকদিন পাঠকের দরবারে আসা হয়নি। সম্প্রতি এক পুরনো পাঠকের সাথে কথাবার্তার সময় প্রশ্ন এল পশ্চিমবঙ্গে বীজ উৎপাদনের সম্ভাবনা কেমন। প্রসঙ্গত, বহুদিন আগে দৈনিক স্টেটসম্যানেই বাংলার ছোট জোতের জমি ও জনসংখ্যার বিচারে বীজ ব্যবসায় কৃষি ও শিল্পের মেলবন্ধনকারী এক চমৎকার উদ্যোগ হয়ে দেখা দিতে পারে এরকম একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম আর, আলোচনায় তার উল্লেখ উঠে এসেছিল। ভদ্রলোককে জানালাম যে সম্ভাবনাটা এখন আরো জোরদার। তখন তিনি আরেকবার ব্যাপারটা নিয়ে লিখতে বললেন। তাই এই হাজিরা।
Advertisement
আমরা জানি কৃষির জন্য একটি অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ হল বীজ। ভারতের সবুজ বিপ্লবের সূচনা যে নর্মান বোরল্যাগের নেতৃত্বে মেক্সিক্যান বেঁটে গমের জাতি থেকে ভারতের জন্য উপযোগী উচ্চ ফলনশীল বেঁটে গমের জাতি বা ফিলিপাইন্সের ইন্টারন্যাশনাল রাইস রিসার্চ সেন্টার থেকে আনীত বেঁটে উচ্চ ফলনশীল ধানের জাতির প্রচলনে তা বোধকরি কাউকে নতুন করে বলতে হবে না। তারপরেও ভারতে নানা ফসলে উল্লেখ্য প্রগতি হয়েছে, দুর্ভিক্ষ ব্যাপারটি অতীত হয়ে গেছে এবং তার প্রধান কৃতিত্ব কিন্তু বীজ বিকাশকারী বা উদ্ভিদ প্রজননবিদদের এমন বলাই যায়।
Advertisement
বিশেষ করে উল্লেখ করা যায় সেই ফসলগুলির কথা, যেগুলিতে হাইব্রিড বা সঙ্কর জাতি বিকাশ করা সম্ভব হয়েছে। দেখা যাবে স্বাধীন ভারতে অগ্রগতি হয়েছে সেই ফসলের উৎপাদনে, যেখানে উৎপাদনশীলতা বেড়েছে আর, সেই কাজে মুখ্য অবদান থেকেছে হাইব্রিড জাতির। পক্ষান্তরে, যে ফসল মূলত স্বপরাগী, যেখানে সঙ্কর জাতি বিকাশ করা সম্ভব হয়নি, যথা নানা ডালশস্য বা অধিকাংশ তেলবীজ, সেখানে সার-জল-কীটনাশকের প্রয়োগ সত্ত্বেও, উৎপাদনশীলতা সেভাবে বাড়েনি এবং ভারত এই দুই ক্ষেত্রে এখনো স্বনির্ভর নয়। ধান বা গম হল ভারতের দুই মুখ্য খাদ্যশস্য এবং, সরকারী নীতি ছাড়া আজোবধি দেশের কৃষি গবেষণার সিংহভাগ ব্যয়িত হওয়া সত্ত্বেও, এই দুই ফসলের ক্ষেত্রেই দেখা যাবে কয়েক দশকের পুরনো জাতির ব্যাপক প্রচলন। তার একটা কারণ যদিও শুধু ফলন নয়, ফসলের নানা গুণমান, স্বাদ ইত্যাদিও গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বের খতিয়ান নিলে অবশ্য গমের মূল্যবৃদ্ধি বেশ চিন্তার বিষয়। কারণ, নানা দেশেই ফলন সেভাবে বাড়ছে না, আর জলবায়ুর পরিবর্তন একটা চিন্তার বিষয়। অনেক গবেষণা সত্ত্বেও গমের ক্ষেত্রে সঙ্কর জাতি বিকাশ এখনো সম্ভব হয়নি। চীন অবশ্য সঙ্কর ধান বিকাশ করে ফেলে সত্তরের দশকেই চাল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে যায়। ভারতেও সঙ্কর ধান নব্বইয়ের দশক থেকেই কৃষিতে পিছিয়ে থাকা অঞ্চলে ব্যাপক ফলন দিতে থাকে এবং একদা ভুখা ভারত যে আজ বিশ্বের পয়লা নম্বর চাল রপ্তানিকারী, তার একটি কারণ সঙ্কর জাতির ধান, অন্যটি পুসা থেকে বিকশিত উচ্চ ফলনশীল বাসমতীর জাতি। এ ছাড়া হালফিলের ভারতে যে দুটি ফসলে উল্লেখ্য উন্নতি হয়েছে তার একটি হল ভুট্টা, যেখানে সিঙ্গল ক্রস হাইব্রিড চমৎকার ফলন দিচ্ছে। তবে, এক্ষেত্রে মূল কৃতিত্ব বহুজাতিক সংস্থার বিদেশস্থিত গবেষণা কেন্দ্রগুলির। আরেকটি হল সর্ষে, যেখানে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা দেশীয় জার্মপ্লাজম ব্যবহার করেই সঙ্কর জাতি বিকাশ করে চলেছেন আর, ভারতের গড় উৎপাদনশীলতা এই গুরুত্বপূর্ণ রবি তেলবীজ ফসলের ক্ষেত্রে ক্রমশ বাড়ছে।
বলে রাখা ভালো, সব্জির ক্ষেত্রেও কিন্তু সঙ্করায়ন দ্রুত হয়ে চলেছে। নানা সব্জির ক্ষেত্রে শুধু ফলন নয়, সব্জির রূপ, গুণাগুণ , স্বাদ এবং অবশ্যই কীট-রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতা খুব জরুরি এবং সেক্ষেত্রে সঙ্করের মাধ্যমে নানা গুণের সমাহার করা সহজ। তবে, দুঃখের বিষয়, বেশ কিছু সবজি বীজের ক্ষেত্রে ভারতের স্বনির্ভরতা এখনো নেই, আমদানির উপর নির্ভর করতে হয়।
আশা করি, বীজ বিষয়ে প্রাথমিক কিছু তথ্য দেওয়া গেছে। এবার আসা যাক উদ্যোগটা সম্বন্ধে। পশ্চিমবঙ্গে এর প্রয়োজনীয়তাটা কীসের!
প্রথম কথা, পশ্চিমবঙ্গে যদিও এখন বেশ কিছু বীজ উদ্যোগ সাফল্যের সাথে কাজ করছে, সর্বভারতীয় স্তরেও নাম শোনা যাচ্ছে, বীজ উৎপাদন ব্যাপারটি দানা বাঁধেনি সেভাবে। এখনো সারা ভারতের ধান, বাজরা, ভুট্টা বা নানা সব্জির বীজ উৎপাদন অন্ধ্র, তেলেঙ্গানা বা কর্নাটকের কুক্ষিগত হয়ে রয়েছে, বীজ উদ্যোগ ব্যাপারটিতেই হায়দ্রাবাদ, বেঙ্গালুরুর একচেটিয়া রমরমা। অন্যদিকে, গমের বীজ বা আলুর টিউবার উৎপাদন পঞ্জাব- উত্তরাখণ্ডের হাতে, কিছু সব্জির বীজ উৎপাদনে হিমাচলের রমরমা। অথচ, অনেক জায়গাতেই, বিশেষত অন্ধ্র-তেলেঙ্গানায় বীজ উৎপাদনে নানা সমস্যা দেখা দিচ্ছে, জল বা শ্রমিক দুর্লভতা যেমন। বীজ উৎপাদনের জন্য সঠিক ভাবেই পুবের দিকে অনেকে তাকাচ্ছেন । বাংলার কাজ শুধু তাঁদের জন্য যথাযথ পরিবেশ তৈরি করে দেওয়া।
দুই, বীজ উৎপাদন বাংলায় প্রচুর শ্রমদিবস সৃষ্টি করতে পারে। প্রায় তিন দশক আগের সমীক্ষা থেকেই দেখা যায়, সাধারণ ধান চাষের তুলনায় ধানের বীজ উৎপাদনে একর প্রতি প্রায় দেড়্গুণ বেশি শ্রমিক লাগে। অতিরিক্ত শ্রমিক লাগে প্রধানত রোগিং অর্থাৎ অনভিপ্রেত বা খাপছাড়া ধানের চারা তুলে জাতির সুষমতা বজায় রাখার কাজে। এছাড়া, বীজ উৎপাদনে সাধারণ চাষের তুলনায় বেশি সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। সঙ্কর জাতির ধানের বীজ উৎপাদনে লাগে আরো বেশি শ্রমিক, রোগিং ছাড়াও, ফিমেল লাইনে জিব্বারেলিক অ্যাসিড বা জিএথ্রি হর্মোন স্প্রে করতে এবং ট্রিপিং-এর মাধ্যমে পরাগসংযোগে সহায়তা করার জন্য। আবার, কাজগুলি ঠিক্ভাবে হচ্ছে কিনা দেখার জন্য চাই অভিজ্ঞ লেবার সুপারভাইজার বা ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট। ধান, গম ইত্যাদি হল ফিল্ড ক্রপ এবং এদের বীজ উৎপাদনে যেমন বেশি জমি লাগে, তেমনি, কাজকর্মে সুবিধার জন্য, একজায়গাতেই একরের পর একর জুড়ে কাজ হলে ভালো হয়। ভুট্টার মত ফসলের বীজ উৎপাদনে আবার এই একত্রীকরণ খুব জরুরি। ভুট্টা হল ক্রস পলিনেটেড ক্রপ এবং, নির্দিষ্ট মেল থেকে না এসে ভিন্ন উৎস থেকে পরাগ এসে পৌঁছলে জাতির সুষমতা বা পিউরিটির দফারফা। সেজন্য, অন্য জাতির বীজ উৎপাদন থেকে ন্যূনতম দূরত্ব বা আইসোলেশন ডিস্ট্যান্স বজায় রাখতে হয়। বীজের প্রাথমিক শর্তাবলীর মধ্যে অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা বা জার্মিনেশন পার্সেন্টেজ, ফিজিক্যাল ও জেনেটিক্যাল পিউরিটি অত্যন্ত জরুরি। আবার, বলাই বাহুল্য, সেসব পরীক্ষার জন্যও নির্দিষ্ট স্কিলওয়ালা শিক্ষিত লোক লাগে। ফিরে যাই জমির একত্রীকরণে। সহজ হিসাবে, একটা গোটা গ্রামের সব চাষী যদি পূর্বনির্ধারিত খরিদ্দারের নির্দিষ্ট কোন ভ্যারাইটি বা হাইব্রিড উৎপাদন করে, তাহলে বীজ উৎপাদনের প্রাথমিক শর্তাবলী সুন্দরভাবে রক্ষিত হয়। সেক্ষেত্রে ওই গ্রাম আদর্শ সীড ভিলেজ বলে মান্যতা পেতে পারে। কৃষকদের সাথে উদ্যোগীদের যোগাযোগ বজায় থাকে সীড এজেন্টদের মাধ্যমে। এরা মূলত শিক্ষিত কৃষকসন্তান।
সবজি বীজ উৎপাদনে অবশ্য ফিল্ড ক্রপের মত বেশি কৃষিজমি লাগে না এবং, অনেক সব্জির ক্ষেত্রেই আইসোলেশন ডিস্ট্যান্স বেশ কম। সেক্ষেত্রে, খুব ছোট জোতের কৃষকও টোম্যাটো, লঙ্কা, বেগুন ইত্যাদির সঙ্কর বীজ উৎপাদন করতে পারেন। তবে, এক্ষেত্রে, মেল ও ফিমেলের মধ্যে ইমাস্কুলেশন ও পলিনেশনের মাধ্যমে পরাগসংযোগ,ঘটাবার কাজটি পুরোপুরি মানবনির্ভর। মানবীনির্ভর বললে আরো ভালো হয়। সবজি থেকে বীজ নিষ্কাশন, শুকানো, ঝাড়াই বাছাইতেও লাগে প্রচুর শ্রমিক। কর্ণাটকের রাণীবেন্নোর ব্লক সবজি বীজ উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। দূর থেকে দেখা যায় ছোট ছোট জোতের ক্ষেতে ডজন ডজন নারীশ্রমিক পরাগসংযোগের কাজে ব্যাপৃত। আর, বলা বাহুল্য, বীজ উৎপাদনে দক্ষ শ্রমিকের মজুরি সাধারণ কৃষিশ্রমিকের চেয়ে বেশি। বাংলার ছোট জোতের কৃষকদের জন্য আদর্শ মডেল না?
তিন, শুধু বীজ উৎপাদন নয়, তার ঝাড়াই-বাছাই, সংরক্ষণ, মোড়কজাত করে বিপণন সর্বত্র যেমন দক্ষ শ্রমিক ও কর্মীর প্রয়োজন তেমনি চাই গুদাম, ঠাণ্ডাঘর এবং, অবশ্যই পরিবহন। সীড প্রসেসিং হায়দ্রাবাদের এক উল্লেখ্য শিল্প। শুখা বাঁকুড়া অনেকটাই হায়দ্রাবাদের ভূমিকা নির্বাহ করতে পারে।
চার, বীজ উৎপাদনের আগে আসে জাতি, ওপেন পলিনেটেড ভ্যারাইটি বা হাইব্রিড ভ্যারাইটির বিকাশ এবং সেজন্য চাই গবেষক ও গবেষণাকেন্দ্র। বাংলায় বিভিন্ন কোম্পানী যে বীজ বিক্রয় করে তার যথাযথ পরীক্ষা হয় কি বাংলায়? আবশ্যিক হলে বেশ কিছু শিক্ষিত ছেলেমেয়ের কর্মসংস্থান হয়। আবার গবেষণাকেন্দ্র মানে একদিকে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান, অন্যদিকে উন্নতমানের কৃষিপদ্ধতির প্রচলন, সাধারণ কৃষকবর্গের মধ্যে তথ্যের বিস্তারলাভ।
এবার, শুধু বাংলাতেই যে বীজ বিক্রয় হয়, আলুর টিউবার সমেত, তার বৃহদংশ বাংলাতেই উৎপাদিত হয়ে থাকতে হবে, এমন যদি আবশ্যিক ধারা চালু হয়, তাহলে বাংলায় বীজ উৎপাদন এক বিরাট উদ্যোগ হয়ে দেখা দেবে না? হিসাব করে দেখুন না গবেষণা থেকে শুরু করে বিপণন অবধি সাধারণ কৃষির তুলনায় কত বেশি কর্মসংস্থান হতে পারে!
Advertisement