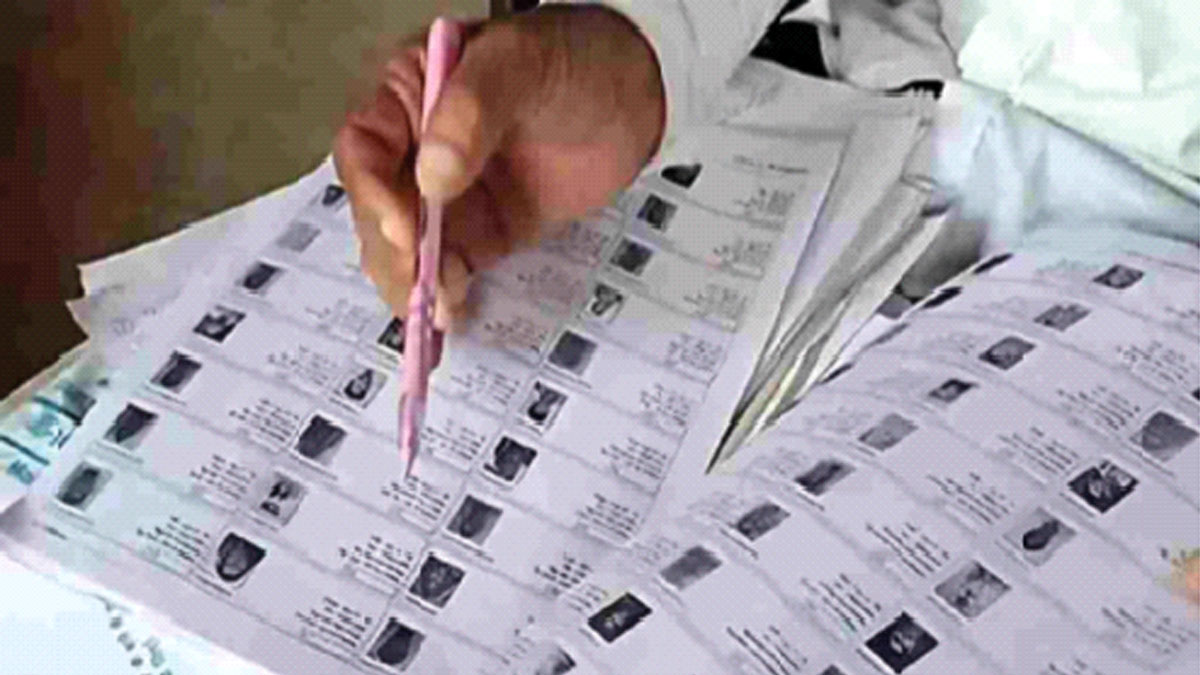শোভনলাল চক্রবর্তী
প্রতি বছরের মতো এ-বারেও অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস একটি শব্দকে বেছে নিয়েছে ২০২৪ সালের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য শব্দ হিসাবে। এমন যে কোনও নির্বাচন নিয়েই দ্বিমত থাকে, থাকতে বাধ্য। কিন্তু প্রথমত, ইংরেজি ভাষার ভুবনে অক্সফোর্ড অভিধানের প্রকাশকের একটি বিশেষ গুরুত্ব ও মর্যাদা আজও বহাল। দ্বিতীয়ত, বছরের ‘সেরা’ শব্দ নির্বাচনের জন্য অক্সফোর্ড বিস্তর কাঠখড় পুড়িয়ে থাকে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বহু শব্দের তালিকা থেকে এক দীর্ঘ, শ্রমসাধ্য ও বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কয়েকটি স্তরে ভেঙে ভেঙে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছয়। সেই প্রক্রিয়ায় বিশেষজ্ঞদের পাশাপাশি সাধারণ নাগরিকেরও একটি বড় ভূমিকা থাকে, এ-বারেও যেমন সংগ্রহ করা হয়েছে প্রায় চল্লিশ হাজার নাগরিকের মতামত। এবং শেষ অবধি অন্য প্রতিযোগীদের পরাজিত করে এই কঠিন পরীক্ষায় যে শব্দবন্ধটি জয়ী হয়েছে সেটি হল ‘ব্রেন রট’। বাংলা করলে দাঁড়ায় মস্তিষ্কের পচন।
Advertisement
সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, বহু মানুষ একটি সমকালীন সামাজিক প্রবণতাকে বোঝাতে গত এক বছরে এই শব্দটি বহু বার ব্যবহার করেছেন। কী সেই প্রবণতা? ক্রমাগত হরেক রকমের অগভীর ও অবান্তর তথ্য আর কথা দেখে, শুনে এবং পড়ে মানুষের মগজ অসাড় হয়ে যাচ্ছে, মানুষ কোনও বিষয় নিয়ে গভীর ভাবে ভাবতে ভুলে যাচ্ছে। এক কথায়, লোকের মগজ পচে গিয়েছে।গত শতাব্দীর শেষ দশকে কলকাতার নাগরিক কবিয়াল ঘোষণা করেছিলেন: ‘মগজে কারফিউ’ জারি হয়েছে, নিজের মতো করে ভাবতে গেলে ‘পেয়াদা ধরবে, বেঘোরে মরবে’। স্বাধীন মগজের অবাধ গতিবিধিকে ক্ষমতাবানেরা সর্বত্র এবং সর্বদা ভয় পায়, নানা ভাবে তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে, নিষ্ক্রিয় করতে তৎপর হয়ে ওঠে। মুসোলিনির ইটালিতে আন্তোনিয়ো গ্রামশির ‘বিচার’ চলার সময় সরকারি উকিল জানান: এই মগজটিকে কুড়ি বছর কাজ করতে দেওয়া যাবে না। হীরক রাজ্যের অধিপতি তাঁর শিক্ষামন্ত্রীকে অমৃতবচন শুনিয়ে দেন: ওরা যত বেশি পড়ে, তত কম জানে, তত কম মানে, অতএব আজ থেকে পাঠশালা বন্ধ। এবং মগজের পুষ্টি রোধ করেই সন্তুষ্ট হন না তিনি, তৈরি হয় মস্তিষ্ক প্রক্ষালন যন্ত্র।
Advertisement
শতাব্দী পাল্টেছে, ক্ষমতার স্বভাব দুর্মর। দুনিয়ার বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশে সজাগ এবং সজীব মগজের ভয়ে সদা-সন্ত্রস্ত নেতানেত্রীরা ক্রমাগত চতুর্দিকে রকমারি জুজু দেখতে থাকেন, কখনও তার নাম আর্বান নকশাল, কখনও মাওবাদী। রাষ্ট্রশক্তির অচলায়তন থেকে ক্রমাগত প্রবল স্বরে ঘোষিত হতে থাকে রক্তচক্ষু নিষেধাজ্ঞা: মগজে কারফিউ।কিন্তু যদি এমন হয় যে মস্তিষ্কের উপর নিয়ন্ত্রণ জারি করার আর কোনও দরকারই থাকল না, সে নিজেই অসাড়, নিষ্ক্রিয়, অচল হয়ে পড়ল? অসার কল্পনা নয়, কঠোর বাস্তব। এই বাস্তবের এক অসামান্য রূপ উন্মোচিত হয়েছে একটি ইংরেজি শব্দের দর্পণে। কোথা থেকে আসে অগভীর এবং অবান্তর কথা আর তথ্যের এমন বিপুল স্রোত? বলা বাহুল্য, তার প্রধান উৎস হল সমাজমাধ্যম। বার্ষিক শব্দ-সমীক্ষাতেও সেই সত্যই উদ্ঘাটিত। সমাজমাধ্যমের বিভিন্ন পরিসরে প্রতিনিয়ত অগণিত নাগরিকের বিরামহীন কথা ও ছবি ভেসে আসে, তাঁরা সেই স্রোতে নিরন্তর ভেসে চলেন। এই অবিরাম মহাপ্লাবনে এক মুহূর্তও থামার অবকাশ নেই, কোনও বিষয়ে সময় নিয়ে মনোনিবেশের ফুরসত নেই। মানুষের মস্তিষ্ক এই পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে গিয়ে নিজের স্বাভাবিক জীবনীশক্তি হারিয়ে ফেলছে।
মনে রাখতে হবে, সেই শক্তি একমাত্র সচেতন ভাবনার মধ্য দিয়েই নিজেকে পুষ্টি দিতে পারে, ভাবনার সুযোগ হারিয়ে গেলে মগজ নিজেই ঝাঁপ ফেলে দেয়, তখন আর বাইরে থেকে কারফিউ জারি করার কোনও দরকার হয় না। শব্দবিশেষজ্ঞরা এই প্রক্রিয়াটিকে নির্ভুল ভাবে চিহ্নিত করেছেন। তার পিছনে অর্থনীতি ও রাজনীতির যে গভীর লীলা কাজ করছে সে বিষয়ে অবশ্য তাঁরা— বিশেষজ্ঞ হিসাবে— কিছু বলেননি। বলার কথাও নয়। সেই কাজ সমাজবিজ্ঞানীদের, এবং প্রতিটি সচেতন নাগরিকের। এক দিকে অর্থনীতির অধীশ্বররা চাইছেন নিশ্চেতন উপভোক্তা তৈরি করতে, অন্য দিকে রাজনীতির নিয়ামকরা চাইছেন প্রশ্নহীন প্রজা উৎপাদন করতে। মস্তিষ্কে পচন ধরলে, চিন্তাশক্তি অসাড় হয়ে গেলে উভয়ের লক্ষ্যই পূর্ণ হয়। ভরসা এইটুকুই যে, দুনিয়া জুড়ে ‘ব্রেন রট’ শব্দটি সারা বছরে যাঁরা ব্যবহার করেছেন, তাঁদের এক বিরাট অংশ বয়সে তরুণ। তাঁদের একটি অংশ যদি এখনও মস্তিষ্কের সচলতা রক্ষার জন্য মগজাস্ত্রে শাণ দেন, তবে অসার অবান্তর কথাসরিৎসাগর থেকে উদ্ধারের পথও মিলবে।
তবে কি এই মস্তিষ্কের এই পচন নিয়ে যাবে অন্য কোনও দরজায়,যেমন স্মৃতিহীনতায়? চিন্তাটা সঙ্গত।কারণ সম্প্রতি জার্নাল অব ইকনমিক লিটারেচার-এর একটি পরিসংখ্যান দেখাচ্ছে পঁয়ষট্টি-ঊর্ধ্ব বয়সের ব্যক্তির স্মৃতিহীনতা রোগটি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। মহিলাদের এই ব্যাধির সম্ভাবনা পুরুষদের থেকে দুই-তৃতীয়াংশ কম। শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় কৃষ্ণাঙ্গ এবং মেক্সিকানদের এই ব্যাধির প্রকোপে পড়ার সম্ভাবনা বেশি। পড়াশোনার জগতের লোকেদের রোগটি হওয়ার সম্ভাবনা কম।
বিস্মরণ রোগের (অ্যালঝাইমার’স ডিজ়িজ়) তিনটি স্তর। প্রথম স্তরে কিছু সাম্প্রতিক ঘটনা ভুলে যাওয়া, নাম ভুলে যাওয়া। এই ধরনের বিভ্রম অনেক প্রৌঢ় লোকেরই হয়, যার জন্য ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হয় না। দ্বিতীয় স্তরে এই লক্ষণগুলি বৃদ্ধি পায়। পরীক্ষা করে মস্তিষ্কের ভিতর কিছু কোষে অস্বাভাবিকতা ধরা পড়ে। তার ফলে স্মরণশক্তি, আচরণগত ও সামাজিক দক্ষতা, এ সবই ধীরে ধীরে নষ্ট হতে থাকে; তা সত্ত্বেও, হাঁটাচলা এবং ব্যক্তিগত কাজকর্ম করার ক্ষমতা তখনও পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। শেষ স্তরটি ডিমেনশিয়া, যখন মানুষ মস্তিষ্কের কোষ বা নিউরনের ক্রমাগত অবক্ষয়ে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়। রোগীর স্বাভাবিক ও স্বাধীন ভাবে শারীরিক কার্য সম্পাদন করার ক্ষমতা হ্রাস পায়। কিছুই আর তাঁর কাছে পরিচিত ঠেকে না।
ইংল্যান্ডের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের ওয়েবসাইট থেকে জানছি এই ব্যাধিটি শুরু হচ্ছে মস্তিষ্কের কোষে দু’রকম প্রোটিন জমা হয়ে, যার একটি হল বিটা অ্যামাইলয়েড ও অপরটি টাউ প্রোটিন। সহজ কথায় এই প্রোটিনগুলি পুঞ্জীভূত হয়ে স্নায়ুগুলির মধ্যে নিউরোফাইব্রিলারি ট্যাঙ্গেলস বা জট তৈরি করে। আবার যে নিউরোট্রান্সমিটার এক স্নায়ুকোষ থেকে আর এক স্নায়ুকোষে রাসায়নিক সঙ্কেত পাঠায়, সেগুলি যদি যথাযথ কাজ না করে, তা হলেও রোগটি দানা বাঁধতে পারে। এই রোগের চিকিৎসায় আমেরিকায় কয়েকটি ওষুধ বেরিয়েছে যা রোগের প্রকোপ স্তিমিত করতে সক্ষম। নিরাময়ের পথ কিন্তু এখনও অজানা।চিকিৎসাশাস্ত্র বলছে বিস্মরণ রোগের মোকাবিলার প্রথম পদক্ষেপটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক। নিজের দেখভাল করা, স্বাস্থ্যকর খাওয়াদাওয়া, মনকে অবসাদমুক্ত রাখা, যোগব্যায়াম বা অন্য কায়িক পরিশ্রম করা, মস্তিষ্কের কোষগুলিকে চালু রাখার চেষ্টা করে যাওয়া। যেমন, ধাঁধা সমাধান, সুদোকু খেলা, শব্দজব্দ, ছবি আঁকা, বই পড়া, নতুন ভাষা শেখার চেষ্টা ইত্যাদি।
দ্বিতীয় পথটি সরকারি হস্তক্ষেপ। অ্যালঝাইমার’স সোসাইটির একটি সমীক্ষা জানাচ্ছে যে, সারা বিশ্বে এই রোগটি নিরাময়ের জন্য যে গবেষণা প্রয়োজন তার জন্য সরকারি অনুদান ক্যানসার বা অন্যান্য ব্যাধির তুলনায় অনেক কম। ভারতের মতো দেশে, যেখানে প্রৌঢ়-যুবার অনুপাত উন্নত দেশগুলির থেকে তুলনামূলক ভাবে অনেক কম, এই রোগটি অবহেলিত।জীবননির্বাহ ক্রমশ জটিল হয়েছে। সন্তান কাজের জন্য বৃদ্ধ বাবা-মাকে ছেড়ে দূরদূরান্তে পাড়ি দিচ্ছেন। অনেকে বাবা-মায়ের কাছে থেকেও তাঁদের দেখাশোনা করতে আগ্রহী নন। এ ক্ষেত্রে কী করণীয়? বৃদ্ধাশ্রম একটি বিকল্প। ভারতে এখন কিছু ভাল বৃদ্ধাশ্রম তৈরি হয়েছে। তবে সেগুলি সাধারণত আমজনতার সাধ্যের বাইরে। অবশ্য সেখানেও কোনও প্রিয়জনের তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন।
যাঁর সে রকম কেউ নেই, তাঁর কী উপায়? অর্থনীতিতে একটি ধারণা আছে, যাকে বলে ঝুঁকি বণ্টন (রিস্ক শেয়ারিং), যা বাজারি বিমার বিকল্প হিসাবে কাজ করতে পারে। ধরুন, আমি আমার সমবয়সি বা সমমনস্ক বন্ধুদের নিয়ে একটি কমিউনিটি বানালাম। তাদের সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা বিনিময় করলাম। এরাই আমার বার্ধক্যের ঝুঁকি খানিকটা বহন করতে পারেন। আবার একই সাহায্য আমি বন্ধুদের জন্য করার চেষ্টা করতে পারি। এই ধরনের কমিউনিটি আমার এক আত্মীয় তৈরি করেছিলেন অনেক বছর আগে। গোলদিঘিতে প্রতি দিন তিনি তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে আড্ডা দিতেন। এখন আমাদের গোলদিঘিতে যাওয়ার আর দরকার নেই, হোয়াটসঅ্যাপ, মেসেঞ্জার বা জ়ুম ‘গ্রামে’ আমরা এই গোষ্ঠী তৈরি করতে পারি। যে কোনও গোষ্ঠী নয়, তার জন্য সচেতন যৌথ উদ্যোগ রাখতে হবে। অবশ্য এই ধরনের অলিখিত ঝুঁকি বণ্টন বাস্তবে কি কার্যকর হয়? রবার্ট টাউনসেন্ড এবং তাঁর গবেষকদের তাইল্যান্ডের কিছু গ্রাম নিয়ে ২০২৪ সালের সমীক্ষা বলছে যে, একই গ্রামে আত্মীয়বন্ধুদের মধ্যে ঝুঁকি বণ্টন সুষ্ঠু ভাবেই কাজ করেছে।
অর্থাৎ বাজার বা রাষ্ট্র যখন সমস্যার সমাধান করতে পারে না, বন্ধুবান্ধব ভার্চুয়াল প্রতিবেশীরা ব্যক্তিগত স্তরে এই ঝুঁকি বণ্টনের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান ও মীমাংসা করতে পারেন। শেষের সে দিন হয়তো ভয়ঙ্করই, তবু চেষ্টা, একটু সকলের সঙ্গে জড়িয়ে থাকার। মনে পড়ে, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের সত্যি ঘটনার উপর লেখা ‘সাক্ষী ডুমুর গাছ’ গল্প। সাতাশি বছরের বৃদ্ধ ধীরে ধীরে বিস্মরণের জগতে চলে গেলেন। সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত বাবাকে হাওড়া স্টেশনে ট্রেনে তুলে দিল মেয়ে, মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিল যে, কোনও এক অজানা স্টেশনে কেউ তাঁকে নামিয়ে নেবে। ভয়ানক এই গল্প এখন প্রায় পরিচিত বাস্তব হওয়ার জোগাড়। বিস্মরণ রোগ সারা বিশ্বব্যাপী এক বিরাট সমস্যা। যখন শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি ধীরে ধীরে অচল হতে থাকে তখন আমরা অসহায় বোধ করি। কিন্তু যখন মাথাটিও ধীরে ধীরে তার কর্মক্ষমতা হারাতে শুরু করে এবং অবশেষে নিজের মানুষকে চেনার ক্ষমতাও হারিয়ে যায়? সেই পরিস্থিতির মোকাবিলা কী ভাবে করবে পরিবার ও সমাজ? উত্তর অজানা।
Advertisement