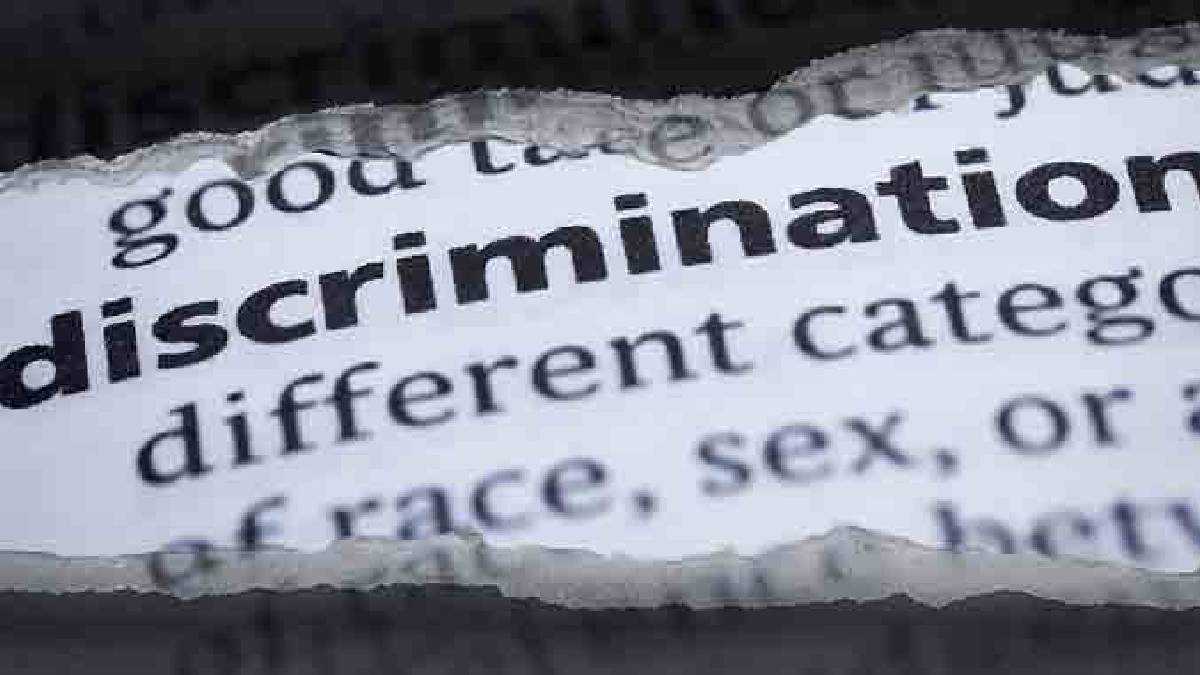শাশ্বতী নন্দ
নতুন দিল্লির ইন্ডিয়া গেটের কাছে সুসজ্জিত জনপথের ওপর সুপ্রশস্ত পরিসরে গড়ে উঠেছে ভারতের জাতীয় জাদুঘর। এই জাদুঘর গড়ে ওঠার ইতিহাসটি মনোজ্ঞ। ১৯৪৬ সালের মে মাসে Maurice Gwyer কমিটি দিল্লিতে একটি জাতীয় জাদুঘর গড়ে তোলার খসড়া পরিকল্পনা পেশ করেন। এরপর ১৯৪৭-৪৮ সালের শীতের মাসগুলিতে লন্ডন-এর রয়্যাল অ্যাকাডেমির ব্যবস্থাপনায় ভারত সরকার ও ব্রিটিশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে ভারতের বিভিন্ন জাদুঘরের সংগ্রহ থেকে বেশ কিছু নির্বাচিত শিল্পসামগ্রী নিয়ে লন্ডনের বার্লিংটন হাউসের গ্যালারিতে ভারতীয় শিল্পকলার ওপর একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনী শেষ হওয়ার পর ওই শিল্পসামগ্রীগুলিকে তাদের নির্দিষ্ট জাদুঘরে ফেরত পাঠানোর আগে ১৯৪৯ সালে দিল্লিতে রাষ্ট্রপতি ভবন পরিসরের মধ্যে প্রদর্শনের ব্যবস্থা হল, যা সাধারণের মধ্যে খুবই সমাদৃত হয়ে সাড়া ফেলে। সেই সাফল্যই হয়ে ওঠে দিল্লিতে প্রস্তাবিত জাতীয় জাদুঘরটি গড়ে তোলার মূল প্রেরণা।
Advertisement
সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, এই মহার্ঘ শিল্পসামগ্রীগুলিকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে দিল্লির জাতীয় জাদুঘরটি গড়ে তোলা হবে। বিভিন্ন রাজ্য সরকার, জাদুঘর প্রশাসন ও ব্যক্তিগত সংগ্রাহক যাঁরা প্রদর্শনীটিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের সবাইকে অনুরোধ করা হয় এই শিল্পসামগ্রীগুলিকে উপহার বা ঋণ হিসেবে দিতে। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই সেই অনুরোধ স্বীকার করেন। এইভাবে বিভিন্ন উৎস থেকে পাওয়া সমস্ত সংগ্রহগুলিকে নিয়ে ১৫ আগস্ট ১৯৪৯-এ রাষ্ট্রপতি ভবন পরিসরে এই জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করা হল। দ্বারোদ্ঘাটন করলেন স্বাধীন ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল সি রাজাগোপালাচারি। তারপর ১৯৫৫ সালের ১২ মে এই জাতীয় জাদুঘরের বর্তমান স্থায়ী সৌধটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। রাজপথ ও জনপথের মিলনবিন্দুতে, সংসদ ভবন ও রাষ্ট্রপতি ভবনের থেকে হাঁটা দূরত্বে এর প্রথম পর্যায়ের উদ্ঘাটন করেন তৎকালীন উপরাষ্ট্রপতি ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৬০-এ এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে বাকি অংশটি সম্পূর্ণ হয় ১৯৮৯ সালে। মনোরম এই সৌধের স্থপতি গনেশ বিকাজী দেওলালিকার। শুরুতে এই জাদুঘরকে শিক্ষামন্ত্রকের আওতায় একটি স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৫৭ পর্যন্ত যার তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে ছিলেন ভারতীয় প্রত্নবিদ্যা নিরীক্ষণ বিভাগের মুখ্য নির্দেশক। প্রত্নসংগ্রহশালা ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃত এই জাদুঘর এখন সংস্কৃতি মন্ত্রকের ছত্রছায়ায়।
Advertisement
রাষ্ট্রপতি ভবনে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর জাদুঘরটিকে সযত্নে সাজিয়ে তোলার জন্য বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত ভাণ্ডার থেকে নানান অনুদান নিয়মিতভাবে সংগ্রহ অভিযান চলতে থাকে। সমান্তরালে সংসদ মনোনীত ক্রয় সমিতি বিভিন্ন উৎস থেকে প্রত্নসামগ্রী কিনে আনার কাজ করতে থাকে। মূল সংগ্রহ অভিযান চালানো হয় ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২-র মধ্যে, যার প্রধান উদ্যোগী ও দাতা ছিলেন ভি এস আগরওয়ালা, মতি চন্দ্র, রাজ কৃষ্ণদাস, কার্ল খান্ডালাওয়ালা এবং তাঁদের পরিচিত বহু ব্যক্তিগত সংগ্রাহক। এছাড়াও বহু মানুষ মূল্যের বিনিময়ে বা বিনামূল্যে তাঁদের ব্যক্তিগত সংগ্রহ জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহশালায় যোগ করে একে সমৃদ্ধ করেছেন, যাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হলেন, ও সি গাঙ্গুলি, বুর্জোর এন ট্রেজারিওয়ালা। ভি এস আগরওয়ালার উদ্যোগে কলকাতার অজিত ঘোষের প্রচুর ব্যক্তিগত সংগ্রহ ছাড়াও ডিকিনসন, গুলাব চাঁদ, মোদী, মেড প্রভৃতি সংগ্রাহক ও সংগ্রহশালা থেকে বহু মূল্যবান জিনিস এই জাদুঘরে এসে জায়গা করে নেয়।
জাদুঘরের প্রবেশদ্বার পার করে এগোলেই সবার প্রথমে দৃষ্টি কাড়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝের দিকে তামিলনাড়ুতে তৈরি ভগবান বিষ্ণুর পাঁচতলা একটি কাঠের মন্দির রথ। তারপর রাস্তার ওপর মূল প্রবেশদ্বার পর্যন্ত রাস্তা জুড়ে সাজানো নানান পাথরের মূর্তি ও শিল্পকলা, সম্রাট অশোকের বেশ কিছু শিলালিপি। এই জাদুঘরে পাঁচ হাজার বছরেরও বেশি পুরোনো নানান দেশি-বিদেশি সংগ্রহ রয়েছে, যাদের মধ্য দিয়ে ধরা পড়েছে ভারতবর্ষের সময়ানুক্রমিক বিবর্তনের ইতিহাস। তালিকায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় রয়েছে হরপ্পা সভ্যতা বা সিন্ধু সভ্যতা থেকে খুঁজে পাওয়া বিভিন্ন সংগ্রহ। এই জাদুঘরের মূল আকর্ষণ সিন্ধু সভ্যতার সংগ্রহগুলি দেখতে দেখতে সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করতেই হয় হরপ্পার সংগ্রহগুলির মূল খনক ও আবিষ্কর্তা দয়ারাম সাহনি এবং মহেঞ্জোদারোর মূল খনক ও আবিষ্কর্তা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। এখানে সংগৃহীত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, প্রাচীন ভাস্কর্য-শিল্পকলার সংখ্যা এখন দুই লক্ষেরও বেশি।
তবে যে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে মোট সংগ্রহের মাত্র ৬-৭% জিনিসই প্রদর্শনীতে রাখা সম্ভব হয়। জাদুঘরের পক্ষ থেকে দেশবিদেশের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে নিয়মিতভাবে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন দেশে প্রদর্শনী, ওয়ার্কশপ এবং সেমিনারের আয়োজন করা হয়। দর্শনার্থীদের সুবিধার জন্য একটি রঙিন সংক্ষিপ্ত পুস্তিকায় এই জাদুঘর সংক্রান্ত মূল ও বিশেষ তথ্যগুলি মুদ্রিত রয়েছে। এই পুস্তিকার শুরুতে লেখা একটি লাইন প্রণিধানযোগ্য— ‘যদি আপনি এই সংগ্রহশালার প্রতিটি কলাকৃতির সামনে মাত্র এক মিনিট করে কাটান, তাহলে পুরো সংগ্রহগুলি দেখতে আপনার তিন বছর নয় মাস তেইশ দিন সময় লাগবে’। ত্রিতল এই জাদুঘরের সংগ্রহগুলি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের বেশ কয়েকটি গ্যালারিতে বিন্যস্ত। প্রধান প্রধান বিভাগগুলি হল Pre-historic Archaeology, Archaeology, Anthropology, Arms and Armour, Decorative Arts, Manuscript, Numismatics and Epigraphy, Painting, Jewellery, Central Asian Antiquities, Pre-Columbian and Western Art, ইত্যাদি।
১) প্রাক্-ঐতিহাসিক প্রত্নবিদ্যা বিভাগ (Pre-historic Archaeology)— হরপ্পান গ্যালারি: সিন্ধু-সরস্বতী নদী উপত্যকায় বিকশিত হওয়া সিন্ধু সভ্যতা বা হরপ্পা সভ্যতা। ভারতবর্ষের প্রাচীনতম এই ব্রোঞ্জযুগ সভ্যতার উল্লেখযোগ্য সংগ্রহগুলি হল ‘দি ডান্সিং গার্ল’, ‘স্ট্যান্ডিং ফিগার অফ দি মাদার গডেস’, ‘ক্লাইম্বিং মাংকি’, ‘বুল’, ‘পশুপতি শিল’, ‘টয় কার্ট’, ‘সিটেড মেল ইন নমস্কার পোজ’, ইত্যাদি। এগুলি সব ২৭০০ থেকে ২১০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের শিল্পকলা। পাকিস্তান ও ভারতে ছড়িয়ে থাকা হরপ্পান সভ্যতার বিভিন্ন অঞ্চলের খননে এই ব্রোঞ্জ-টেরাকোটা শিল্প ছাড়াও ছোটো বড়ো বিচিত্র সুন্দর গড়নের মাটির নানারকম পাত্র, বহুরকম খেলনা, বিভিন্ন ধরনের অলংকার, বহুবিধ প্রত্নসামগ্রী খুঁজে পাওয়া গেছে। পাঁচ হাজার বছর আগেকার নৃত্যরতা কন্যাটির সাজসজ্জা ও অলংকারের সঙ্গে আজকের উত্তর ভারতীয় মহিলাদের সাজপোশাক, অলংকারের আশ্চর্য মিল খুব অবাক করে। সেই যুগের একটি পূর্ণাবয়ব নারী শরীরের অক্ষত অস্থিসংস্থান এই বিভাগের উল্লেখ্য অতি মূল্যবান সংগ্রহ। বাঁ হাতের শঙ্খবলয় দুটি থেকে ধারণা করা হয় মহিলা বিবাহিত ছিলেন।
২) প্রত্নবিদ্যা বিভাগ (Archeology): সিন্ধু সভ্যতা পরবর্তী প্রাচীন ভারতবর্ষে নানা শাসক রাজবংশের উদ্ভব হল। এই বিভাগ ইতিহাসের সেই পর্যায়ের বিভিন্ন প্রমাণ ধরে রেখেছে। উত্তর ভারতে মৌর্য, শুঙ্গ, শতবাহন, কুশান, গুপ্ত, বর্ধন ও প্রতিহার বংশ, পূর্বে পাল ও সেন বংশ, পশ্চিমে মৈত্রক বংশ এবং দক্ষিণে চোল, চালুক্য, হয়সাল, বিজয়নগর ও নায়ক বংশ বিভিন্ন সময়ে দেশের নানা অংশে রাজত্ব করেছে। এদের শাসনকালে শিল্প-ভাস্কর্যের বহুধা প্রসার ঘটেছিল। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে উঠেছিল নানা শৈলীর মন্দির বা অন্যান্য ধর্মীয় স্থাপত্য, প্রাসাদ, দুর্গ, স্মৃতিসৌধ, বিভিন্ন উপকরণে গড়া ভাস্কর্য। এইসব সময়ের প্রত্নসামগ্রী ও শিল্পকলা নিয়ে তৈরি করা হয়েছে তিনটি গ্যালারি— ‘মৌর্য, শুঙ্গ ও শতবাহন শিল্পকলা’, ‘কুষাণ ও ইক্ষ্বাকু শিল্পকলা’ এবং ‘গুপ্ত শিল্পকলা, প্রারম্ভিক ও অন্তিম মধ্যযুগীয় শিল্পকলা’। এই পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য সংগ্রহগুলি হল ‘অর্ধনারীশ্বর’, ‘ভারত’, ‘ভূ-দেবী’, ‘উড়ন্ত স্বর্গবাসী’, ‘মোহিনী’, ‘সরস্বতী’, ‘বুদ্ধ’, ‘সূর্য’, ‘বিষ্ণু ইত্যাদি।
৩) নৃ-বিদ্যা বিভাগ (Anthropology): জাদুঘরের নৃ-বিদ্যা বিভাগের সংগ্রহ ভাণ্ডার বিশাল, এখানে রয়েছে বিভিন্ন উপকরণ ও মাধ্যমে তৈরি আট হাজারেরও বেশি সংগ্রহ। আছে টেরাকোটা, বয়ন শিল্প, বাঁশের কাজ, কাঠের কাজ, ধাতু, কাগজ, চর্মশিল্প, ইত্যাদির সম্ভার। ‘উত্তর-পূর্ব ভারতের আদিবাসী জীবনশৈলী’ বিষয়ক গ্যালারিটিতে এইসব মাধ্যমে তৈরি বিভিন্ন ধরনের শিল্পকলা প্রদর্শিত রয়েছে, যাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য নানারকম পুতুল, পোশাক-আশাক, মুখোশ, অস্ত্র-শস্ত্র, উপযোগী গৃহসামগ্রী, চিত্রকলা, অলংকার, বাদ্যযন্ত্র, ইত্যাদি।
৪) অস্ত্রশস্ত্র ও বর্ম আভূষণ বিভাগ (Arms and Armour): ইতিহাস পূর্ববতী আদিম মানবসভ্যতা থেকে আবহমান চলে আসছে অস্ত্রশস্ত্র ও বর্ম আভূষণ নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা। নিজেকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাখা বা শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহের প্রয়োজনে নানারকম অস্ত্র আবিষ্কারের সাক্ষী মানবসভ্যতার প্রতিটি পর্যায়। বিভিন্ন সময়কালের অনেকরকম অস্ত্রশস্ত্র ও বর্ম আভূষণ নিয়ে একটি সুবিশাল ভাণ্ডার গড়ে উঠেছে এই জাদুঘরে। আছে নানান ধরনের তিরধনুক, ছোরাছুরি, বর্ম, শিরোস্ত্রাণ, শরীর ও পায়ের সুরক্ষা বর্ম আভূষণ, নানা ধরনের তলোয়ার, মোগল এবং ভারতের বিভিন্ন সাম্রাজ্যের অস্ত্রশস্ত্র, অওরংজেব-এর তলোয়ার, কামান, বন্দুক, গান পাওডার রাখার পাত্র ইত্যাদির সম্ভার। এই বিভাগটি এখন মূল জাদুঘর থেকে লালকেল্লায় স্থানান্তরিত হয়েছে।
৫) পরিশোভা শিল্পকলা বিভাগ (Decorative Arts Collection): প্রতিটি দেশের নিজস্বতা, বিশিষ্টতা তার শিল্পকলায় বিধৃত থাকে। এই গ্যালারিতে তেমনি ধরা হয়েছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন শাসনকালের পরিশোভা শিল্পকলা সম্ভার ও তাদের বিবর্তন। এখানে রয়েছে সেরামিক টাইল, কাঠ, সেরামিক ও ধাতুপাত্র, কাপড়, অলংকার, ইত্যাদির ওপর মনোলোভন নানান শিল্পকলা। যাবতীয় এই শিল্পকলা মানুষের হাতের কাজ এবং তাদের নির্দিষ্ট সময়কালের সামাজিক, ধার্মিক, সাংস্কৃতিক, বাণিজ্যিক বা প্রকৌশলগত উৎকর্ষের দর্পণ। এছাড়াও এদের মাধ্যমে বিভিন্ন রাজবংশের বিলাসবহুল জীবনযাত্রার একটি রূপরেখা পাওয়া যায়।
৬) পাণ্ডুলিপি বিভাগ (Manuscript Collection): দিল্লির জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে ১৪,০০০-এরও বেশি বিভিন্ন ভাষা, লিপিতে চিত্রিত বহুবিধ বিচিত্র বিষয়বস্তু, শিল্পশৈলী ও ভৌগোলিক অঞ্চল থেকে সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি রয়েছে। এদের মধ্যে বেশকিছু সম্পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে, কিছু খণ্ডিত। প্রায় এক হাজার পাণ্ডুলিপি রয়েছে ব্যাখ্যাসহ। যেগুলির বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়নি, তাদের অধিকাংশই খুব সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা এমন সুশোভন অলংকৃত লিপি, মনে হয় যেন আঁকা ছবি। বেশকিছু টীকার ব্যাখ্যা আবার আসল সোনার পাতে লেখা। এগুলি বহুরকম ঐতিহাসিক ও ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার মূল্যবান উৎস। সপ্তম শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত তেরো-চোদ্দোশো বছর সময়কালের পরিসর জুড়ে আছে এই সংগ্রহগুলি। পাণ্ডুলিপিগুলির মাধ্যমও অগণ্য এবং বিচিত্র, তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য পার্চমেন্ট কাগজ, বার্চ গাছের বাকল, তালপাতা, কাগজ, কাপড়, কাঠ ও নানারকমের ধাতু। ভাষামাধ্যমে রয়েছে ধ্রুপদী সংস্কৃত ছাড়াও পবিত্র ধর্মীয় ভাষা পালি, প্রাকৃত। এছাড়াও রয়েছে পুরাকালীন ভারতবর্ষের সীমারেখার বাইরের পারসিক, আরবিক, চৈনিক, ব্রহ্মদেশীয় বা তিব্বতীয় ভাষা। এই গ্যালারির ভাণ্ডারে এমন কি হিন্দি ও তার আঞ্চলিক রূপান্তর রাজস্থানি, মৈথিলি, অওধি, ব্রজ, বুন্দেলি, ইত্যাদি ভাষার পাণ্ডুলিপিও অনেক রয়েছে। এগুলি অধিকাংশই যে শুধু দুষ্প্রাপ্য তাই নয়, এদের মধ্যে অনেকগুলির ওপরে রয়েছে অতি মহার্ঘ তৎকালীন সম্রাটের রাজকীয় হস্তাক্ষর এবং শিলমোহর, যা মূল পাণ্ডুলিপি হিসেবে এদের প্রামাণ্য করে তুলেছে। এই বিভাগে বিভিন্ন লিপির ক্রমবিবর্তনের মানচিত্র, বিশেষ করে তৃতীয় খ্রীষ্টপুর্বাব্দে সম্রাট অশোকের সময় থেকে বিবর্তিত হয়ে কৃষ্ণকীর্তন কাব্যগ্রন্থে ব্যবহৃত বর্তমান বাংলা লিপির সৃষ্টি আগ্রহ জাগাবে।
৭) মুদ্রা, পদক এবং শিলালিপি বিভাগ (Numismatics and Epigraphy Collection): ভারতীয় মুদ্রাসমূহের উদ্ভাবন ও বিবর্তনের মধ্যে রয়েছে এক সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক পরম্পরা যা সমকালীন ও বিশেষ বিশেষ আঞ্চলিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পটভূমি এবং রুচি ও সৌন্দর্যবোধ সম্বন্ধে বিশেষ তথ্যসূত্র হিসেবে কাজ করে। আবিষ্কৃত শিলালিপিগুলিতে উৎকীর্ণ লিপি থেকে বিভিন্ন সময়ের এবং সেইসব রাজ্যাংশের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পটভূমির সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। এই গ্যালারি এমনই সব আকর্ষণীয় বহুমূল্য সংগ্রহে সমৃদ্ধ।
৮) চিত্রকলা বিভাগ (Painting Collection): এখানে ১৭ হাজারের ওপর ছবি আছে, যা সমস্তরকম গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় ক্ষুদ্র চিত্রকলার প্রতিনিধিত্ব করছে। এটি দেশের মধ্যে একটি বৃহত্তম ক্ষুদ্র চিত্রকলা সংগ্রহালয়। দেওয়াল, কাপড়, ক্যানভাস এবং কাঠের ওপর আঁকা এই ছবিগুলি ভারতীয় চিত্রকলার এক গুরুত্বপূর্ণ পরম্পরা ও বিশিষ্ট ধারা। এর মূল শাখাগুলি হল দক্ষিণী, মুঘল, রাজস্থানি ও পাহাড়ি (উত্তর পাহাড়ি অঞ্চল)।
৯) রত্ন-জহরত বিভাগ (Jewellery Collection): এই গ্যালারি ‘অলংকার’ (Alamkara) ২৫০-র বেশি মণিমাণিক্য, গয়না-অলংকারে সাজানো হয়েছে। দেশের সমস্ত প্রান্তের অলংকারের সৌন্দর্যে সুশোভিত এই বিভাগ ধরে রেখেছে ভারতবর্ষের রত্ন-জহরত শিল্পকলার কাহিনি ও ইতিহাস। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পান সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে উদ্ধার করা সুন্দর করে গাঁথা পুঁতির মালা থেকে শুরু করে অসাধারণ সুন্দর ঝকমকে উজ্জ্বল মণিমাণিক্য আভূষিত দেবী-দেবতার মূর্তি, মুঘল সাম্রাজ্য ও বিভিন্ন মহারাজার প্রাসাদ আলোকিত করা জমকালো রত্ন অলংকারে এক সুদীর্ঘ ভারতীয় সময়কালের রত্ন-জহরত শিল্পকলাকে উপস্থাপিত করেছে এই গ্যালারি। ভারতীয় রত্ন-অলংকারের এই প্রদর্শনী ইতিহাস পূর্ববর্তী সময় থেকে এ দেশের সৌন্দর্যবোধ ও সাংস্কৃতিক জীবন ইতিহাসের পাঁচ হাজার বছরেরও বেশি সমৃদ্ধ জীবনযাত্রার এক আকর্ষণীয় অভিব্যক্তি। জাতীয় জাদুঘরের এই রত্ন-জহরত সম্ভার তাদের বহুমুখী বৈচিত্র্য, ভারতীয় অলংকারের অপূর্ব সুন্দর নকশা পরিকল্পনা ও অসামান্য সব জানা-অজানা শিল্পীর প্রতিভা আর হস্তকলার এক সগৌরব উদ্যাপন।
এছাড়াও আর দুটি বিখ্যাত গ্যালারি হল ‘Central Asian Antiquities’ এবং ‘Pre-Columbian and Western Art’, যেখানে যথাক্রমে ভারতীয় উপমহাদেশের দেশগুলির সাংস্কৃতিক মিশ্রধারা ও দক্ষিণ আমেরিকার প্রত্নসামগ্রীর সম্ভার সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে। কাশী গ্যালারি নামে নতুন একটি গ্যালারিতে কাশীর ঐতিহ্য ও ইতিহাস বিধৃত হয়েছে। বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধযুগের প্রভূত সংখ্যক সংগ্রহ রাখা হয়েছে মূল ভবন সংলগ্ন আর একটি ভবনে। এই বিভাগে সবিশেষ উল্লেখ্য ভগবান বুদ্ধের অস্থি ও অস্থিভস্ম।
এই মিউজিয়ামে ইউনেসকো ও অন্য কিছু সংস্থার সহযোগিতায় ‘অনুভব’ নামের একটি আলাদা গ্যালারি তৈরি করা হয়েছে। এই গ্যালারিতে বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য ওঠানামার ব্যবস্থা, অডিও গাইড ও ব্রেইল হরফে বর্ণনাসহ ছুঁয়ে অনুভব করা যায় এমন কিছু উল্লেখযোগ্য প্রত্নসামগ্রীর প্রতিরূপ রাখা আছে।
দিল্লির জাতীয় এই জাদুঘর একটি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবেও স্বীকৃত এবং এখানে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলিতে স্নাতকোত্তর পঠনপাঠন ও গবেষণার ব্যবস্থা রয়েছে। এই বিষয়ে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো এখানেও উপযুক্ত ছাত্রবৃত্তি প্রদান করা হয়। যদিও ভারতের প্রাচীনতম এবং পুরো এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের বৃহত্তম জাদুঘরটি কলকাতায়। দিল্লির এই জাদুঘর (ভারতে তৃতীয় বৃহত্তম) স্বাধীনতা পরবর্তী এক নবজাতক রাষ্ট্রের প্রয়াস এবং সেই অর্থে বিশিষ্ট। বছরে গড়পড়তা ছয় থেকে সাত লক্ষ দর্শনার্থী এখানে আসেন, প্রতিদিন গড়ে প্রায় আড়াই থেকে তিন হাজার।
ইংরেজি ‘মিউজিয়াম’ শব্দটি গ্রিক মউসিয়ান শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ পুরাণের শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক মিউসদের মন্দির। এই ধরনের মন্দিরগুলোকে কেন্দ্র করে প্রাচীন গ্রিসে পাঠাগার, শিল্পকলা প্রভৃতির সংগ্রহশালা গড়ে উঠত। তবে বাংলায় আমরা যখন একে জাদুঘর বলি, তা তাত্ত্বিক প্রতিশব্দের গণ্ডি ছাড়িয়ে আরো ব্যাপক হয়ে ওঠে। আশ্চর্য সব জিনিসের সমাহার সত্যি সত্যিই আমাদের জাদু করে। এখানে এই দিল্লির ন্যাশানাল মিউজিয়ামে যেমন হরপ্পা সভ্যতার আমলে ব্যবহৃত জিনিসপত্র, বুদ্ধের অস্থিভস্ম আমাদের হতবাক করে, প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে অতীত।
ইন্টারন্যাশানাল কাউন্সিল অফ মিউজিয়ামের মতে, জাদুঘর হল অলাভজনক, জনসাধারণের কাছে উন্মুক্ত স্থায়ী একটি সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান, যা শিক্ষা, জ্ঞান ও আনন্দলাভের উদ্দেশ্যে ঐতিহ্যবাহী জিনিসপত্র সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও সেগুলি নিয়ে গবেষণা করে। এর মাধ্যমে মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আমরা অবহিত হই ও বিভিন্ন দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের একটি সেতু গড়ে ওঠে। মিউজিয়ামের গুরুত্ব সম্বন্ধে এই ব্যাখ্যা আমাদের সম্যক সচেতন করে, মানবসভ্যতার দূরদর্শী কারিগরদের কাছে আমরা নতমস্তক হই। এই বিষয়ে সচেতনতা বাড়িয়ে তোলার লক্ষ্যে প্রতি বছর ১৮ মে তারিখটি ‘আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস’ হিসেবে উদ্যাপিত হয়।
Advertisement