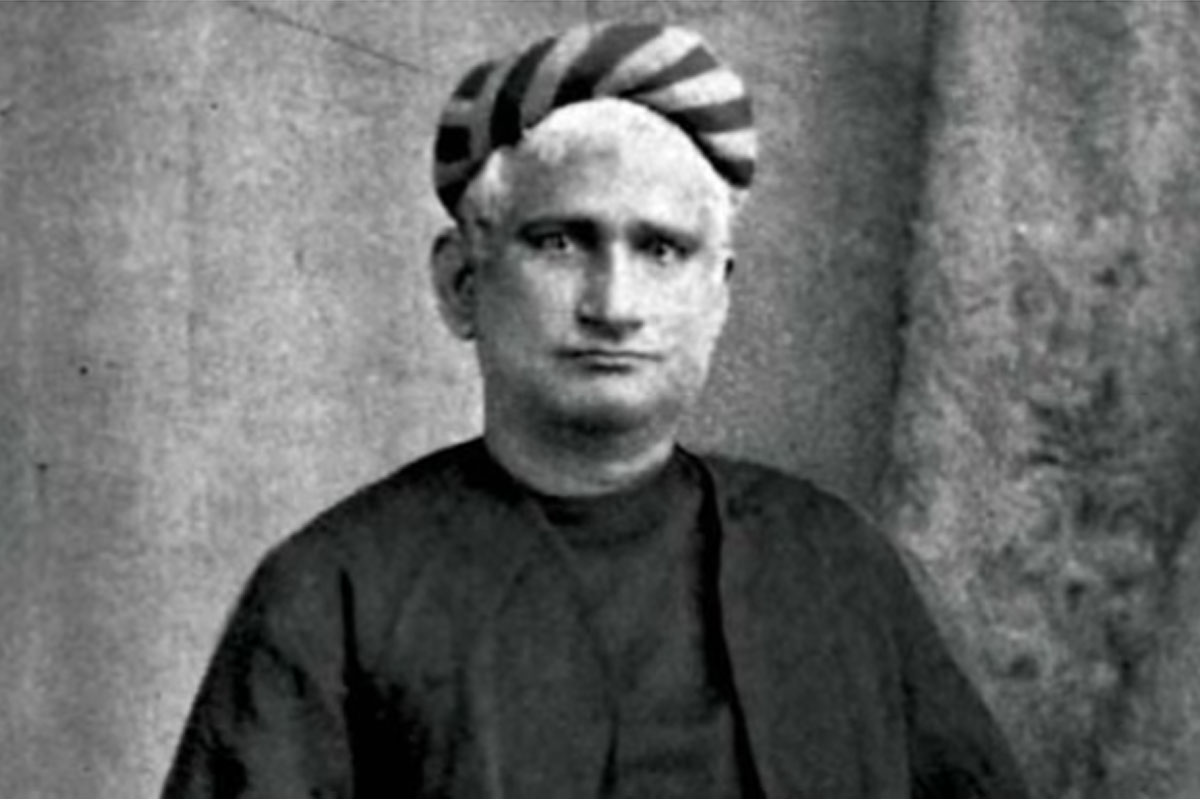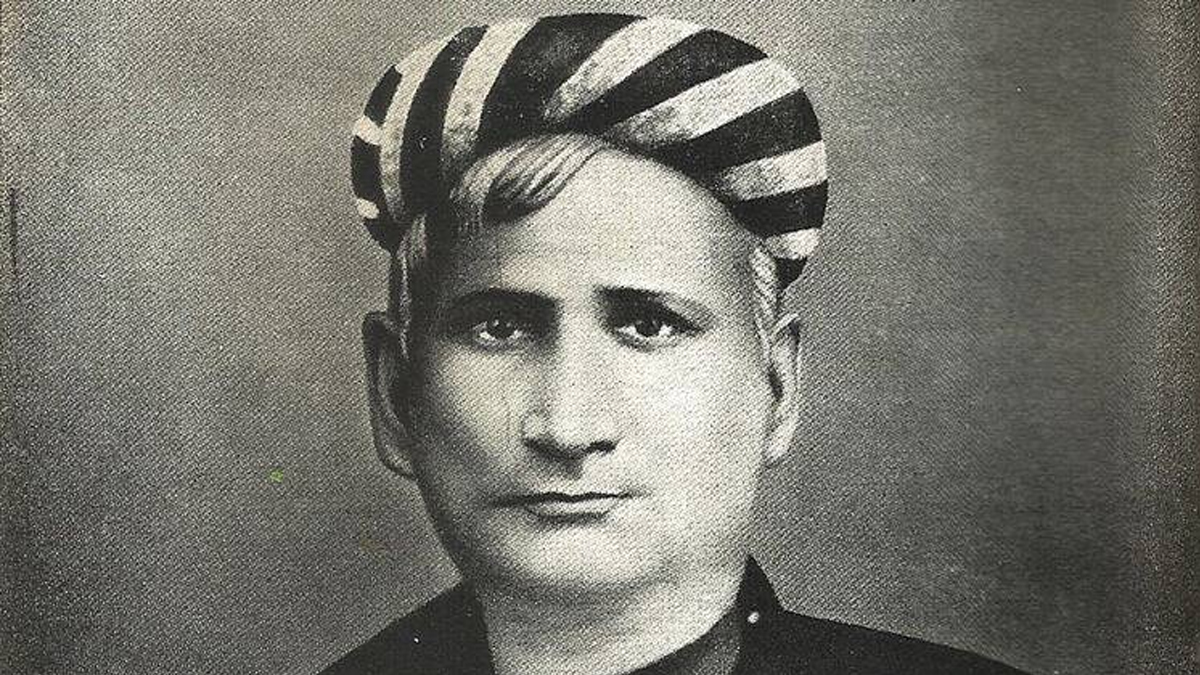শান্তনু রায়
বিনা আড়ম্বরেই চলে যায় তাঁর জন্ম ও প্রয়াণবার্ষিকী। সাধারনভাবে তাঁকে নিয়ে বর্তমান সমাজপরিসরে তেমন কোন আগ্রহ না থাকলেও প্রয়াণের সোওয়া শতক পরেও তাঁর বিরুদ্ধে আলোচনা চর্চা ও সমালোচনার নামে চর্বিত চর্বণে সেই একই সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ উথ্থাপিত হয়ে থাকে পণ্ডিতম্মন্যতার নতুন নতুন ‘গবেষণা’য়। ধর্মীয় ভিন্নতাজনিত কারণে বাঙালি জাতীয়তাবাদের অন্তর্নিহিত টানাপোড়েনের আলোচনায় যথারীতি বারবার আসে বঙ্কিমের বহুচর্চিত আনন্দমঠ উপন্যাসটি ।অভিযোগও সেই বহুদা জ্ঞাপিত পুরাতন যার জন্য জীবৎকালেও তিনি হয়েছিলেন একশ্রেণীর দ্বারা সমালোচিত।
Advertisement
বাংলাদেশের একাংশের কাছে ইদানীং জনপ্রিয় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি আহমদ ছফা তাঁর শতবর্ষের ফেরারিঃ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯৯৭) গ্রন্থে ‘মানুষের যাবতীয় সৃষ্টি কর্মের মধ্যে রাষ্ট্রই হলো সর্বাধিক গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়’ উল্লেখ করে মন্তব্য করেছেন – কিন্তু রাষ্ট্র যে সমাজের সার্বজনীন কল্যাণের নিয়ন্তা সে জিনিসটি উনবিংশ শতাব্দীর কোন কৃতবিদ্য ব্যক্তির মানস ফুড়ে জন্মাতে পারেনি। একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রই ছিলেন ব্যতিক্রম। বঙ্কিম ছিলেন আধুনিক বাংলা তথা ভারতের সর্বপ্রথম রাষ্ট্রবেত্তা। তিনি এও স্বীকার করেছেন-বাংলা তথা ভারতের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের উন্মেষ্ পর্বে বঙ্কিমের চিন্তা এমন একটা গভীর মর্মবেগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলো, অনুশীলন এবং যুগান্তর দুটি সন্ত্রাসপন্থী রাজনৈতিক সংগঠনের নেতা ও কর্মীরা বঙ্কিমকে তাদের গুরু এবং আনন্দমঠ গ্রন্থটিকে প্রেরণা পুস্তক হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।
Advertisement
বাঙালি জাতীয়তাবাদের অন্দরমহলে একটা টানাপোড়েন ছিল এবং আছেও- ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক ভিন্নতাহেতু বা পারিপার্শ্বিক অন্য কোন কারণে-এ রূঢ় বাস্তব। প্রসঙ্গত প্রায় পচাঁনব্বই বছর আগে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ধর্মমত ও সমাজরীতি সম্বন্ধে হিন্দু-মুসলমানে শুধু প্রভেদ নয় বিরুদ্ধতা আছে একথা মানতেই হবে। এতদিন সেই গোড়ার দিকে এক রকমের মিল ছিল। পরস্পরের তফাত মেনেও আমরা পরস্পর কাছাকাছি ছিলুম। সম্প্রদায়ের গন্ডির উপর ঠোকর খেয়ে পড়তে হত না, সেটা পেরিয়েও মানুষে মানুষে মিলের যথেষ্ট জায়গা ছিল। হঠাৎ এক সময়ে দেখা গেল, দু’ই পক্ষই আপন ধর্মের অভিমানকে উচিয়ে তুলতে লেগেছে। যতদিন আমাদের মধ্যে ধর্মবোধ সহজ ছিল ততদিন গোঁড়ামি সত্ত্বেও কোনো হাঙ্গামা বাধেনি। কিন্তু এক সময়ে যে কারনেই হোক, ধর্মের অভিমান যখন উগ্র হয়ে উঠল তখন থেকে সম্প্রদায়ের কাঁটার বেড়া পরস্পরকে ঠেকাতে ও খোঁচাতে শুরু করলে। (কালান্তর)
রবীন্দ্রনাথ কথিত সেই ‘একসময়’ কখন কিভাবে এল এবং তাতে কার কি ভূমিকা ছিল সে বিচার বিশ্লেষন এ নিবন্ধের প্রতিপাদ্য নয়; তেমনই নয় ‘পরস্পরকে ঠেকানো ও খোঁচানো’র সেই প্রয়াসের চরম পরিণতিতে যে তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশবিভাগপূর্বক ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে স্বাধীনতা প্রাপ্তি হয়েছিল তারই স্বাভাবিক প্রভাবজনিত পারস্পরিক অবিশ্বাস ও বিরুপতা সময়ের সঙ্গে হ্রাস পেয়েছে না পরবর্তীতে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের আবির্ভাবের পরেও আরও ব্যাপ্ত ও নব-বিদ্বেষ বিষে জারিত ও পোক্ত হয়েছে সে বিচারও।
প্রসঙ্গত, বঙ্কিম-মানসেও ছিল-বাংলা হিন্দু মুসলমানের দেশ, একা হিন্দুর দেশ নহে। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান এইক্ষণে পৃথক-পরস্পরের সহিত সহৃদয়তা শূন্য। বাংলার প্রকৃত উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় যে, হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য জন্মে। একথাও স্মর্তব্য যে বিপিনচন্দ্র পাল ও চিত্তরঞ্জন দাশের মতো বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তিত্বরাও বঙ্কিমচন্দ্রকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের নির্মাতা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠিত হননি।
তথাপি দুর্ভাগ্যজনকভাবে আনন্দমঠের স্রষ্টা বিধায় বঙ্কিমকে কেবল হিন্দু জাতীয়তার প্রাণপ্রতিষ্ঠার ‘অপরাধে’ চিহ্নিতকরণের এক মানসিকতা বিধৃত বিংশ শতকের উপান্তে দাঁড়িয়েও আহমদ ছফা কৃত বঙ্কিম-মূল্যায়নেও। ওই গ্রন্থে তিনি মন্তব্য করেছেন ‘যদি বাংলাদেশ বিভাগ করার কোন একজন ব্যক্তিকে দায়ী করতে হয়, তিনি অবশ্যই বঙ্কিম’।
১৯০৫-এ কার্জনের বঙ্গভঙ্গের প্রণোদনায় ১৯০৬-এ ঢাকায় মুসলিম লীগ গঠনের তথ্য স্মরণে রাখলে বাংলাভাগের (১৯৪৭) জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে অভিযুক্ত করার প্রবণতায় ইতিহাস চর্চায় অমনোযোগই সূচীত করে। কারণ প্রথমত মধ্যবর্তীকালের ইতিহাস যথাযথ পর্যালোচনা করলে ঐ মন্তব্যটি- বঙ্কিমনিন্দায় সোৎসাহে ব্যবহৃত হলেও (যেমনটি নজরে এল সাম্প্রতিক একটি নিবন্ধে)— অতি-সরলীকরণ, অতিশয়োক্তি এবং বিদ্বেষ-বিষে সত্য-বিমুখতার দোষে দুষ্ট প্রতিপন্ন হতে বাধ্য।
উল্লেখ্য, ঠিক পরের বাক্যটিতেই ছফা স্বীকার করেছেন— অনেকে আপত্তি উত্থাপন করে বলতে পারেন, বাংলা এবং ভারত বিভাজনের মাল মসলাসমূহ এই দেশীয় সমাজ কাঠামোর অভ্যন্তরে আত্মগোপন করে অনুকুল পরিস্থিতির প্রতীক্ষা করেছিলো। ইতিহাসের চোরাগোপ্তা স্রোতসমূহ বঙ্কিম মানসের ওপর চাপ সৃষ্টি করে, তাঁকে দিয়ে ইতিহাসের ধাত্রীর ভূমিকা পালন করিয়ে নিয়েছিলো। বঙ্কিম ইতিহাসের যন্ত্রের কাজটিই করেছিলেন।
বস্তুত তৎকালীন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ব্যাপারটি এভাবে ভেবে নিলেই সঠিক হয় যে সে সময়ে পরাধীন দেশের জাতিগঠনে, হতমান দেশবাসীর ‘মূঢ় মুক ম্লান মুখে’ ভাষা যোগানোর জন্য এমন রচনাই যুগের দাবি ছিল।বরং একথাও বলার যে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় ‘nation builder’ তিনি এক মুহুর্তের তরে বিস্মৃত হন নি স্বদেশের কথা। এই গঠনের কাজটি,যার অপরিসীম প্রয়োজনীয়তা সেই সময় ছিল, বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের মাধ্যমে করে গেছেন সারা জীবন। সেই প্রেক্ষিতে বঙ্কিমের হিন্দু জাতীয়তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা বা ইসলাম বিদ্বেষের ‘অপরাধ’ প্রমাণে নিছক তাঁর উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর সংলাপ কিংবা ‘বন্দেমাতরম’ সঙ্গীতের মাধ্যমে স্বদেশকে মাতৃজ্ঞানে বন্দনায় উদ্বুদ্ধ করাকে উদাহরন হিসেবে উত্থাপন কতখানি সমীচীন তা ভেবে দেখার মতো।
ঘটনা হলো আনন্দমঠ প্রকাশিত হওয়ার প্রায় তেইশ বছর পরে ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে উত্তাল বাংলায় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় নামে এক বর্নময় চরিত্র যিনি একাধারে রবীন্দ্রসুহৃদ আবার তীব্র ইংরেজ বিরোধী যার দেশপ্রেম ছিল নিখাদ তিনি তাঁর ‘সন্ধ্যা’ পত্রিকায় উদ্দীপক লেখনীতে ইংরেজের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম ঘোষণা করেন এবং আনন্দমঠের দৃষ্টান্তের উল্লেখে দেশমাতৃকার চরণে আত্মবলিদানের জন্য বাংলার তরুণদের প্রতি ওজস্বিনী ভাষায় তাঁর আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সশস্ত্র স্বদেশী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়া অগ্নিযুগের সেই বিপ্লবীদের (ছফা-কথিত সন্ত্রাসবাদী নন) অনেকের কাছে আনন্দমঠ ছিল অবশ্য পাঠ-সত্য। কিন্তু এর মধ্যে ধর্মীয় বাদবিচারের কোন অনুষঙ্গ ছিলনা। তথাপি এই আলোচনায় যদি এমন অনুসিদ্ধান্তে পৌঁছন যে আনন্দমঠ পাঠ করে কিংবা বঙ্কিম সাহিত্যে অনুপ্রাণিত হয়ে ‘তুলনামূলকভাবে অগ্রসর হিন্দু সমাজের স্বাধীনতা প্রয়াসী তরুন বিপ্লবীরা হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে মরণপন করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন’ তবে তা হবে সম্পূর্ণ ভুল ও বাস্তবের বিপ্রতীপ।
বর্তমান আবহে ‘ন্যাশনালিজম’ শব্দটিতে কোনো কোনো মহলে কিঞ্চিৎ অস্বস্তি ও একধরনের বীতরাগে প্রায়শ সমালোচনা হয় যে আসলে জাতীয়তাবাদের জন্য একটি ‘অপর’ প্রয়োজন হয়। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বর্তমান বিশ্বে সব দেশই জাতীয়তাবাদী ভিন্ন ভিন্ন রূপে। হ্যাঁ, তথাকথিত বামপন্থীরা ভ্রুকুঞ্চন করলেও এও সত্য যে পূর্ব ইউরোপের এবং অন্যত্র সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি এমনকি সোভিয়েত রাশিয়াও এর ব্যতিক্রম নয়। কারন দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ দেশগঠনের অন্যতম উপাদান; এর সঙ্গে অবশ্য ধর্মীয় অনুষঙ্গ সম্পর্কিত নয়।
এখানে স্মরণ করা যেতে পারে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উদগাতা বঙ্কিমের ‘ধর্মতত্ত্বে’ আত্মস্বরূপ (দ্বিতীয় সত্তা) গুরুর উক্তিটি-আমি তোমাকে যে দেশপ্রীতি বুঝাইলাম তাহা ইউরোপীয় প্যাট্রিয়টিজম নয়। … ইউরোপীয় প্যাট্রিয়টিজম এর তাৎপর্য এই যে পরসমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব এবং স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব, কিন্তু অন্য সমস্ত জাতির সর্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে। এই দুরন্ত প্যাট্রিয়টিজম এর প্রভাবে আমেরিকার আদিম জাতিসমূহ পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত।
১৮৮২-তে ‘আনন্দমঠে’র প্রকাশে যাঁরা বঙ্কিম মূলত হিন্দু জাতীয়তাবাদের নির্মাতায় রূপান্তরিত— এমন একটি ‘অভিনব’ আখ্যান নির্মাণের প্রয়াসী তাঁরা সচেতনভাবে বিস্মৃত যে ১৮৮৭ সালে প্রকাশিত ‘সীতারাম’ বঙ্কিমের সর্বশেষ উপন্যাস যার আট বছর আগে ১৮৭৯ এ ‘সাম্য’ রচনার প্রায় সাত বছরের মধ্যে ১৮৮৬-তে ‘কৃষ্ণচরিত্র’ ও ন’বছর ব্যবধানে ১৮৮৮তে রচিত হল ‘ধর্মতত্ত্ব’ এর মত গ্রন্থ,যেখানে অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকের পাশ্চাত্যের নবমানবতাবাদী ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত এক বঙ্কিমকে পাওয়া যায়৷ ‘আনন্দমঠে’র সমসাময়িক তাঁর একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস ‘রাজসিংহ’ কিংবা পরবর্তী ‘সীতারাম’এ মুসলমান ফকির চাঁদশাহের বয়ানে সীতারামের উদ্দেশ্যে বলা কথাগুলিতে ব্যক্তি বঙ্কিম-মননের যে রূপ প্রতিভাত হয় সেই গুরুত্বপূর্ন দিকটিও অনেক সমালোচকের নজর এড়িয়ে যায়। আনন্দমঠেরও শেষ অংশে বঙ্কিম মহাপুরুষের বয়ানে বলেছেন, ‘তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা সনাতন ধর্ম নহে, সে একটা লৌকিক অপকৃষ্ট ধর্ম;… প্রকৃত হিন্দুধর্ম জ্ঞানাত্মক, কর্মাত্মক নহে। বস্তুত বঙ্কিমকে ‘হিন্দু জাতীয়তাবাদী’ আখ্যা দেওয়া আসলে ইতিহাসের এক বামপন্থী অপব্যাখ্যা মাত্র বলে মনে করেন অনেক ইতিহাসবিদ।
বঙ্কিমচন্দ্র সাম্প্রদায়িক লেখক ছিলেন কিনা এই প্রশ্ন বিচার করতে গিয়ে আহমদ ছফাও স্বীকার করেছেন যে বঙ্কিমচন্দ্র সাম্প্রদায়িক এ মতের অনুসারীদের মধ্যে যেমন হিন্দু লেখকেরা আছেন তেমনই তিনি সত্যিকারভাবে একজন অসাম্প্রদায়িক, আধুনিক উদার দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন লেখক এই মতাবলম্বীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশ আবার মুসলমান। এ প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে উল্লেখ্য বীরভুমের সুসন্তান পরবর্তীকালে বহরমপুর নিবাসী সাংবাদিক সাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় রেজাউল করীম মহাশয়ের নাম মহম্মদ আলী জিন্নার চৌদ্দ দফা শর্তের বিরুদ্ধে প্রবাসী পত্রিকায় তাঁর জোরালো এক লেখা প্রকাশিত হলে সেসময়ে আলোড়ন পড়ে গিয়েছিল। আনন্দমঠ সম্বন্ধে একশ্রেণীর মুসলমানদের তীব্র বীতরাগের প্রেক্ষিতে বঙ্কিমের আদর্শের অনুসারী না হয়েও মুসলিম মানসে জাতীয়তাবাদের প্রসার ঘটানোয় নিরলস প্রয়াসী রেজাউল করীম ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত তাঁর ‘বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ’ গ্রন্থে লিখছেন, ‘কেহ কি দেখাইতে পারিবেন যে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সমগ্র গ্রন্থে কোথাও ইসলাম ধর্মকে আক্রমন করিয়াছেন?… ইসলামের রীতিনীতি, সৌন্দর্য প্রভৃতির প্রতি তিনি কি ব্যঙ্গোক্তি করিয়াছেন? তাহা যদি না করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে ইসলাম বিদ্বেষী বা মুসলমানের শত্রু মনে করিবার কোন কারন থাকিতে পারে না’।
শিল্পকলাকে কেবলমাত্র শৈল্পিক মাপকাঠিতে বিচারের তত্ত্বে অনাগ্রহী বিদ্বজনদেরও সম্ভবত অজানা নয়, যে বঙ্কিমের এই উপন্যাস ‘আনন্দমঠ’ সম্বন্ধে রেজাউল করীম আট দশক আগেই তাঁর ওই গ্রন্থে কি বলেছিলেন- “আনন্দমঠ শুধু আনন্দ দেয় নাই, দিয়াছে প্রাণ, দিয়াছে উৎসাহ, প্রাণের পরতে পরতে ছুটাইয়াছে আগুনের ফোয়ারা। প্রাণে জাগাইয়া দিয়াছে দেশাত্মবোধের মহান আদর্শ।… আনন্দমঠ না থাকলে পরবর্তী যুগের কোন আন্দোলন (যেমন স্বদেশী, হোমরুল, খিলাফত, অসহযোগ) সার্থক ও পূর্ণ হইত না… স্বদেশীযুগ হইতে এ পর্যন্ত জাতীয় জাগরনের জন্য যে সব আন্দোলন হইয়াছে, আনন্দমঠ পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে তাহার সবটাতে অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছে।… আনন্দমঠের সুমধুর ‘বন্দেমাতরম’ ধ্বনির তালেতালে জাতি ভেদাভেদ ভুলিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে কর্তব্যের আহ্বানে-দেশের উদ্ধারের কাজে। আসমুদ্র হিমাচল প্রকম্বিত করিয়াছে অমর বঙ্কিমচন্দ্রের একটিমাত্র সঙ্গীত বন্দেমাতরম’। আবার ত্রিশের দশকে যখন সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন হয়ে চরম বঙ্কিম-বিদ্বেষে ১৯৩৮-এ বঙ্কিম জন্মশতবর্ষে যখন কলকাতায় প্রকাশ্যে আনন্দমঠ পোড়ানো হয় উৎকট উল্লাসের মাঝে, তখনও রেজাউল করীম একে মধ্যযুগের বর্বরতা আখ্যা দিয়ে গভীর দুঃখ ও হতাশা প্রকাশ করেন।
প্রসঙ্গত, আহমদ ছফার বঙ্কিম-বিচার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বাংলা দেশেরই বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক বাংলা একাডেমীর সভাপতি অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হকও, যাঁর নেতৃত্বে ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ উপন্যাস পরিষদের উদ্যোগে ‘বঙ্কিমচন্দ্র: সার্ধশত জন্মবর্ষে’ শীর্ষক যে অনুষ্ঠান হয় বিরোধিতা আসে তখনকার রাষ্ট্রপতি এইচ এম এরসাদ আরো কিছু ব্যক্তি ও এমনকী কিছু সংবাদপত্রের থেকেও। প্রসঙ্গত, তাঁর একমাত্র সন্তান নিহত হন একটি জেহাদী গোষ্ঠীর হাতে ২০১৫-য়। যাহোক অনুষ্ঠানে প্রদত্ত রেকর্ডকৃত বক্তৃতা এবং আরো কিছু লেখা নিয়ে প্রকাশিত হয় ‘বঙ্কিমচন্দ্র সার্ধশতবর্ষে’ নামে গ্রন্থ। এরই প্রতিক্রিয়ায় আহমদ ছফা লেখেন শতবর্ষের ফেরারী বঙ্কিমচন্দ্র। ফজলুল হক লিখছেন (ভোরের কাগজ সাময়িকী, ২৮ জুন, ২০২৪)— ১৯৩৮ সালে বঙ্কিম জন্মশতবর্ষ উদযাপনকালে কলকাতার গড়ের মাঠে মওলানা আক্রম খাঁর নেত্তৃত্বে অনুষ্ঠিত ‘আনন্দমঠের বহ্নি উৎসব’ এবং ১৯৯০-এর দশকে প্রকাশিত আহমদ ছফার ‘শতবর্ষের ফেরারি বঙ্কিমচন্দ্র’ অনুধাবন করলে বোঝা যায় ‘মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদী’ চিন্তাধারায় বঙ্কিম-বিদ্বেষ কত প্রবল।
বলাই বাহুল্য, প্রায় সওয়া শতক আগের বঙ্কিম-মানস ও সাহিত্য মূল্যায়ন বিংশ শতকের উপান্তের একটি রচনাকে ধ্রুবসত্য জ্ঞানে বিক্ষিপ্ত বাক্য উদ্ধৃত করে সম্পন্ন হলে বিভ্রান্তি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। বঙ্কিমকে বিচার করতে হবে তাঁর সমসাময়িক সমাজ ও কালের প্রেক্ষিতে— সময়ের দাবিরও আবহে, আজকের দিনের নিরিখে যেমন নয় তেমনই নয় গত নব্বই দশকের পড়শি দেশের আবহে।
তখনকার বাংলাদেশের আবহ খানিকটা হয়ত আন্দাজ করা যায় বাংলাদেশের বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ও সাহিত্যিক অধ্যাপক ড. মুনতাসীর মামুনের বাংলাদেশ: বাঙালি মানস, রাষ্ট্র গঠন ও আধুনিকতা গ্রন্থে (২০০৭) গ্রন্থে এই পর্যবেক্ষণ থেকে— বাংলাদেশে গত এক দশকে মৌলবাদের উত্থানে বাংলাদেশ, বাঙ্গালির রাষ্ট্র থেকে মুসলমানদের রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে এবং ১৯৭৫-এর পর থেকে এ ধারণাটাই তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে শাসক দলের তরফ থেকে তো, বিদেশি প্রচার মাধ্যমেও যে এটি মুসলমানেরই আবাসভূমি। উল্লেখ্য বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ববিদ তালাল আসাদকে উদ্ধৃত করে ড. মামুন লিখেছেন— তালাল আসাদ নির্ধারিত মাপকাঠিতে বর্তমান বাংলাদেশকে বিচার করলে অবশ্যই আধুনিক বলা যাবে না, বরং ১৯৭১-এর বাংলাদেশ সে মাপকাঠিতে হয়ত উতরে যেতে পারে।
অধ্যাপক ফজলুল হক আরও বলেছেন, আমার ধারণা, স্বাধীন মূল্যবোধ ও যুক্তি অবলম্বন করে ইতিহাসবিচার করলে এবং বঙ্কিমের উপযোগিতা বুঝতে চাইলে এই বঙ্কিম বিদ্বেষ থাকবে না। ওই সুদীর্ঘ প্রবন্ধে আরও বলেছেন যে বাংলাদেশে উন্নত নতুন ভবিষ্যত সৃষ্টির প্রয়োজনে নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সঙ্গে ব্রিটিশ শাসিত বাংলার রেনেসাঁস ও বঙ্কিম চন্দ্রের পুনর্পাঠ আজ একান্ত প্রয়োজন। তাঁর মতে বাংলা হিন্দু-মুসলমানের দেশ একথা স্বীকার করে নিয়েও বঙ্কিম হিন্দু জাতীয়তাবাদী ছিলেন। বিচার করতে গেলে দেখা যাবে তাঁর চিন্তা যতটা ধর্মীয়, তার চেয়ে অনেক বেশি মানবতান্ত্রিক। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের (১৯০৫-১১) সময় থেকে রাজনৈতিকভাবে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদ পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপ নিয়ে সামনে আসতে থাকে। তখন থেকে সাম্প্রদায়িকতাবাদী রাজনীতির কারণে ও প্রভাবে, বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তার মানবতান্ত্রিক দিকটি বহুলাংশে চাপা পড়ে যায়।আহমদ ছফার ‘শতবর্ষের ফেরারি বঙ্কিমচন্দ্র’-এই নামটি স্বাধীন বাংলাদেশের এক ধারার লোকদের কাছে খুব প্রিয় হয়েছে। তারা যে বঙ্কিমচন্দ্রের কিংবা আহমদ ছফার চিন্তাকে ঠিকমতো বুঝতে পেরেছেন, তা মনে হয় না। তাদের মধ্যে ভারতবিদ্বেষ ও হিন্দুবিদ্বেষ প্রবল।
অথচ বঙ্কিমচন্দ্রই একমাত্র সাহিত্যিক যিনি তাঁর উপন্যাসে যে অসংখ্য মুসলমান চরিত্র সৃষ্টি করেছেন সেগুলি সাহিত্যে অমর হয়ে আছে। তাঁর বিরুদ্ধে বিশেষ ধর্মবিদ্বেষী হওয়ার অভি্যোগ কেবল অসত্য অনৈতিক নয় এর দ্বারা নিজ মনের ধর্মীয় কলুষতার প্রকাশই ঘটে।
এ বঙ্গেও পরিকল্পিত (অপ)প্রয়াসের ক্ষান্তি নেই আজও। একাজে কখনও ঢাল করা হয় বঙ্কিম-উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর উক্তিকে কখনো প্রেক্ষিত বিচারে অমনোযোগে মীর মোসারফ হোসেনের ‘বিষাদসিন্দু’র মূল্যায়নে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসাসূচক মন্তব্যেরও অপব্যাখ্যায়। অথচ বদরুদ্দীন উমরের ‘মুসলমানদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন’ প্রবন্ধ কিংবা গবেষক রফিউদ্দিন আহমেদের The Bengal Muslims 1871-1906:A quest for identity গবেষণামূলক গ্রন্থে ঋদ্ধ অনেকেরই স্মরণে আসতে পারে যে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যে বিশ্বাসী বঙ্কিমচন্দ্রও কত আগেই তো বলেছিলেন, যতদিন উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদিগের মধ্যে এমন গর্ব থাকিবে যে, তাহারা ভিন্নদেশীয়, বাংলা ভাষা তাদের ভাষা নহে, তাহারা বাংলা লিখিবেন না, কেবল উর্দু-ফারসির চালনা করাইবেন ততদিন সে ঐক্য জন্মিবে না। কেননা জাতীয় ঐক্যের মূল ভাষার একতা।
২৬ জুন এই মনিষীর ১৮৭তম জন্মবার্ষিকী।
Advertisement