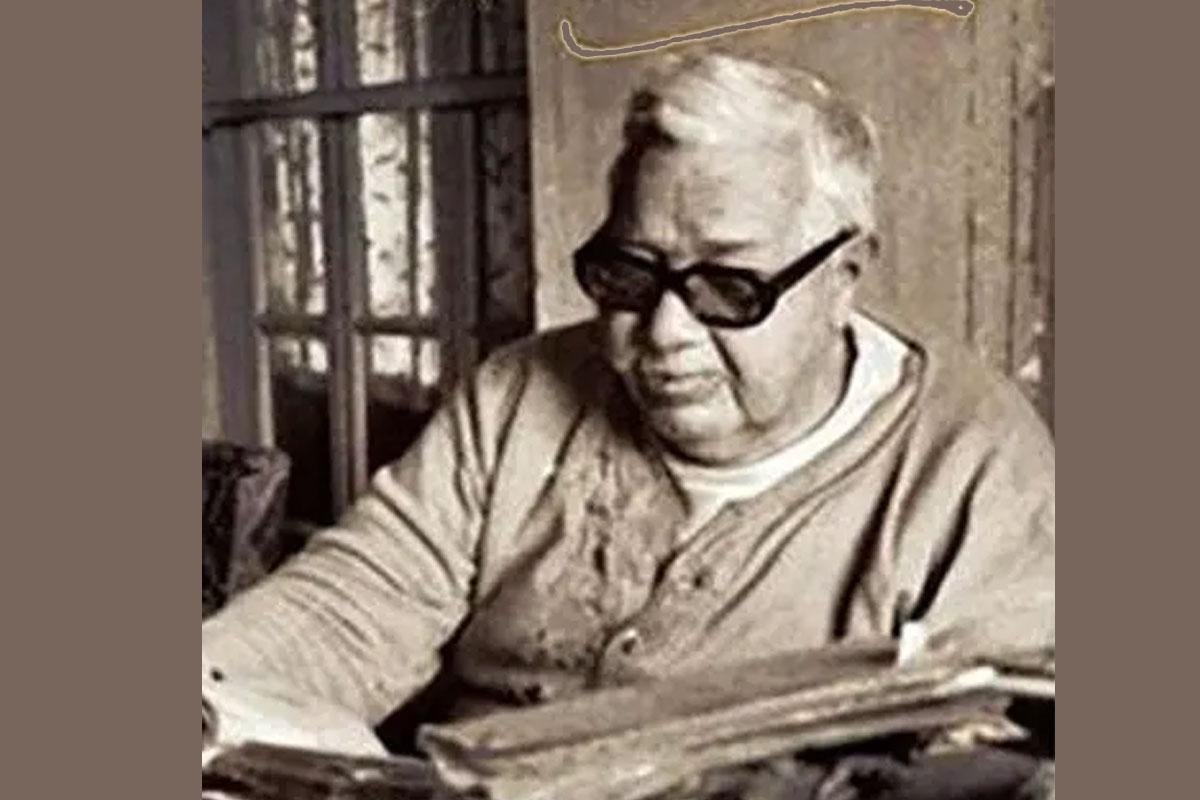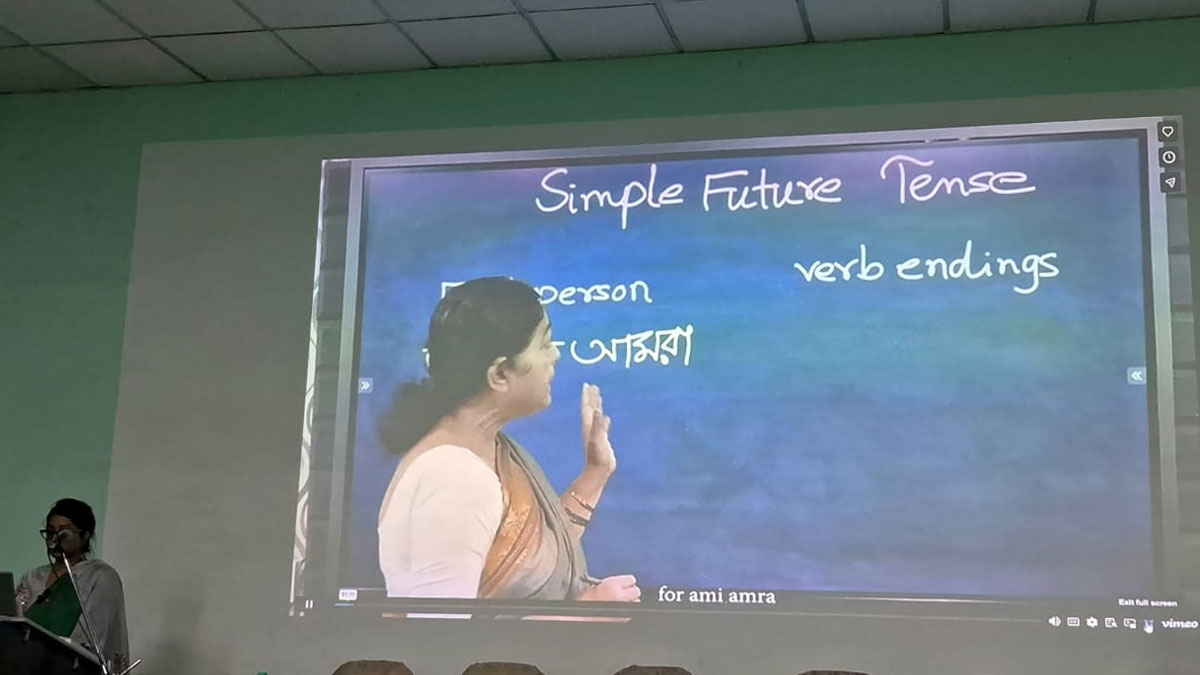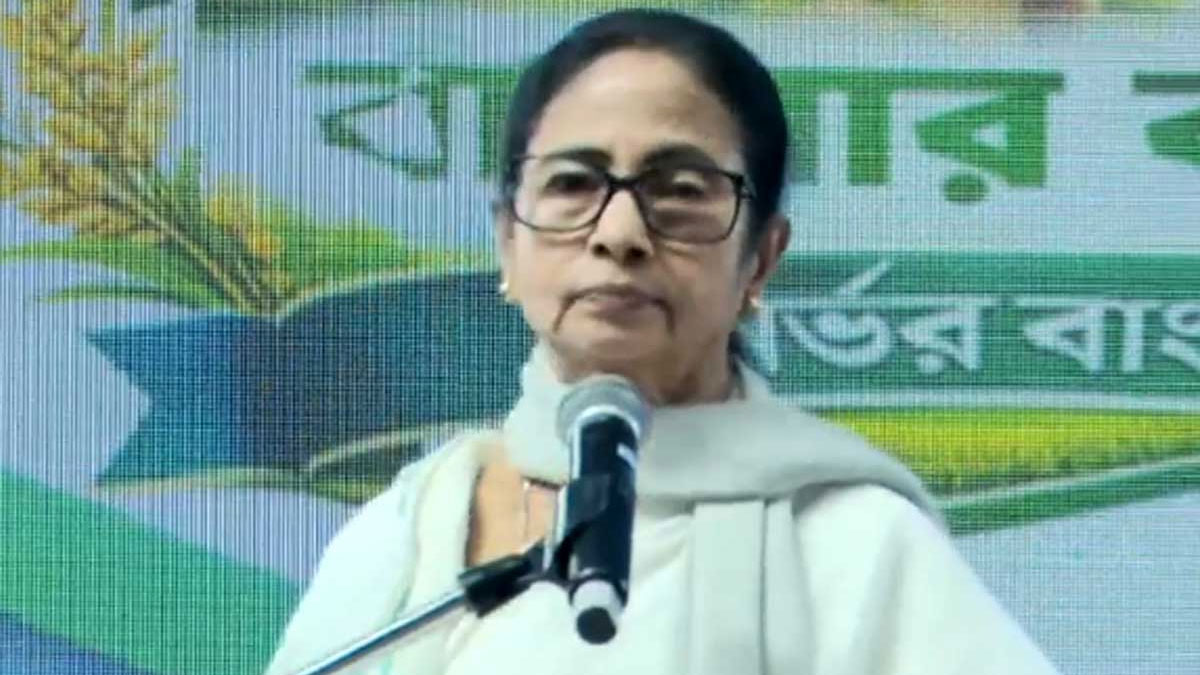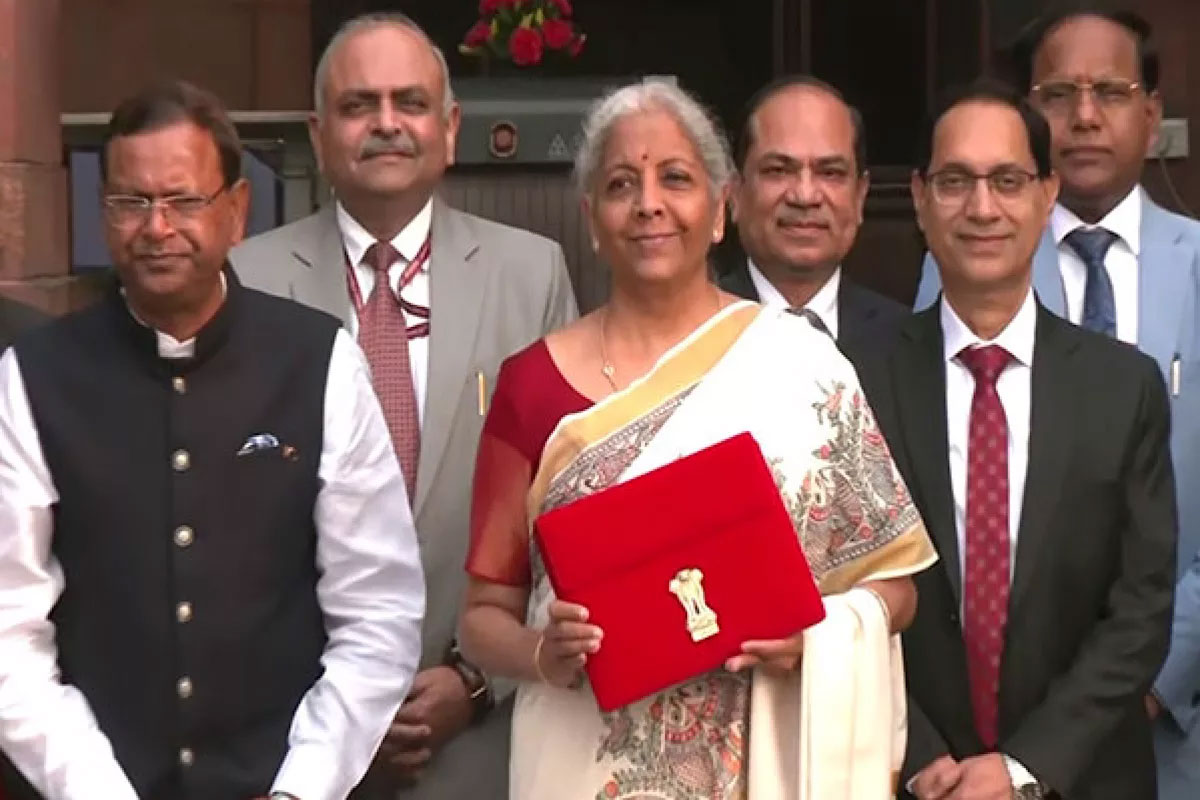শ্রীসুকুমার সেন
Advertisement
পূর্ব প্রকাশিতর পর
Advertisement
গ. সন্ধির নিয়ম কঠোরভাবে প্রযুক্ত হত ধ্রুপদী সংস্কৃতে।
ঘ. ঝোঁকের কোনো রূপতাত্ত্বিক, শব্দার্থগত তাৎপর্য রইল না।
ঙ. ধ্রুপদী সংস্কৃতের শব্দরূপ ও ধাতুরূপ অপেক্ষাকৃত সরল।
ভাষাতাত্ত্বিক ক্ষেত্র হিসাবে ভারতবর্ষের একটি বৈশিষ্ট্য হল একই সময়ে আমরা একাধিক ভাষার ব্যবহার দেখতে পাই—একটি সাহিত্যের ভাষায় আরেকটি কথ্য ভাষায়। তাই আমরা লক্ষ্য করি সর্বভারতীয় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বাহক হিসাবে একটি ভাষা এবং রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণের এবং বৌদ্ধ-সংস্কৃতির আরেকটি ভাষা। মধ্যভারতীয় আর্যভাষার স্তরেও এই প্রক্রিয়া সক্রিয় ছিল, এমনকি বর্তমান কালেও সাধু এবং চলিতের মধ্যেও আমরা সেই প্রবণতা লক্ষ্য করতে পারি।
মোটামুটিভাবে খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতক থেকে মধ্যভারতীয় আর্যভাষার সূচনা ধরা যায়। মধ্যভারতীয় আর্যভাষার প্রথম স্তর মূলত প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষারই ভগ্ন এবং সরলীকৃত রূপ। এবং ১ম খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতীয় আর্যভাষায় বিভিন্ন উপভাষার পরিচয় অত্যন্ত সুস্পষ্ট অশোকের শিলালিপিতে। বিভিন্ন ধ্বনিতাত্ত্বিক এবং রূপতাত্ত্বিক সরলীকরণের মাধ্যমে মধ্য ভারতীয় আর্যভাষাই নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় পরিণত হয়েছে। তবুও মধ্য ভারতীয় আর্যভাষাকে সংস্কৃতের সঙ্গে কঠোর এবং দীর্ঘ প্রতিযোগিতা করতে হয়েছিল।
সম্ভবত উত্তর পশ্চিম এবং উত্তর ভারতের বৈদেশিক রাজতন্ত্রই মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার স্থানে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষাকে পুনরায় রাজভাষা অর্থাৎ শাসনকার্য ও জনসংযোগের ভাষা হিসাবে প্রচলনের চেষ্টা করেছিল। অথচ অশোকের সময়েই মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা প্রশাসনিক কাজে ব্যবহৃত হত। তার প্রমাণ পাই ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত অশোকের অনুশাসনে। খ্রীস্টীয় ৪র্থ শতাব্দের শুরুতেই মধ্যভারতীয় আর্যভাষা সংস্কৃতের কাছে হার মানে। চীনীয় তুর্কীস্থানের কয়েকটি আর্যভাষাভাষীদের মধ্যে প্রশাসনিক স্তরে মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার দ্বন্দ্বের প্রমাণ মিলেছে খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দেও গীর্ণারে প্রাপ্ত রুদ্রদামনের শিলালেখে। লেখটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত (খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দ)। অথচ এর কয়েক শতাব্দ আগেই অশোকের অনুশাসন মধ্যভারতীয় আর্যভাষা ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
বিভিন্ন গ্রাম্য ও ইতর উপভাষা প্রচলনের প্রবণতা আমরা খুঁজে পাই পালি জৈন প্রাকৃত প্রভৃতি ভাষার সাহায্যে। এইসব ভাষাই সংস্কৃতের সঙ্গে নব্য ভারতীয় আর্যভাষার সংযোগসূত্র ধরিয়ে দেয়। এ প্রসঙ্গে এ কথাই বলা যেতে পারে মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা সংস্কৃত থেকেই প্রাণরস আহরণ করে সমৃদ্ধিশালী হয়েছিল।
প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার তুলনায় মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:
ক. স্বরধ্বনির সংখ্যার উল্লেখযোগ্য হ্রাস। ঋ, ঋৃ, ৯ প্রভৃতির লোপ। দীর্ঘ দ্বি-স্বরধ্বনি ঐ এবং ঔ স্বরৈকধ্বনিতে পর্যবসিত হল। যথা ঋষি>ইসি (পালি) রিসি (প্রাকৃত); মৃগ>মগ, মুগ; কৃত>কট, কত, কিত; বৃক্ষ>রুক্ষ; বৃষভ, ঋৃষভ>রিসভ, উসভ; বৃদ্ধ>বুঢ্ঢ; সৈন্ধব>সেন্ধব। অতঃপর সংস্কৃত সাধুভাষা এবং প্রাকৃত চলিত হিসাবে গৃহীত হয়, এই প্রক্রিয়া খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দ পর্যন্ত চলেছিল। রুদ্ধ অক্ষরের পূর্বে দীর্ঘ দ্বি-স্বরধ্বনি হ্রস্ব হল।
(ক্রমশ)
Advertisement