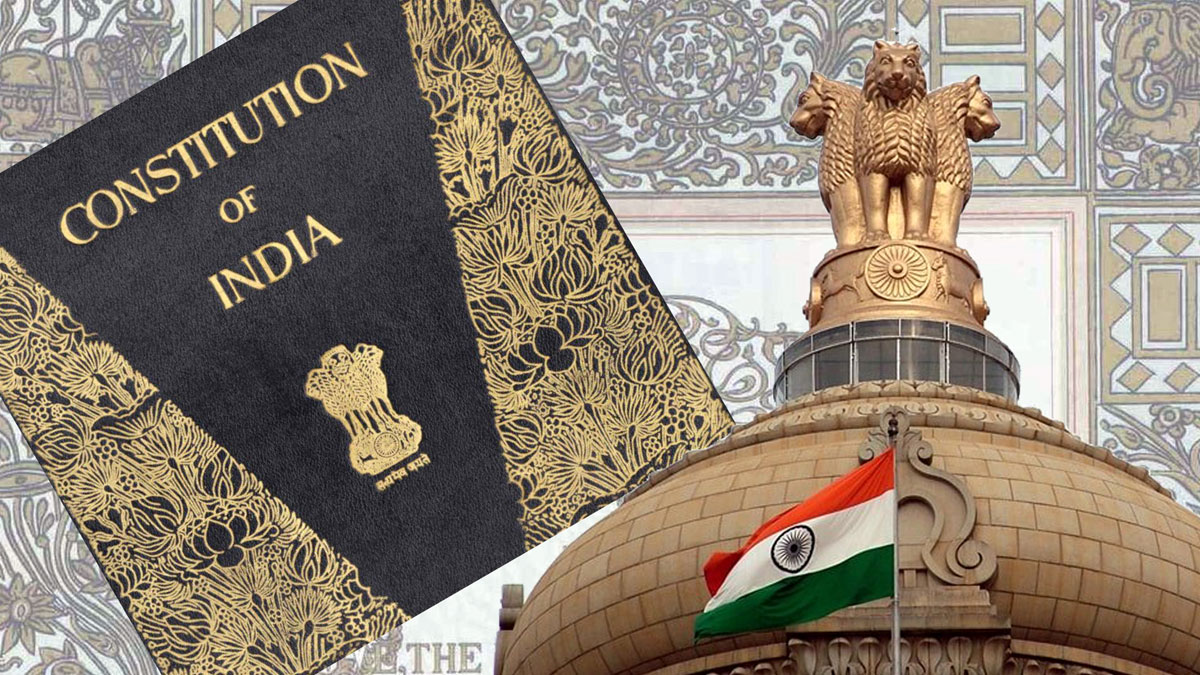শোভনলাল চক্রবর্তী
বিবিধ রাজনৈতিক ডামাডোলের মধ্যে অনেক জরুরি সংবাদ চাপা পড়ে যায়। তেমনই একটি সংবাদ শোনা গিয়েছিল গত বছরের নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে। ভারতের সর্বোচ্চ আদালত সংবিধান বিষয়ক একটি অত্যন্ত গুরুতর পর্যবেক্ষণ করে এই মর্মে যে, ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ ও ‘সমাজতান্ত্রিক’ শব্দ দু’টি সংবিধানের মুখবন্ধে যোগ করার বিষয়টিকে নতুন করে কাঠগড়ায় তোলার কোনও দরকার নেই। গত কিছু বছর ধরেই দক্ষিণপন্থী হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক দলসমূহ বিভিন্ন পন্থায় বিভিন্ন মঞ্চে প্রচার করে চলেছে যে, জরুরি অবস্থাকালে সংবিধানের ৪২তম সংশোধনীতে এই দু’টি শব্দ যোগ করার ফলে রাষ্ট্রীয় চরিত্রটিকে পাল্টানো, এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুকে বিশেষ রকম ‘তোষণ’মূলক দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা হয়েছিল। সুতরাং শব্দগুলিকে বাদ দিতে হবে। সেই মর্মেই একটি মামলা সর্বোচ্চ আদালতে পৌঁছলে মাননীয় বিচারপতিরা স্পষ্ট একটি সূত্র দেন। সূত্রটি আসে সংবিধানের একেবারে প্রধান বক্তব্য থেকে, যেখানে আইনের সামনে সকল নাগরিকের সমতার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল, এবং নাগরিকের যে কোনও ধর্ম, বিশ্বাস, আচার পালনের স্বাধীনতা স্বীকার করা হয়েছিল। এই যে বক্তব্য— একেই এক কথায় ধর্মনিরপেক্ষ বলা যায়, এর থেকে বেশি কিছু পরবর্তী কালের সংশোধনেও বোঝাতে বা প্রতিষ্ঠা করতে চাওয়া হয়নি: বিচারপতিরা বলেন।সমাজতান্ত্রিক’ শব্দটি সংবিধানে থাকবে কি না, এই নিয়ে সংবিধান সভাতেও প্রচুর আলোচনা চলেছিল, শেষ অবধি বাবাসাহেব আম্বেদকরের একটি সংশয়ের কারণে শব্দটি আর প্রবিষ্ট হয়নি। আম্বেদকরের মনে হয়েছিল, পরপ্রজন্মকে কোনও একটি বিশেষ অর্থনৈতিক পথ নিতে সংবিধানমতে বাধ্য করা উচিত নয়।
Advertisement
লক্ষণীয়, বিশ শতকের মধ্যভাগে সমাজতন্ত্র বলতে যে সুনির্ধারিত মতবাদ বোঝানো হত, ভারতীয় সংবিধানে কিন্তু তা বলতে চাওয়া হয়নি। ১৯৭৬ সালে সংবিধান সংশোধনের সময়েও সমাজতন্ত্রের অর্থটি সচেতন ভাবে সীমিত রাখা হয়েছিল— শ্রেণি গোষ্ঠী ধর্ম লিঙ্গ নিরপেক্ষ ভাবে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। বিচারপতিরা আর একটি খুব জরুরি কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন— প্রশ্ন তোলার মানেই পিছু হটা নয়। কেন এই সংশোধন করা হল, সেই প্রশ্ন তোলাই যায়। কিন্তু তাই বলে সংশোধন বাতিল করে দেওয়ার মতো পদক্ষেপ— অপ্রয়োজনীয়। এর কারণ, দু’টি শব্দের কোনওটিতেই ভারতীয় সংবিধানের চরিত্রের কেশাগ্রমাত্র পরিবর্তন ঘটানো হয়নি। যা আগে ছিল, তাকে স্পষ্টতর করা হয়েছে মাত্র। এবং, ১৯৭৬ সালের ঢের আগে থেকে শব্দ দু’টির সুর যে শুধু ভারতীয় সংবিধানেই ছিল, তা নয়— স্বাধীনতা-উত্তর ভারতীয় জাতিরাষ্ট্রের ধারণার একেবারে গোড়ায় যে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র থাকবে, তা স্থির হয়েছিল দেশ স্বাধীন হওয়ার অন্তত দেড়-দু’দশক আগেই। বিরোধ ছিল, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল ধারণা দু’টির পক্ষে সমর্থন। উন্নয়নের সূত্র ধরে জাতীয়তার যে সংজ্ঞা ভারতনির্মাণের প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে, তার জন্য ধর্মনিরপেক্ষতা ও সামাজিক ন্যায়কেন্দ্রিক সমাজতন্ত্রের ধারণা অপরিহার্য।
Advertisement
বিজেপি শাসিত ভারতে যে ভাবে সংখ্যালঘু-বিরোধিতা বেড়েছে, এমনকি রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমেও বৈষম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাতে সুপ্রিম কোর্টের সংবিধান বিষয়ক এই বক্তব্যটির গুরুত্ব অপরিসীম। তাঁরা এও মনে করিয়ে দিয়েছেন যে জরুরি অবস্থা শেষে ১৯৭৮ সালে সংবিধানের ৪৪তম সংশোধনীর সময়ও বিষয়টি বিশদে আলোচিত হয়েছিল। এবং তখন বিচারবিভাগের শীর্ষে ছিলেন যাঁরা, তাঁরাও এই মত প্রদান করেছিলেন। রাজনীতির কূটচক্রে সাংবিধানিক আদর্শের গতি ঘুরিয়ে দেওয়া যায় না। ১৯৭৬ সালের সংশোধনীতে সেই গতি ঘুরিয়ে দেওয়া হয়নি, কেবল নবরূপে সংযোজিত হয়েছিল মাত্র। এখন আবার সেই সংযোজনকে রাজনীতির প্রয়োজনে মুছে দেওয়ার চেষ্টা— পরিত্যাজ্য।সংবিধানের প্রস্তাবনায় গোড়া থেকে ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক শব্দ দু’টি ছিল না, ইন্দিরা গান্ধীর আমলে ১৯৭৬ সালে ৪২তম সংশোধনীর মাধ্যমে তা যোগ হয়। এই ঘটনাকেই হাতিয়ার করে সাম্প্রতিক কালে বিজেপির নানা নেতা বার বার প্রশ্ন তুলছেন সংবিধানের প্রস্তাবনায় এই ধারণা দু’টির, বিশেষ করে ধর্মনিরপেক্ষতার যৌক্তিকতা এবং ‘অস্তিত্ব’ নিয়েই। তাঁদের যুক্তি, শুরু থেকে না থাকার অর্থ— সংবিধান-প্রণেতারা এই শব্দ দু’টি আদৌ প্রস্তাবনায় যুক্ত করতেই চাননি।
এ যুক্তি অত্যন্ত হাস্যকর— ১৯৭৬-এর আগে কি তবে ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ছিল না, হিন্দু রাষ্ট্র ছিল? স্বাধীনতা-উত্তর কালের যৎকিঞ্চিৎ সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন নাগরিকমাত্রেই জানেন, ধর্মের ভিত্তিতে হওয়া দেশভাগের পরিণাম দেখেই স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রনেতারা আরও বেশি করে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাকে ভারতের সংবিধানের মূল কাঠামোয় অঙ্গীভূত করেছিলেন। জওহরলাল নেহরু তো বটেই, তৎকালীন গণপরিষদের সকল সদস্যও এই ঐকমত্যে আসতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি— স্বাধীন সার্বভৌম ভারত যে এক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র তা বলার অপেক্ষা রাখে না, আলাদা করে উল্লেখ বাহুল্যমাত্র। তার পরেও যে তা আলাদা করে সংবিধানের প্রস্তাবনায় খোদিত হয়েছিল তার কারণ, ধর্মনিরপেক্ষতা-বিরোধী রাজনীতির ক্রমাগত মাথা তোলা বা বাড়বাড়ন্তের পরিস্থিতিতেও ভারত যেন তার মূল সুর থেকে কখনও বিচ্যুত না হয়। বিজেপির শাসনামলের এই ভারতই প্রমাণ, সংবিধানের মূল সুরটি কতখানি বেসুরে বাজছে। আজ সংবিধানের প্রস্তাবনা থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাকে বাদ দিতে শাসক দলের যাবতীয় তোড়জোড়, সুপ্রিম কোর্টের বারংবার মনে করিয়ে দেওয়াতেও কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না। লোকসভা নির্বাচনের আগে ‘চারশো পার’-এর ঢক্কানিনাদে কেন্দ্রের এই বার্তাও প্রচ্ছন্ন ছিল, সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভই শুধু বাকি, সংবিধান পাল্টানো তথা ধর্মনিরপেক্ষতার আনুষ্ঠানিক বিসর্জন সময়ের অপেক্ষামাত্র।
আপাতত তা করা যায়নি, কিন্তু সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণার উপরে নানাবিধ আঘাত যে ক্রমাগত আসতেই থাকবে তা পরিষ্কার। এই আঘাতের মুখে ভারতের বিচারব্যবস্থা এই মুহূর্তে ধর্মনিরপেক্ষতার যত্নশীল অভিভাবক। আদালত বারংবার বলেছে, ধর্মনিরপেক্ষতা শুধু সংবিধানের মূল কাঠামোর ভিত্তিই নয়, সাম্যের ধারণারও তা অচ্ছেদ্য অঙ্গ, সব ধর্মকে ‘সমান’ দৃষ্টিতে দেখা, কোনওটির প্রতি পক্ষপাত কিংবা বিভেদ না দেখানোই সমত্ব। সমাজতান্ত্রিকতার ধারণা নিয়ে তবু আলোচনা ও তর্ক চলতে পারে, কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নে কোনও আপস নয়।তবে আশঙ্কা দূর হয়েছে, এমন কথা বলার উপায় নেই। ধর্মস্থানের ইতিহাস খুঁড়ে দেখার যে প্রবণতা চতুর্দিকে অশান্তি, উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে, সেটি ষোলো আনা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। বাবরি মসজিদ-রাম জন্মভূমির ইতিহাস সেই রাজনীতির, আক্ষরিক অর্থেই, যুগান্তকারী অধ্যায়। সহিষ্ণুতা, সহাবস্থান এবং যুক্তসাধনার ভিত্তিতে গড়ে তোলা গণতন্ত্রের ধারণাকে সরাসরি অস্বীকার করে ধর্মাশ্রিত সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির আগুনে সংখ্যাগুরুবাদী রাজনীতির হাতিয়ার তৈরি করার যে পথ প্রায় চার দশক আগে উন্মোচিত হয়েছিল, ভারত সেই পথে বহু দূর অবধি এগিয়ে গিয়েছে। পিছন দিকে এগিয়ে গিয়েছে বলাই যুক্তিযুক্ত। সংখ্যালঘুর উপাসনাস্থল খুঁড়ে খুঁড়ে সংখ্যাগুরুর উপাসনাস্থলের চিহ্ন ‘আবিষ্কার’ করার যে ধুন্ধুমার তৎপরতা এখন দেখা যাচ্ছে, সেই ভয়ঙ্কর অভিযানের মধ্যে কোনও যথার্থ ধার্মিকতা নেই, নেই ইতিহাস-চর্চার কিছুমাত্র আকাঙ্ক্ষা, এ কেবল ‘হিন্দু ভোট’ এককাট্টা করার ষড়যন্ত্র। অযোধ্যা নামক ‘ঝাঁকি’র ফসল গোলাঘরে উঠেছে, এখন কাশী মথুরা-সহ ‘বাকি’ বিষবৃক্ষগুলির ফল আহরণের পালা।
১৯৯১ সালের আইনটি ছিল এই বিষময় সম্ভাবনা প্রতিরোধের একটি প্রকরণ। নতুন করে যেন আর কোনও বাবরি মসজিদ কাহিনির পুনরাবৃত্তি না হয়, সেই উদ্দেশ্যেই স্থিতাবস্থা বজায় রাখার এই আয়োজন হয়েছিল সে-দিন। সেই আইনের সাংবিধানিক বৈধতা বিষয়ে মহামান্য সর্বোচ্চ আদালত শেষ অবধি কোন সিদ্ধান্ত স্থির করবেন, তা অবশ্যই তাঁদের বিচার্য। কিন্তু সেই আইনি প্রশ্নের বাইরে, সুস্থ স্বাভাবিক কাণ্ডজ্ঞানের জায়গা থেকে, একটি নিতান্ত সহজ প্রশ্ন মনে রাখা আজ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।
স্বাধীনতার ৭৫ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে, শতবার্ষিকী উদ্যাপনের কথা হাওয়ায় ভাসছে। এমন একটি দেশের নাগরিকরা সমবেত ভাবে, জাতি ধর্ম বর্ণ ইত্যাদি যাবতীয় সঙ্কীর্ণ পরিচয় নির্বিশেষে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাবেন, না পিছন দিকে মুখ ফিরিয়ে খোঁড়াখুঁড়ি এবং ভাঙচুরের নব নব ধ্বংসকাণ্ডে মাতবেন? বহু কাল ধরে বহু ধর্ম-সংস্কৃতির টানাপড়েনে ভারততীর্থের সৃষ্টি, এ দেশে মাটি খুঁড়ে ‘আদি অতীত’কে উদ্ধার করতে গেলে শেষ অবধি প্রস্তরযুগেই ফিরে যেতে হবে। সেটাই কি বিশ্বগুরুর ভবিষ্যৎ? ১৯৯১ সালের আইনটি সম্পর্কে সরকারের অবস্থান জানতে চেয়েছে সর্বোচ্চ আদালত। প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর পারিষদবর্গ তথা তাঁদের পশ্চাদ্বর্তী নাগপুরের চিন্তানায়করা দাবানলের আগুনে ক্ষমতার রুটি সেঁকার তাড়নায় পিছন দিকেই এগিয়ে চলবেন কি না, দেখা যাক।
Advertisement