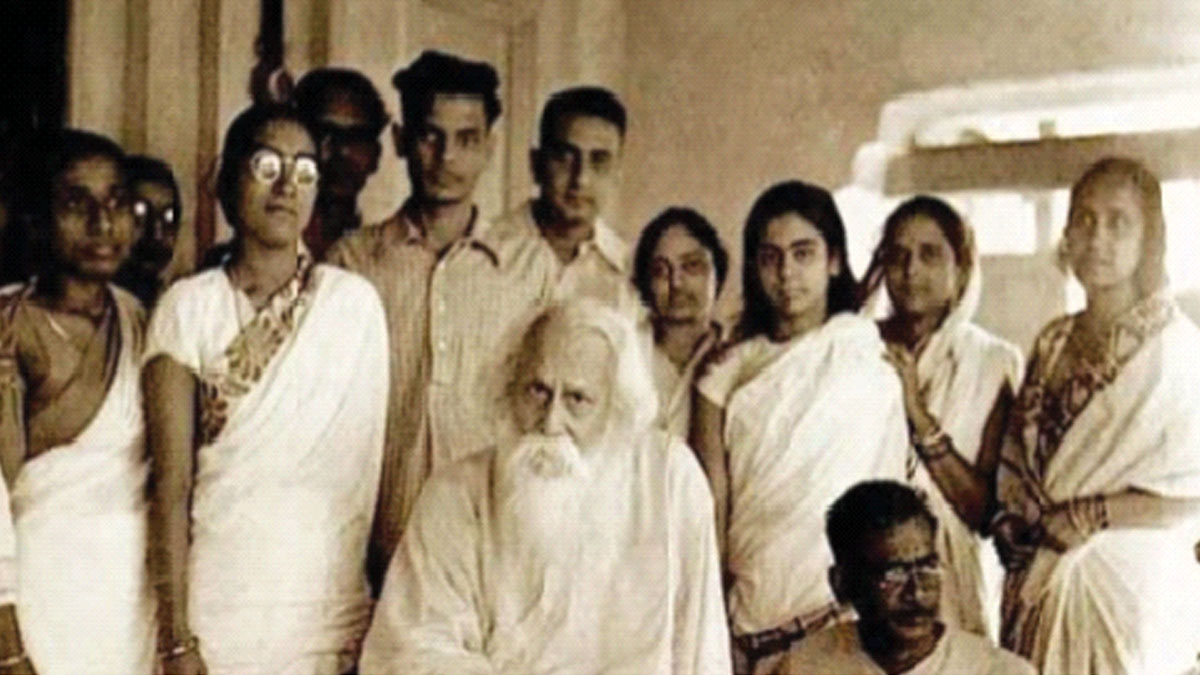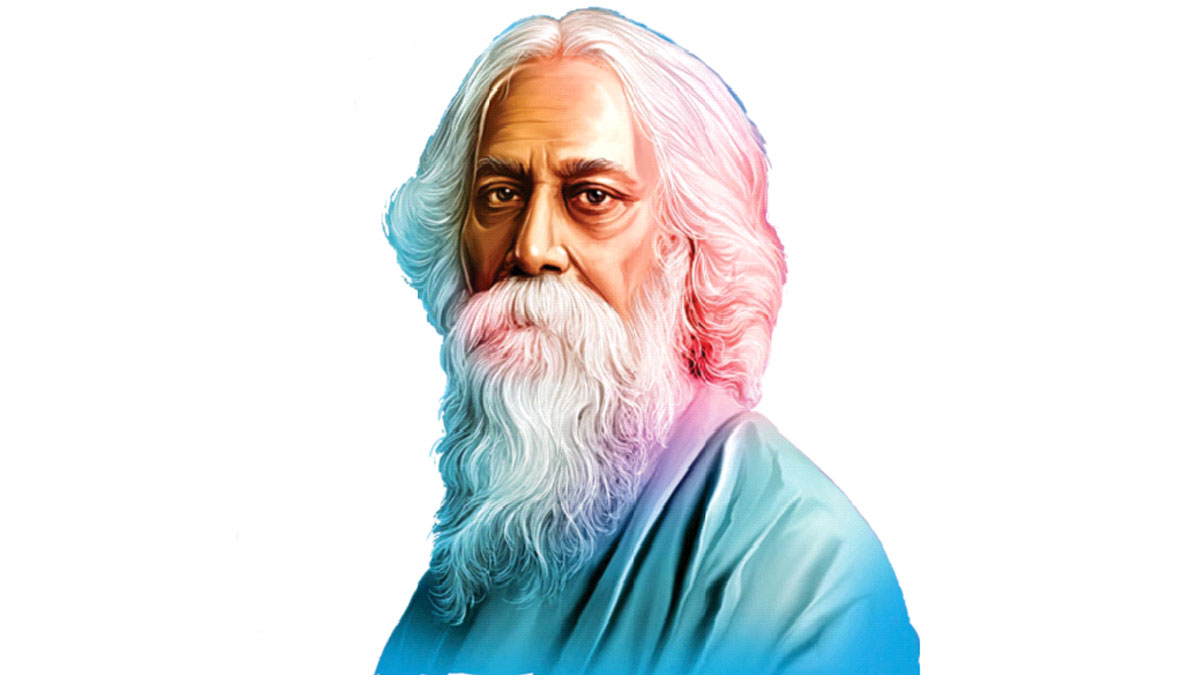শোভনলাল চক্রবর্তী
পাড়ায় বা কফি হাউসে রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে মোলাকাত আমার সেই কলেজবেলা থেকে। এঁরা প্রত্যেকে জীবনের নানা সময়ে নানা প্রক্রিয়ায়,রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে, সুকুমার রায়ের ভাষায় ‘স্টুপেন্ডাস অ্যামাউন্ট অব অ্যাস্টাউন্ডিং ইনফরমেশানস’ জোগাড় করে লোকজনের মধ্যে বিলিয়েছেন। মনে রাখতে হবে আমি যে সময়ের কথা বলছি সেই সময় রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট ইত্যাদি কিছুই ছিল না। অতএব তাঁরা তথ্য গোপন রাখলেও পারতেন, কিন্তু তাঁরা তা করেননি, নিজেদের সঞ্চিত ভাণ্ডার অকাতরে বিলিয়েছেন।
Advertisement
বিমলবাবু এঁদের মধ্যে প্রথম সারির লোক।উনি না থাকলে আমরা জানতেই পারতাম না যে প্রশান্ত নামে কে একজন রবি ঠাকুরের হিসেবের খাতা দেখে দিত। “আরে প্রশান্ত না থাকলে উত্তরায়ণের জমির পিছন দিকের আমবাগান কেনার কথা রবিদা ভাবতেই পারতেন না। একটা একটা করে পয়সা বাঁচিয়ে প্রশান্ত ওই জমি কিনে দিয়েছিল।” আমরা হাঁ করে শুনতাম।
Advertisement
বহু বছর বাদে সাহসে ভর করে এক দিন জিজ্ঞেস করেই ফেললাম, “আচ্ছা, ওই প্রশান্ত লোকটা কে?” উনি তাচ্ছিল্যের হাসি ঠোঁটের কোণে ঝুলিয়ে বলেছিলেন, “আরে তোমরা যাকে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ বলো, আমি রবিদা, নন্দদা, রাম, আর দু’চার জন ওকে প্রশান্ত বলেই ডাকতাম। পাটনার কাছে বাড়ি। বড়লোকের ছেলে। তা ওর বাপ এক দিন রবিদার পায়ে কেঁদে পড়ল গুরুদেব, আমার ছেলেটার কী হবে? আমি রবিদার কানে ফিসফিস করে বললেম, নিয়ে নিন, হিসেব রাখার জন্যও তো একটা লোকের দরকার। রবিদা কলমের এক খোঁচায় চাকরিতে বহাল করে নিলে। তার পর কী হল, সে তো তোমরা সবাই জানো।” আমরা হতবাক। বিমলবাবু জীবনে না হোক গোটা দশেক রবীন্দ্র-বিষয়ক বই লিখেছেন এবং সম্পূর্ণ বিনি পয়সায় জোর করে সেগুলো পরিচিতদের মধ্যে বিলিয়েছেন। সবচাইতে মারাত্মক ব্যাপার এই যে, কয়েক জন সেগুলো মন দিয়ে পড়েওছে এবং ভাগ্নে-ভাইঝিদেরও পড়িয়ে ইসকুল কলেজের পরীক্ষায় সেইসব থেকে রেফারেন্স টেনে উত্তর লিখিয়েছেন। এ নিয়ে অবিশ্যি কোনও প্রকার তর্ক উঠলে বাজারে চলতি রবীন্দ্রজীবনী এবং সাহিত্য বিষয়ক কয়েকটা বই ঘাঁটলেই সব সন্দেহের নিরসন সম্ভব।
কমলদা যেমন নিয়ম করে দিয়েছিলেন, ওঁর বাড়িতে কেবল বাচ্চাদেরকেই নয়, অতিথি অভ্যাগতরা এলেও ঠাকুর চাকরেরা পরিবেশন করার সময় পাতের ওপর লুচি দুলিয়ে জিজ্ঞেস করবে “আর একটা দেব কি?” প্রাথমিক অস্বস্তি কাটিয়ে ওঠার পর আমাদের মতো নির্লজ্জ বেহায়া কেউ যদি এ হেন অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন, কমলদার চটজলদি উত্তর, “এটাই ঠাকুরবাড়ির ট্র্যাডিশন। এর মধ্যে যে বাঙালিত্ব লুকিয়ে আছে, যে সংযম-শিক্ষা, যে মানসিক স্থৈর্যের পরীক্ষা, যে আর্য সভ্যতার……” ইত্যাদি ইত্যাদি। এর পর তো আর কিছুই বলার থাকতে পারে না। দুঃখের কথা,রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আম বাঙালির উচ্ছ্বাস থেকে বরাবরই আমাকে একটু দূরে দূরে থাকতে হয়েছে। সব সময় যে পুরো ব্যাপারটা বুঝে পাশ কাটিয়ে গেছি তা নয়, বেশির ভাগ সময়ে উনিই নিরাপদ দুরত্ব বজায় রেখে আমার পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন বললেই বরং নিজের কাছে খানিকটা সৎ থাকা যাবে।
একদম ছেলেবেলায় যে ক’টি কবিতা মুখস্থ করলে বাপ-মায়ের কর্তব্যপরায়ণতা এবং সেই সময়ে তাঁদের সাংস্কৃতিক-মনস্ক-পশ্চিমবঙ্গীয়-বামপন্থী অস্তিত্ব সংকটাপন্ন হত না, এবং ভবিষ্যতে সদর দরজা ঠেলে বাড়িতে ধোপা-নাপিতের আনাগোনার ব্যবস্থাটিও মোটামুটি অক্ষুণ্ণ রাখা যেত, সেই ক’টা কবিতা আমি যতটা সম্ভব মন দিয়ে একপ্রকার মুখস্থ করেছিলাম। ‘একপ্রকার’ বলার কারণ এই যে, অসমবয়স্ক কিছু ব্যক্তির লাগাতার কালচারালি রাবীন্দ্রিক চাপ এবং একটি নেহাতই নবীন কিশোরকে একলা পেয়ে উদ্বুদ্ধ করার নাছোড় গোঁ সত্ত্বেও আমি কোনও দিন স্টেজে ওঠার আগে দাঁতে দাঁতে করতাল বাজিয়ে সর্বাঙ্গে ঠকাঠক কাঁপুনি ধরাকে আটকাতে পারিনি। উত্তেজিত আত্মীয়েরা প্রথমাবস্থায় শারীরিক বেরামটিকে ‘আমলকি বন কাঁপে যেন তার বুক করে দুরু দুরু’ গোছের পোয়েটিক ইন্সপিরেশন, বা সোজা বাংলায় কাব্যিক প্রতিভাসম্পন্ন অপাপবিদ্ধ বালকের ভর হওয়া বলে ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু পঁচিশে বৈশাখের পর বাইশে শ্রাবণেও ফের এক বার যখন ‘হে মোর চিত্ত…’ বলেই আটকে গিয়ে সর্বসমক্ষে কোঁকাতে শুরু করলাম, তখন তারা কেস গোলমেলে বুঝে শেষমেশ সরেই দাঁড়ালেন। সবচাইতে দুঃখ পেয়েছিলেন আবৃত্তি শেখাতে আসা ভদ্রলোক।
এবার জয়দেবের কথা বলি। জয়দেব এক বার রবীন্দ্র সন্ধ্যায় সাঙ্ঘাতিক একটা কারবার করেছিল। ‘দিকে দিকে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে’ দিয়ে কবিতা আবৃত্তি শুরু করে মাঝে,মানে, ‘প্রাসঙ্গিক ফাঁকে’ ও ‘দুর্গম গিরি কান্তার মরু’ ইত্যাদি ঢুকিয়ে এলাকায় হইচই ফেলে দেয়। যা-ই হোক, সেই সময়ে আমাদের পাড়ার লোকাল কমিটির সেক্রেটারির আদি বাড়ি ছিল কিশোরগঞ্জ। ওঁর আত্মীয় এক বাংলাদেশি কবি সেবার রবীন্দ্রজয়ন্তীর সময় উপস্থিত থাকায় তাঁকেই সভাপতি করা হয়। জয়দেবের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের কোনও তুলনা হয় না। দেবতার গ্রাসে ‘কাণ্ডারী বলো’-কে ঢুকিয়ে নিমেষে ‘‘ভাইজান বলো ডুবিছে মানুষ’’ বলায় সবার সে কি হাততালি। জয়দেবের ভাইপোকে চুলদাড়ি লাগিয়ে রবীন্দ্রনাথ সাজিয়ে আনা হয়েছিল ডুবে যাওয়ার আগে ‘মাসি মাসি’ বলে চিৎকার করার জন্য। স্টেজের ওপর সাড়ে তিন ফুট রবীন্দ্রনাথ কচি গলায় ‘মাসি’ আর্তনাদে পাড়া প্রকম্পিত করে তুলছে এমন শিহরন জাগানো দৃশ্য যারা দেখেননি, তাঁদের উদ্দেশে ‘আপনারা রবীন্দ্রনাথকে চিনলেন না’ ছাড়া আমার আর কিছুই বলার নেই।
গোটা পৃথিবী জুড়ে যেখানেই চারটে বাঙালি জুটেছে, সেখানেই ট্রাঙ্ক হটিয়ে, মায়ের শাড়ি, বাবার ধুতি, বউয়ের ওড়না টাঙিয়ে মঞ্চ বেঁধে, বউকে আর মেয়েকে ‘গীতবিতান’-এর সামনে বসিয়ে, গান তুলিয়ে, ছেলেকে দিয়ে ‘বীরপুরুষ’ মুখস্থ করিয়ে রবীন্দ্র-সন্ধ্যার আয়োজন করেছে। বৈশাখের প্রখর রোদ অগ্রাহ্য করে মহিলাদের দেখেছি, ঠোঁটে লিপস্টিক, কচি কলাপাতা রঙের জরি বসানো শাড়িতে শোভিত হয়ে কুচো বাচ্চার গালে ফলস দাড়ি লাগিয়ে রবীন্দ্রনাথ সাজিয়ে ইসকুলে নিয়ে চলেছেন। বাচ্চাটির ফুটপাথে ঠোক্কর খেতে খেতে ‘এই গেল সেই গেল’ অবস্থা, মা-টি বাচ্চার ডানা হেঁচকে তার মধ্যেই টানতে টানতে “কানে তাঁদের গোঁজা জবা ফুল”এর পর কী হল বলে, “ড্যাডি কাল তোমায় যেমন ভাবে বলতে বলেছে, সে ভাবে বলো” বলতে বলতে মেক-আপ গলে যাওয়া মিসেস দাশগুপ্তর ছেলেকে টপকে কী ভাবে তার কচিটি বাংলার সাংস্কৃতিক আকাশে ধূমকেতুর ন্যায় উদিত হয়ে বাকিদের ভাত মেরে দেবে, সেই চিন্তায় আকুল হয়ে ছুটে চলেছেন। মা-টির কানে জবা ফুল গুঁজে তেপান্তরে ছেড়ে দিলে বাংলার উন্নতি ত্বরান্বিত হত সন্দেহ নেই।
রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আমাদের উচ্ছ্বাসের অনেকটাই ওনার লেখা না পড়ে বছরে এক বার পুজো-প্যান্ডেলে কেবলমাত্র হেমন্ত মুখোপাধ্যায় আর কিশোরকুমারের গলায় তাঁর গান শোনা, এবং একটা বয়সের পরে অফিসের ব্যাগ বগলদাবা করে শেয়ালদা স্টেশনে দাঁড়িয়ে উনি ‘মহেশ’ নামক ছোট গল্পটি লিখেছিলেন না ‘ছুটি’, এই তর্কের একজিস্টেনশিয়াল মীমাংসায় সীমাবদ্ধ। আমাদের পাড়ার ইসকুলের হেডমাস্টারমশাই বিনয়বাবু নিজে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে একটা চটি বই ছাপিয়ে বের করেছিলেন। আবার বলি, সামান্য মাইনের চাকরিতে সংসার চালিয়ে, বড় ছেলের নাম রথীন্দ্রনাথ, ছোট ছেলের নাম সমীকেন্দ্রনাথ রেখে বাড়িতে কাকিমাকে সারা জীবন ঘটিহাতা ব্লাউজ পরিয়ে অকল্পনীয় কৃচ্ছ্রসাধনের পরেও এমন উৎসাহ দেখে ‘কেয়াবাত’ না বলে উপায় নেই। তবুও উনি আবেগমথিত কণ্ঠে যখনই “তোমরা ভেবে দেখো, উনি কত বড় মাপের মানুষ ছিলেন, যে সময় ইলেকট্রিসিটি ছিল না, বাস-ট্রাম ছিল না, সে যুগেও উনি কিন্তু নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন” বলে হাল্কা ঠোঁট কাঁপিয়ে মাটির দিকে চেয়ে চশমার কাচ মুছতেন, আমাদের কেমন একটা খটকা লাগত।
আমাদের ক্লাসের সুমন্ত্র বরাবরের চুপচাপ ভাল মানুষ কারও সাতে-পাঁচে না থাকা বেচারা মার্কা ছেলে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুররা তো জমিদারির পয়সায় বড়লোক ছিলেনই, কিন্তু ওঁদের এত কাঁচা পয়সার আসল সোর্স যে মিষ্টি বিক্রি করে, সেটা কি জানতেন? রবীন্দ্রনাথের বাবার নাম ছিল দ্বারিকানাথ ঠাকুর, ওই নামেই দ্বারিকের মিষ্টির দোকান বড় রাস্তার ওপর এবং সারা দিন বিক্রি দেখলে মাথা ঘুরে যাবে ইত্যাদি ঐতিহাসিক কারণ ছাড়াও সামাজিক কারণেই গুরুত্বপূর্ণ এই তথ্য আমরা সুমন্ত্রর লেখা থেকেই প্রথম জানতে পারি। আপনারা ভাবছেন ফের সস্তা রসিকতায় বাজার মাত করার চেষ্টা করছি তা করছি সন্দেহ নেই, তবে এতেও সন্দেহ নেই যে, গত বেশ কিছু দশক আমাদের নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ এই যে এত পপুলার কবি হয়ে উঠেছেন, তার ভিত্তি এই ধরনের কয়েকটি পাথ-ব্রেকিং ইনফরমেশন। রবীন্দ্রনাথ প্রায় একা হাতে আমাদের জীবন, সাহিত্য, ছবি দেখার চোখ, রাজনীতি, স্বদেশ ও জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি বিষয়গুলোর সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ফান্ডামেন্টাল প্রেমাইসগুলোকে যেমন উল্টে পাল্টে দিয়েছিলেন, তেমনই আবার আমরা ‘সে যুগেও নোবেল’ পাওয়ার মতো অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা বা দ্বারিকের সন্দেশ ব্যবসার সঙ্গে ওঁদের পৈতৃক যোগাযোগ স্থাপিত করে ওঁকে সমকালের প্রয়োজন অনুযায়ী ছাঁচে ফেলে গড়েপিটে নিয়েছি।এই ভাবেই নানা রঙের রবীন্দ্রনাথ আমাদের মধ্যে বেঁচে রয়েছেন।
Advertisement