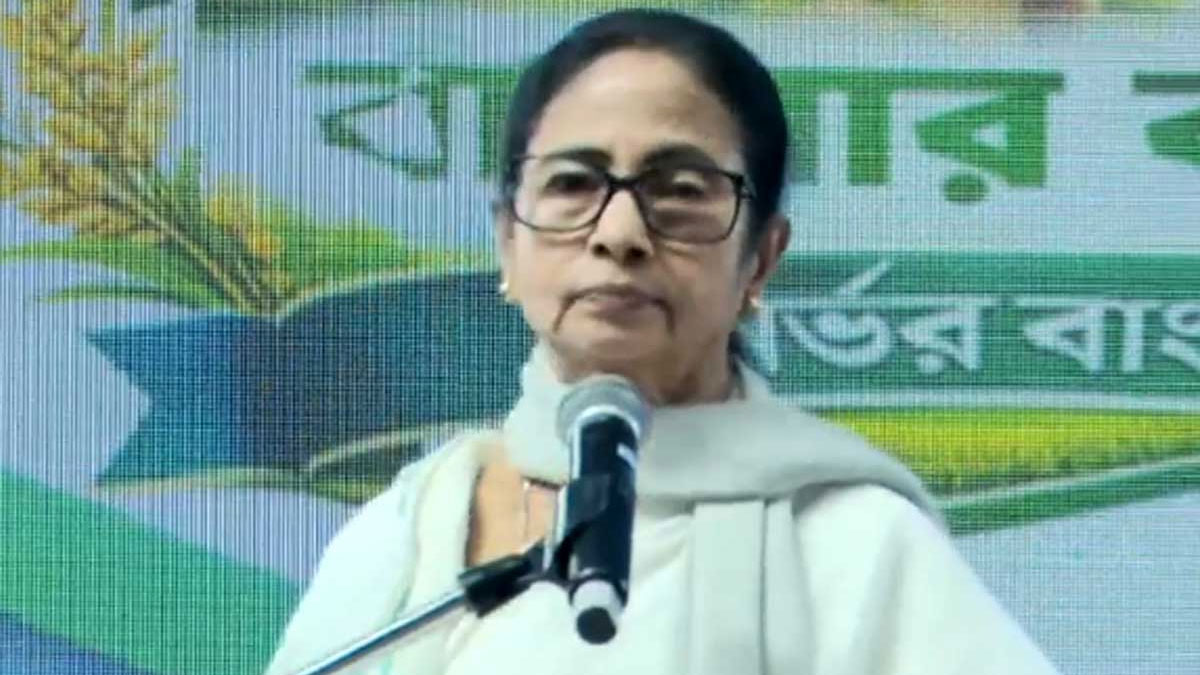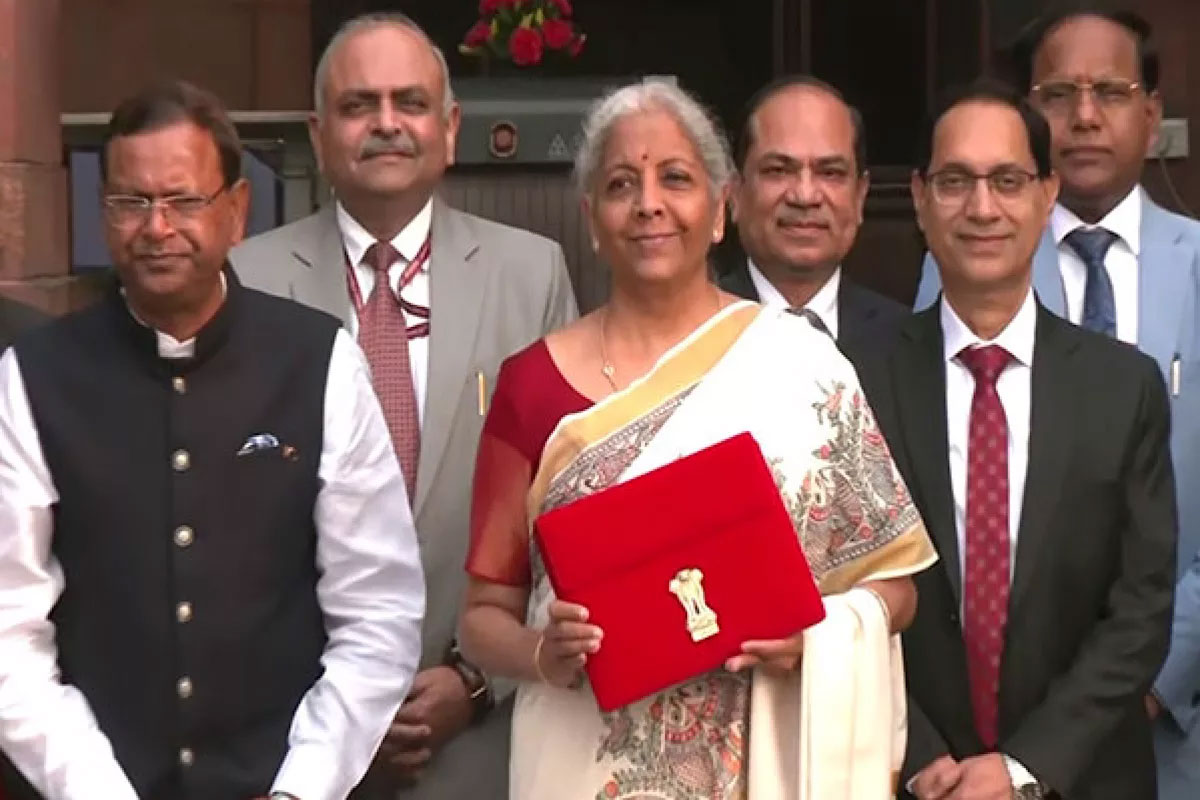‘আমি শিশুদের মুখের দিকে তাকাই, আর ভাবিঃ / এই কদর্য, কুৎসিত পৃথিবীতে / এত নিষ্পাপ সারল্য নিয়ে / কীভাবে জন্মায় এই শিশুরা? / তখন আমার সেই লোকপ্রবাদটা মনে পড়েঃ / ‘পাঁকেই তো পদ্মফুল ফোটে।’ — হিমাংশু পাল
এক অখ্যাত লেখকের কাব্যকথা। সবার নজরে আসার মতো নয়। কিন্তু যদি দৈবাৎ কারও নজরে এসে থাকে তো মনে হবে আপনার-আমার সবারই মনের কথা বলেছেন ওই অনাখ্যাত লেখক। যদি আমাদের সেই অনুভবী মনটা আদৌ থেকে থাকে। কারণ আজকের বিশ্বায়ন-বেষ্টিত পণ্যায়নের যুগে আমাদের ‘অনুভব’-এর ব্যাপারটাই উধাও হয়ে গেছে। বিশেষ করে সমাজ-সংসারের সিংহভাগ শিক্ষিত মানুষের ক্ষেত্রে। অন্যদের ক্ষেত্রে নিষ্ঠুর হলেও নিজেদের ক্ষেত্রে অনুভবী মন অবশ্য ষোলআনাই অটুট আছে।
Advertisement
আজ আর অস্বীকার করে লাভ নেই, মানুষ এখন অনেকটা যন্ত্র হয়ে উঠেছে। আসলে যন্ত্রশাসিত সমাজে অধিকাংশ মানুষই ধীরে ধীরে তাদের অন্তর্গত আবেগ আর হৃদয়ের স্পন্দনকে অনেকটাই ‘নিয়ন্ত্রণ’-এ এনে ফেলেছে। স্বাভাবিক বোধ ও বোধি তাদের মধ্যে বিশেষ কাজ করেন। এটা প্রযুক্তি অধ্যুষিত সময়ে যন্ত্রের সঙ্গে রাতদিন নিরবচ্ছিন্ন সহবাস করার জন্যে, নাকি ভোগবাদি তথ্য পণ্যায়িত সমাজে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার তাগিদ— তা নিয়ে আমাদের মধ্যে অবশ্য কিছুটা সংশয় জাগে বৈকি।
Advertisement
যে কোনও সম্প্রদায়েরই একজন মানুষ, যিনি ফুল দেখে, শিশু দেখে, শৈল্পিক কাজ দেখে, প্রাকৃতিক বৈভব বৈচিত্র্য দেখে আমোদিত হবেন, আহ্লাদিত হবেন, বিমোহিত হবেন— এটাই তো তার মনুষ্য চরিত্রের স্বাভাবিক দিক হওয়া উচিত। এর ব্যতিক্রম হলেই বরং আমাদের চিন্তার বিষয়। কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই, আজকের যান্ত্রিক যুগের সিংহভাগ মানুষই এই সুস্থ ও স্বাভাবিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই যেন ক্রমশঃ হারিয়ে ফেলছেন। কেন এই অস্বাভাবিক পরিবর্তন— তা নিয়ে সমাজবিজ্ঞানীরা ভাববেন নিশ্চিত।
শুধু সমাজবিজ্ঞানীরা কেন, ভাববেন মনোবিজ্ঞানীরাও। কারণ সুস্থ ও স্বাভাবিক সমাজ-জীবনের জন্য এগুলো ভীষণভাবেই প্রয়োজন। আজকের পণ্যায়িত জীবনে তথা ভোগবাদী সমাজে সুস্থতার বাতাবরণটিই যেন ভেঙে একেবারে তছনছ হয়ে যাচ্ছে। এই ‘সভ্য সমাজ’-এর মানুষ ক্রমশঃই বড় বেশি আগ্রাসী হয়ে উঠছেন। ‘আমি’ ও ‘আমার’ ছাড়া কোনওকিছু ভাবতে নারাজ। সমাজের প্রয়োজনেই যে অন্যদের কথাও তাকে ভাবতে হবে— এই সহজ স্বাভাবিক বোধটাই তার মধ্য থেকে ক্রমশঃ উবে গেছে।
‘এ বড়ো সুখের সময় নয়।’ এক গভীর অসুখ বাসা বেঁধেছে আমাদের মধ্যে। এই ‘গভীর অসুখ’ থেকে মুক্তি না পেলে গোটা মনুষ্য প্রজাতিরই ভয়ানক ক্ষতি হয়ে যাবে, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু আমরা তা বুঝছি কোথায়? প্রবহমান গড্ডালিকায় গা ভাসিয়ে চলেছি সবাই। আহার-নিদ্রা-মৈথুন তো বিশ্বের সব প্রাণীজগতের মধ্যেই আছে। মানুষ আর পশুতে তাহলে প্রভেদ কোথায়? মনুষ্য চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেললে মানুষ আর মানুষ থাকে না। অর্থাৎ জীবজন্তুর সঙ্গে কোনও ফারাক থাকে না।
প্রিয়পাঠক হয়তো ভাবছেন, ধান ভানতে শিবের গাজন কেন? নিবন্ধের শিরোনাম থেকে দূরে সরে যাওয়া হচ্ছে না তো? না পাঠক, শিবের গাজন এজন্যই যে, তথাকথিত ‘স্বাধীনতা’র পঁচাত্তর বছর পেরিয়েও এদেশের সিংহভাগ শিশুরা এক অনিশ্চিত বর্তমান ও ভবি,্যতের সন্ধিক্ষণে ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। ‘আজাদি’র অমৃত মহোৎসবের ছিটেফোঁটাও তাদের দিকে ছিটকে পড়েনি। যাদের ঘিরে আমরা ভবিষ্যতের রঙিন স্বপ্ন দেখি, তাদের এই বিপন্নতা আমাদেরকে কোনওভাবেই কেন যে স্পর্শ করে না?
অথচ কতো না ঘটা করে প্রতিবছর শিশুদিবস উদযাপিত হয়। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর জন্মদিনটিকে বিশেষ মর্যাদা দিতে নিষ্পাপ শিশুদেরই বেছে নেওয়া হয়েছিল। আমাদের রাজনৈতিক অভিভাবকরা, বিশিষ্টজনরা ওইদিন সেজেগুজে মঞ্চ কাঁপিয়ে কত ভালো ভালো কথাই না বলেন। বৈদ্যুতিন মাধ্যমের আসরে কতশতো মহতি পরিকল্পনার কথাই না তাদের শ্রীমুখ থেকে উচ্চারিত হয়। সেসব দেখে-শুনে তাৎক্ষণিক বিহ্বলতায় বিহ্বল হয়ে উঠি আমরা অনেকেই।
কিন্তু সেই তাৎক্ষণিক বিহ্বলতা কাটতে তেমন সময়ও লাগে না আমাদের। ২৪ ঘণ্টা পেরোতেই আমরা বাসি কাপড়ের মতোই ত্যাগ বা পরিবর্তন করি তা। আর রাত পেরোতেই পিছনে ফেলে আসি শিশুস্বার্থ সম্পর্কিত ওইসব গালভরা কথা আর পরিকল্পনার যাবতীয় ফুলঝুরি। ত্যাগবস্ত্রের বিপণি ভরে ওঠে আমাদেরই দ্বিচারি আচরণে। আলো-আঁধারিতে ভরা বিস্তীর্ণ বস্তি, খালপাড়ের সারিবদ্ধ ঝুপড়ি আর শহর ও শহরতলির ফুটপাতের শিশুরাই শুধু নয়, প্রত্যন্ত অভাবী অঞ্চলের শিশুরাও বুঝি মুচকি হাসে।
কেন মুচকি হাসে? কারণ পরিকল্পনা বা প্রতিশ্রুতির কোনও বাস্তবায়ন ঘটে না তাদের জীবনে। তারা যে তিমিরে, সেই তিমিরেই থেকে যায়। আলোর পথে পা রাখার সামর্থ্য হয় না। তাদের ঘিরে থাকা ঘন কালো অন্ধকার ঠেলে সামান্য আলোর রেখাটুকুও দেখা যায় না। প্রায় দেড়শো কোটির এদেশে বিচ্ছিন্নভাবে কাজ-করা দু-চারটে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বা এনজিও-র সাধ্য কি দেশের সিংহভাগ শিশুদের সেই ঘন অন্ধকার থেকে টেনে তোলার। বিদ্যুৎ চমকের মতো মনে হয় শিশু-কল্যাণে তাদের মানবিক কাজকর্ম।
কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য আর নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীরা বার বার পঠিত হন বিভিন্ন সভা-অনুষ্ঠানে। তাঁদের অর্থাৎ বাচিকশিল্পীদের সুচারু পরিবেশনে হয়তো অনেক হাততালিও পড়ে। যাঁরা শোনেন, তাঁদের মুখে ওই সময়টুকুর জন্যেই মুগ্ধতার আবেশ ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু ব্যস, ওই পর্যন্তই। যাঁরা মঞ্চ ছেড়ে যান কিংবা যারা দর্শকাসন ছেড়ে গৃহ অভিমুখে পড়ি দেন, তাদের কারও মনেই কোনও দাগই কাটে না সদ্য-শোনা ওই হৃদয়-নিংড়ানো কাব্যকথা। যদি সামান্যতমও দাগ কাটতো, তাহলে কিছুটা কাজ হতো।
আপনি স্বীকার করুন আর নাই করুন, এটাই আসলে আজকের বাস্তব। এটাই কঠোর ও কঠিন সত্য। এটাই আমাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অন্যতম দিক। সস্তা আবেগ ছেড়ে একবার সত্যি করে বলুন তো, একে কোনওভাবেই অস্বীকার করা যায় কি? পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর জন্মদিনে এদেশের বঞ্চিত শিশুদের নিয়ে এই নির্মম আচরণ আমাদের সামান্যতম ব্যথিত করে না। শিশুদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে ন্যূনতম সতর্ক ও সচেতনও করেন। স্বাধীনতার পর এভাবেই কেটে গেল দীর্ঘ পঁচাত্তরটি বছর।
তবুও শিশুদের বাসযোগ্য ভূমি আজও তৈরি করা সম্ভব হল না এদেশে। অথচ প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে ঝাঁ-চকচকে বাড়িঘর উঠল। দেশের সর্বত্র অত্যাধুনিক ভবন মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছে। ঐতিহ্যবাহী সাবেকি সংসদভবন ভেঙে আরও ঝাঁ চকচকে নতুন সংসদভবন নির্মিত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন ও তাঁর কার্যালয়ও ভেঙে নতুন করে নির্মিত হচ্ছে। ঐশ্বর্যের আবহে চারদিক ম-ম করছে। ভারতের মতো ক্ষুধা-বঞ্চনা কবলিত দেশে এর চেয়ে নিষ্ঠুর পরিহাসের আর কী আছে? একবারও ভেবে দেখেছি কি?
ভাবুন তো, দলমত নির্বিশেষে দেশ শাসনের নামে সরকার বাহাদুরগণ কী করছেন? শুধু একতরফা ভাবে দিল্লিকে দোষ দিয়ে তো লাভ নেই। দলীয় রাজনীতি দূরে সরিয়ে একবার নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তাকান রাজ্যগুলির দিকে। কী দেখবেন? রাজনীতির নামে স্রেফ দল করছেন শাসকরা। অপেক্ষমান শাসকরাও একই পথের পথিক। ফারাকটা মাত্র উনিশ-বিশ। দলের বাইরে তাদের চিন্তাভাবনা বিস্তার লাভ করে না। ফলে দেশের আপামর মানুষের সামগ্রিক উন্নয়ন ঘটে না। ‘খড়্গ হাতে’ উন্নয়ন আটকে থাকে রাস্তায়।
দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাদের কতই না বড়াই। কিন্তু যারা প্রকৃত অর্থেই ‘দেশের ভবিষ্যৎ’ তাদের সম্বন্ধে সরকার বাহাদুর তো বটেই, আমরা— সহনাগরিকরাও কেমন যেন উদাসীন। সরকারের কাঁধে সব দায়ভার চাপিয়ে দিয়ে আমরা নির্লিপ্ত আর নির্বিকার থাকাটাই পছন্দ করি। কেন্দ্র কিংবা রাজ্য— সব স্তরেই সরকারেরই দায়-দায়িত্ব তো আছেই এবং তারা সে দায়ভার বহনেও দারুণভাবেই ব্যর্থ। কিন্তু একজন সহ-নাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু দায়দায়িত্ব আছে একথা ভুলে গেলেই বা চলবে কেন? কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে তাদের শিশু-কল্যাণে সাংবিধানিক দায়দায়িত্ব পালনে বাধ্য করা, শিশু-কল্যাণে কাজ করা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (এনজিও)-র পাশে সক্রিয়ভাবে দাঁড়ানো, সাধ্যমতো ব্যক্তিগত স্তরে প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া হলে শিশু-কল্যাণের কাজে কিছুটা অগ্রগতি হতেই পারে। কিন্তু আমাদের মধ্যে তেমন তাড়না বা তাগিদ কোথায়? কেবল নিজের শিশুটিকে নিয়েই আমাদের যাবতীয় চিন্তাভাবনা। পাশের বঞ্চিত শিশুটির কথা একবারও আমাদের ‘প্রগতিশীল’ মাথায় আসে না।
যাঁরা সমাজের সচ্ছল (ধনী ও উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের) মানুষ, তাঁরা আর্থিকভাবে পারেন। অভাবী শিশুদের তাঁরা আর্থিক দিক থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সহযোগিতা করতে পারেন। অন্যদিকে যাঁরা আর্থিকভাবে পারেন না, কিন্তু অন্যভাবে পারেন, তাঁরা অন্ততঃ শিক্ষা-সংস্কৃতির দিক থেকেও তো শিশু-কল্যাণের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে সহায়ক ভূমিকা নিতে পারেন। এদেশের কমপক্ষে দশ শতাংশ নাগরিকের তেমন আর্থিক সঙ্গতি বা ক্ষমতা আছে, একথা বলাই বাহুল্য। নেই কেবল মানসিক ক্ষমতা বা সঙ্গতি।
সাধক-কবি রামপ্রসাদ সেনের বহুশ্রুত গানের কলি একটু বদলে বলা যেতেই পারে— ‘এমন শিশু (মানব) জমিন রইলো পতিত / আবাদ করলে ফলত সোনা / মন রে কৃষি কাজ জানো না…।’ দেশজুড়ে শিশুসম্পদের এমন নির্বিকল্প অপচয় দেখেও আমাদের মনে কোনও রকম অস্বস্তি বা ব্যথাবোধ হয় না। আমাদের মনুষ্যত্ব ও মানবিকতাবোধ কোথায় বন্ধক রেখেছি, তা ভাবলে বেশ অবাকই লাগে। বিস্ময় জাগে। ‘ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে’— এই শিশুদের জন্য একবারেও কি আমাদের মন কাঁদবে না?
আশপাশের বঞ্চিত শিশুদের মুখের দিকে আমাদের তাকাতে হবে। আর ভাবতে হবে— এই কদর্য, কুৎসিত পৃথিবীতে / এত নিষ্পাপ সারল্য নিয়ে / কীভাবে জন্মায় এই শিশুরা?’ শুধু লোকপ্রবাদ স্মরণে এনে নিজেদের দায়িত্ব এড়ানো যাবে না। কিংবা ‘পাঁকেই তো পদ্মফুল ফোটে’ বলে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াও যাবে না। মনুষ্যত্ব ও মানবিকতা বোধকে জাগিয়ে তুলতে হবে নিজেদের মধ্যে। মুখের কথায় নয়, কাজের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করতে ‘আমরাও মানুষ’ আর মানুষ হয়ে মানুষের যথার্থ কর্তব্যই বা ভুলি কী করে?
Advertisement