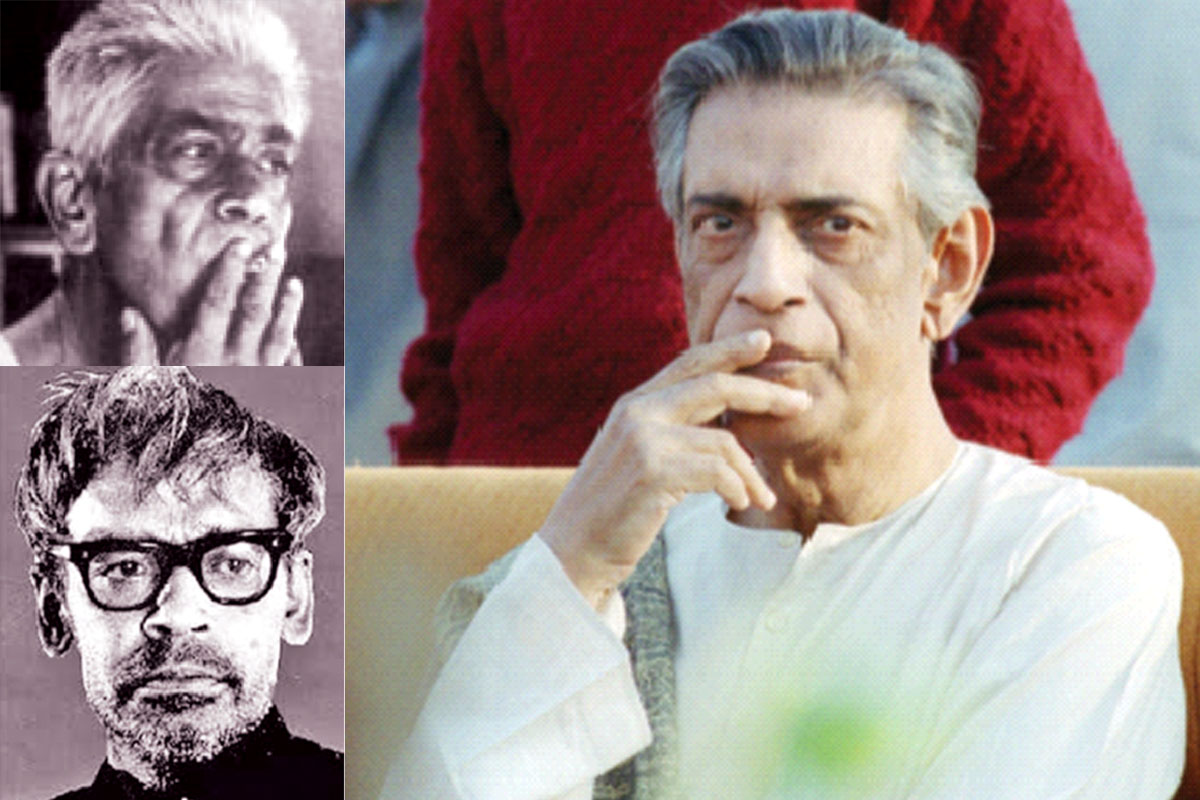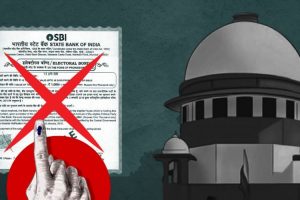সুব্রত রায়
বারীন সাহার কথা আমার শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের মুখে অনেকবার শুনেছি। নিমাই ঘোষ, ঋত্বিক ঘটক ও বারীন সাহা— এই তিনজন চলচ্চিত্রকারকে নিয়ে একটা আলাদা উত্তেজনা ছিল আমাদের মধ্যে যখন আমার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের চলচ্চিত্রবিদ্যা বিভাগের ছাত্র। সত্যজিৎ রায় ও মৃণাল সেন ছিলেন দুই প্রধান সেনাপতির মতো, যাঁরা বাংলা অন্যধারার চলচ্চিত্রকে দেশে বিদেশ নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের ছবি যেন আমাদের সরকারি চাকরিনির্ভর মধ্যবিত্ত নিরাপত্তার বাইরে বেঁচে থাকার ছাড়পত্র। একটা সময় বাংলা সিনেমা, শিল্পের আঙিনায় প্রবেশ করার একটা প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে রণে ভঙ্গ দেবে। ঢুকে পড়বে বাণিজ্য ও শিল্পের মেলবন্ধনের এক ইউটোপিয়ায়। যেখানে দাঁড়িয়ে আশা করা হবে সিনেমার বিনোদনমূল্য ও শিল্পমূল্য— দুই দিকেই ডানা মেলে সিনেমাপ্রেমী ও প্রযোজকদের আনন্দ দেবে। মানে সাপ মরবে কিন্তু লাঠি ভাঙবে না।
এই হাতিমির দশা লাগার আগে যাঁরা তখনও সিনেমাকে এক শিল্পমাধ্যম ভেবে ছবি করার চেষ্টা করছিলেন তাঁদের মধ্যে ঋত্বিক ছিলেন সবার আগে। আর ছিলেন নিমাই ঘোষ ও বারীন সাহা। বারীন সাহা ‘তেরো নদীর পারে’র (১৯৬১) মতো এক অনবদ্য ছবি বানিয়ে, স্বেচ্ছায় মেদিনীপুরের এক অজ গ্রামে বসে গ্রামের মানুষদের শিক্ষাদানে ব্রতী হন। ব্যাপারটা ঠিক বোঝা যেত না। আজ বুঝতে পারি বারীন সাহার হতাশা আর যন্ত্রণাকে। অন্যধারার চলচ্চিত্রকারদের সেই যন্ত্রণার রূপ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে।
যে কোনো আর্টই একধরনের বিনোদন। রামায়ণও এক ধরনের বিনোদন। রামচরিত মানস ভারতে সব থেকে বেশি সুরেলা ছন্দে গাওয়া হয়েছে। এই যে বিনোদনের মধ্যে দর্শককে অবাক করে দেওয়ার চেষ্টা থাকে, তা ‘তেরো নদীর পারে’ ছবিটির মধ্যেও ছিল। একটা গরিব সার্কাস, যারা বিশেষ কিছু পারে না, সেই সার্কাসে একটা মেয়ে এল। একটা শহুরে মেয়ে যে আলাদা করে দ্রষ্টব্য হয়ে উঠলো। ফলে যারা পুরোনো তারা ভাবলো আমার একটা প্রতিদ্বন্দ্বী এসে গেছে। তারা ভাবতে শুরু করলো যে, আমাদের তো কেউ দেখবে না। এই যে শিল্পীর সংকট তৈরি হলো। একটা ট্রাডিশনাল ধারণার মধ্যে আর্টিজানের থেকে যন্ত্রনির্ভর শিল্প অধিক পরিচিতি পাচ্ছে। নর্তকীর এই যে আসা, যা দীর্ঘক্ষণ জিপ প্যান করে দেখানো হয়েছে তা আসলে শিল্পের ইতিহাসকে ধরার চেষ্টা। গ্রামীণ যাত্রাপালা বা সার্কাস তার মধ্যে শহুরে ভাবমূর্তি ঢুকে গেল। নারীকে যৌন উৎকোচ হিসাবে তুলে ধরা হলো। আর সেটাই হলো শহুরে বিনোদন। সে শিল্পী নয়, অভিনেত্রী নয়, মানুষ নয়, সে হয়ে উঠল যৌন উৎকোচ। এটাই শিল্প, বিনোদন ও আত্মার জিজ্ঞাসার মাঝে শিল্পী কোথায় আছে এই প্রশ্নটা তুলে দিল।
এখানে ‘তেরো নদীর পারে’ মানে পাল্টে যাওয়া সভ্যতা ও বিনোদনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে তাকে কী কী করতে হবে সেটা সে জানে না। তার এই দ্বন্দ্ব, দ্বিধা ও চিন্তা এটাই ‘তেরো নদীর পারে’। ‘তেরো নদীর পারে’ মানে এমন পরপার যা আমরা জানি না, কিন্তু আছে, এটা অনুভব করতে পারি। পারফর্মিং আর্টের মধ্যে এমন সংকট তৈরি করে যার সঙ্গে ইংগমার বার্গম্যানের shaw Dust, Tinsel ও Fredriko Fellini-র la strada একটা খ্রিস্টান ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মধ্যে নারীকে বিনোদন হিসাবে তুলে ধরা।
গুরু দত্ত, ঋত্বিক ঘটক ও বারীন সাহা বস্তুত তিনজন মানুষই যেটা করেছেন— এঁদের জীবনের মূল সমস্যা হলো কমার্শিয়াল ওয়ার্ল্ডের টাকার ঝনঝনাতের মধ্যে কীভাবে শিল্পকে খুঁজে পাওয়া যাবে। লক্ষ্মী আর সরস্বতী এক সঙ্গে থাকতে পারে কি না, এটা বুঝতে গিয়ে জীবন বুঝতে গিয়ে ওরা তিনজনই ব্যর্থ হয়েছেন। বারীন সাহা অভিমান করে বহু দূরত্বের জীবন বেছে নিয়েছেন। এও এক ঐতিহাসিক সমাপতন যে, এই তিনজনই ১৯২৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন, যে বছর তৈরি হয়েছিল ‘যুদ্ধজাহাজ পটেমকিনের’ মতো অন্যতম সেরা পরীক্ষামূলক চলচ্চিত্র।
যে দমবন্ধকর পরিবেশ ও পরিস্থিতি নিয়ে আজকের অন্য ধারার চলচ্চিত্রকাররা বিক্ষুব্ধ বোধ করেন তার অশনিসংকেত কিন্তু বারীনবাবু অনেক আগেই পেয়েছিলেন। ঋত্বিক ঘটক তা বুঝলেও ময়দান ছেড়ে যেতে রাজি ছিলেন না। তাই তিনি গোটা আটেক কাহিনীচিত্র, এগারোটা ছোটো ছবি আর পাঁচটা শেষ না করতে পারার ভাণ্ডার রেখে গেছেন আমাদের জন্য। আর বারীন সাহা রেখে গেছেন একটি কাহিনীচিত্র, তাও যেটা দৈর্ঘ্যে প্রচলিত কাহিনী চিত্রের মাপের অনেক ছোটো। আর তিনটে ছোট ছবি। এই নিয়ে কেউ যে অমরত্ব লাভ করবে এমন আশা নিতান্তই দুরাশা কিন্তু কী অবাক করা কাণ্ড, বারীন সাহাকে বিস্মৃতির অতলে ঠেলে দেওয়ার সবরকম প্রক্রিয়া তাঁর জীবিতকালে ও পরবর্তীকালে জারি থাকলেও মানুষটাকে একেবারে পগার পার করে দেওয়া যায়নি নানা কারণে। পরের প্রজন্মের অন্য ধারার চলচ্চিত্রপ্রেমীদের স্মৃতিতে তিনি বারে বারেই ফিরে ফিরে আসেন।
ঋত্বিক ঘটককে তাঁর জীবৎকালে নানা অপমান, লাঞ্ছনা দিয়েও আজকের বিশ্বায়নের বাজারে তাঁর ছবির সেলভ্যালু তৈরি করে নিয়ে ঝাঁ-চকচকে মাল্টিপ্লেক্সের দোকান ঘরে ঠাঁই দিয়েছে। তাঁকে নিয়ে আলাপ আলোচনা কিংবা উৎসব আয়োজনে পয়সা ঢালতেও রাজি থাকেন কোনো বাণিজ্যিক সংস্থা। কিন্তু বারীন সাহার ছবির ডিভিডি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। ভরসা সেই প্রান্তিক চলচ্চিত্রপ্রেমীদের দল।
বারীন সাহার মতো একজন পণ্ডিত চলচ্চিত্রকার বাংলা চলচ্চিত্র জগতে খুব কম দেখা গিয়েছে। তিনি ভালো ক্যামেরাম্যানও ছিলেন। বারীনবাবুর জন্ম ১৯২৫ সালে। প্রথাগত শিক্ষা শেষ করে তিনি অভিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। রাজনৈতিক কারণে তাঁকে জেলেও যেতে হয়েছিল। ১৯৫২ সালে বারীন সাহা জেল থেকে বেরিয়ে বিদেশে পাড়ি দেন। ফ্রান্সের বিখ্যাত চলচ্চিত্র বিদ্যালয় থেকে চলচ্চিত্র পরিচালনা ও সম্পাদনা নিয়ে স্নাতক হন। পরে ইতালির Centro sperimentale the Cinematographia থেকে চিত্রগ্রহণ বিষয়ে স্নাতক হন। ফলে সে যুগের ফ্রান্সের ‘নিউ ওয়েভ’, ইতালির ‘নিওরিয়ালিজম’ চলচ্চিত্র আন্দোলনের মধ্যেই তিনি নিজেকে গড়ে তোলার সুযোগ পেয়েছিলেন বলা যায়। এর তিন বছর পর তিনি দেশে ফিরে মেদিনীপুরের ‘তেরো নদীর পারে’ তিনি তাঁর জীবনের প্রথম ও একমাত্র পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবির কাজ শুরু করেন নিজের পকেটের টাকা খরচ করে। ‘তেরো নদীর পারে’ যখন তিনি তৈরি করছেন তখন সত্যজিৎ রায় তৈরি করছেন ‘অপুর সংসার’, মৃণাল সেন তৈরি করছেন ‘বাইশে শ্রাবণ’ আর ঋত্বিক ঘটক ব্যস্ত রয়েছেন ‘মেঘে ঢাকা তারা’র কাজে। বাংলা অন্যধারার সিনেমার স্বর্ণযুগের সূচনা হচ্ছে।
‘তেরো নদীর পারে’ প্রথম একটি বাংলা ছবি যা সম্পূর্ণভাবে আউটডোরে শুটিং হয়েছিল। সেই আউটডোরের লোকেশন ছিল মহিষাদল পার হয়ে হলদি নদীর ধারে ‘তেরো পাখিয়া’ নামের একটি গঞ্জ। এককালে আজকের হলদি নদীকেই তেরো নদী বলা হত। মহিষাদলের রাজা তেরোজন পাইক পাঠিয়ে এই গঞ্জ দখল করেছিল বলে নাম হয়েছিল তেরো পাখিয়া সেখানে সিনেমা বানানোর যাবতীয় সরঞ্জাম নিয়ে পৌঁছনো সহজ কাজ ছিল না। তা এতটাই দুর্গম ও বসবাসের অযোগ্য ছিল যে কলকাতার অভিনেতারা সেখান গিয়ে থাকতে রাজি হননি। ফলে শুটিং শুরু হলে বারীন সাহাকে বারেবারেই অভিনেতা বদল করতে হয় তিনি স্থানীয় লোকজনকে নানা চরিত্রে অভিনয় করিয়েছিলেন। এসবই তিনি করেছিলেন নিজের বিশেষ এক চলচ্চিত্র ভাবনার জায়গা থেকে, যার ভিত্তি ছিল আন্দ্রে বাজার ‘ইমপিওর সিনেমা’ তত্ত্ব।
‘তেরো নদীর পারে’ ছবিটি মুক্তি পায় ১৯৬১ সালে। এই ছবি গল্পআশ্রিত চলচ্চিত্র নয়, কাহিনী এখানে গৌণ। যেটুকু আছে তাও যেন গল্প অনুসরণের সাহায্যার্থে দর্শকের কাছে সূত্র হিসাবে পরিবেশিত। তাই নির্মল ঘোষের যে কাহিনী অবলম্বনে ‘তেরো নদীর পারে’ তাতে নিটোল গল্পের সম্ভাবনা থাকলেও পরিচালক তাঁর ছবিতে পরম্পরাগত মোটা দাগের গল্প এড়িয়ে ৬/৯ গেছেন। নাটকের যথেষ্ট উপাদান থাকা সত্ত্বেও, অতিনাটকীয়তা তো নেইই, নাটকীয়তারও সাহায্য নেননি। পক্ষান্তরে এই ছবিতে অমসৃণ জীবন ভগ্নাংশের ইঙ্গিতময় কিছু খণ্ডচিত্রের মাধ্যমে শিল্পজিজ্ঞাসা ও জীবন প্রসঙ্গে তাঁর অনুভব তুলে ধরতে চেয়েছেন। তাই ছবিতে শিল্পের উদ্দেশ্যঘটিত অপাতপ্রত্যক্ষ প্রশ্নটিই সব নয়। আরও গভীরে জীবন প্রসঙ্গে আর এক অন্তর্মুখ বিমূর্ত প্রশ্নও এ ছবির অন্তরাত্মা, যে প্রশ্ন জীবনের চাওয়া ও পাওয়ার এক বিমূর্ত প্রশ্ন। ছবিটিতে যে মূল চরিত্রটিকে অবলম্বন করে এই জিজ্ঞাসা উপস্থাপিত সে একজন অতি সাধারণ ভ্রাম্যমাণ সার্কাস খেলোয়াড়— ওস্তাদ। এই ওস্তাদের চরিত্র চিত্রণে বারীন সাহা অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।
ছবির প্রথম পর্বে প্রতিদ্বন্দ্বী সার্কাস দলের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার জন্য ম্যানেজারের নর্তকী আনার প্রস্তাবের মুখে ওস্তাদ নির্মম ও কঠোর। কিন্তু পরে সহকর্মীদের কষ্টের কথা ভেবে সে সম্মতি দেয়। সার্কাসে নর্তকীর আবির্ভাব ওস্তাদের পরাজয় বহন করে আনে। কিন্তু ওস্তাদের আচরণে নর্তকীর প্রতি কোনো ঈর্ষা বা বিরূপতা প্রকাশ পায় না। আত্মঘাতী গ্লানিতে অপ্রকৃতিস্থ অসহায় এক দুঃসাহসী খেলায় মাতে সে এবং একটা দুর্ঘটনায় পতিত হয়। নর্তকী তাকে শুধু সুস্থই করে তোলে না, ভালোবাসার ছোঁয়ায় ওস্তাদের ভেতরে নতুন করে জীবন বিশ্বাস ফিরিয়ে আনে। এই নতুন জীবনকে ওস্তাদ তাই সানন্দে বরণ করে নেয়। কিন্তু বাদ সাধে ম্যানেজার। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে সে ওস্তাদকে আক্রমণ করে বসে। অবশ্য পরাজিত হয়। ম্যানেজার সার্কাস ছেড়ে চলে যায়। নর্তকীও তার কাছে বিদায় নিতে আসে। জীবনের এক অমোঘ ভবিতব্যের মতোই সে এই বিচ্ছেদকে মেনে নেয় ওস্তাদ। এক স্থিতধী, মগ্ন শিল্পীর মতোই সে আবার সার্কাসে ফিরে আসে তার নিজস্ব শিল্পাশ্রয়ে, যেখানে প্রেমের চেয়েও বড় তার শিল্প।
Advertisement
মাঝে মাঝে ওস্তাদ চরিত্রটিকে যেন প্রতীক বলে মনে হয়। ওস্তাদের শিল্প জীবনের শ্রেষ্ঠ তার শিল্পসাধনা | নর্তকীর মধ্যে সে তার প্রেমকে খুঁজে পেল। কিন্তু প্রতিবন্ধক হলো ম্যানেজারের বৈষয়িক বোধ ও স্থূল ঈর্ষা। এই সংঘাতে জীবনের সামনে যখন প্রশ্ন শ্রেয় না প্রেয়, তখন শিল্পকেই শিল্পী বরণ করে নিল।
Advertisement
চলচ্চিত্রে বারীন সাহা একজন নির্মোহ, নিরাসক্ত জীবনস্রষ্টা| জীবন সম্পর্কে কোনো কাল্পনিক বা আরোপিত মসৃণতায় তিনি বিশ্বাসী নন। দর্শকের অভ্যস্ত প্রত্যাশাকে তিনি বারেবারেই নিষ্ঠুর হাতে ভেঙে দিয়েছেন। প্রেমের ত্রিভুজকে শীর্ষবিন্দুতে এনে ভেঙে চুরমার করে দর্শককে আহত বা বিক্ষুব্ধ করতেও ভয় পাননি।
বারীন সাহা চলচ্চিত্র দিয়ে উপন্যাস রচনা করতে চেয়েছিলেন অন্য শিল্পমাধ্যমের বাইরে দাঁড়িয়ে, সিনেমার নিজস্ব শর্তকে মেনে উন্নত স্বাধীন এক চলচ্চিত্র-শিল্পভাষার জন্ম দিতে। ‘তেরো নদীর পারে’ ছবিটি বারে বারেই সেই কথাই মনে করিয়ে দেয়।
Advertisement