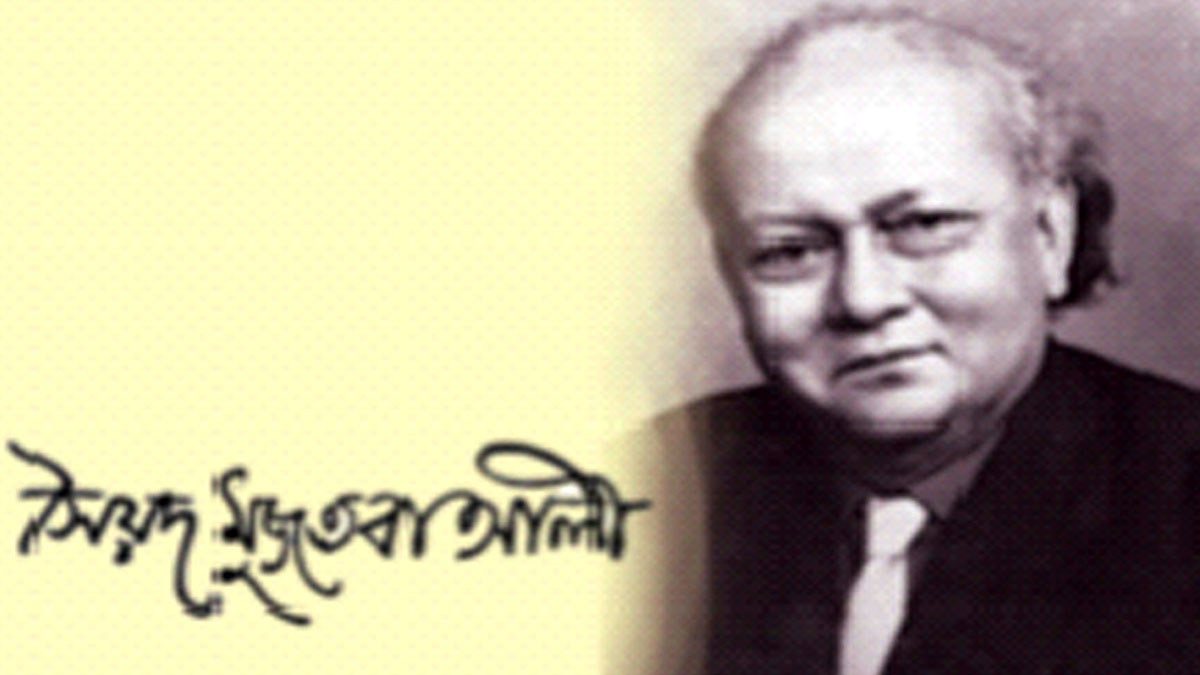পূর্ব প্রকাশিতর পর
তবে এই শোকের দিনে একটি সান্ত্বনার বাণী জানাই। সাহিত্য আকাদেমি এ পুস্তকের বাঙলা অনুবাদকর্মে লিপ্ত হয়েছেন। কিন্তু এর সঙ্গে একটি সাবধান বাণীও শুনিয়ে রাখি। সে অনুবাদে বাঙালী পাবে কাশ্মীরী শালের উল্টো দিকটা। পাবে মূলের অসম্পূর্ণ পরিচয়, এবং হয়তো পাবে অসম্পূর্ণের সম্পূর্ণ পরিচয় পাবার আকাঙ্ক্ষা। তাই যদি হয়, তবে হয়তো কোনো কোনো বাঙালীর অনাদৃত উর্দুভাষা শেখার ইচ্ছাও হতে পারে। আমাদের সে প্রচেষ্টা হয়তো শোকদুঃখের অতীত অমর্ত্যলোকে মৌলনা আবুল কালাম মহীউদ্দীন আহমদ অল্-আজাদকে আনন্দ দান করবে।
Advertisement
নসরুদ্দীন খোজা (হোকা)
ইস্তাম্বুল তেকে রয়টারের খবরে প্রকাশ, রসিক এবং মূর্খ চূড়ামণি নসরুদ্দীন খোজার সপ্তশতম জন্মদিবস মহা-আড়ম্বরে উদযাপিত হয়েছে।
Advertisement
ইংরিজি বর্ণমালার কল্যাণে ‘খোজা’ কিন্তু বাঙলায় ‘হোকা’ রূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। অধুনা তুর্কী ভাষা ইংরিজি (লতিন) হরফে লেখা হয় বলে তার রূপ hoca; কিন্তু তুর্করা ‘এচ’ অক্ষরের নীচে একটি অর্ধচন্দ্র বা উল্টো প্রথম বন্ধনী দেয় এবং তার উচ্চারণ অনেকটা স্কচ ‘লখ্ জর্মন ‘বাখ’ বা ফার্সী ‘খবরের্র মত,—কিন্তু ‘হ’ ভাগটা বেশী এবং ‘সি’ অক্ষরের উপরে একটি হুক্ দেয়—এবং তার উচ্চারণ হয় পরিষ্কার ‘জ’। ঠিক সেই রকম বাঙলা শব্দ (আসলে আরবী) ‘খারিজ’ তুর্কী ভাষায় haric লেখা হয়,— অবশ্য ‘হ’-এর নিচে পূর্বোল্লিখিত অর্ধচন্দ্র এবং ‘সি’-র উপরে হুক্ দেয়। ‘পররাষ্ট্রনীতি’ তাই তূর্কীতে ‘সিয়াসত খারিজ।’
রয়টারের টেলিগ্রামে এই অর্ধচন্দ্র ও হুক্ বাদ পড়াতে ‘খোজা’ ‘হোকা’ হয়ে গিঁয়েছেন। খাজা নাজিমুদ্দীনের ‘খাজা’ ও আগা খানের ‘খোজা’ (সম্মানিত) সম্প্রদায়ের নামেও একই শব্দ—এটি আমাদের সম্পূর্ণ অজানা নয়।
এই ধ্বনি পরিবর্তনে আমাদের রাগত হওয়ার কারণ নেই। ক্রিকেটার মাঁকড়ের নাম যখন আমরা হামেশাই ‘মনকদ’, ‘মানকদ’ অনেক কিছুই লিখে থাকি, এবং ফড়্কর-কে ‘ফাদকার’, ‘ফদকর’ লিখি, এমনকি এই কলকাতা শহরেই গোখলে-কে ‘গোখেল’ লিখি এবং উচ্চারণ করি, তখন রসিকবর খোজা যে হোকা হয়ে আমাদের ধোঁকা দেবেন তাতে আর আশ্চর্য কি?
খোজার জন্মদিন যে-বাইশ তারিখে উদযাপিত হচ্ছিল সেইদিনই ইস্তাম্বুল থেকে রয়টার আরেকটি তার পাঠিয়েছেন; তাতে খবর এসেছে যে ঐ দিন পাঁচ শ’ বছর পরে তুর্কীকে এক সুপ্ত অগ্নিগিরি জেগে উঠে হা হা করে হেসে উঠেছে।
তা হলে বোঝা গেল মা ধরণীর পাকা দু’শ বছর লেগেছে খোজার রসিকতার মর্ম গ্রহণ করতে; তাই বোধ হয় হাসতে হাসতে তাঁর নাড়িভূঁড়ি এখন ভূগর্ভ থেকে ছিঁড়ে বেরিয়েছে!
এদেশে আরবী এবং ফার্সীর চর্চা একদা প্রচুর হয়েছিল। আকবর বাদশাহের আমলে ইরানের এমনই দুরবস্থা যে সেখানকার পনেরো আনা কবি দিল্লী ধাওয়া করেছিলেন। আকবরের সভাকবি আব্দুর রহিম খানখানা নিজেই গণ্ডা গণ্ডা ইরানী কবি পুষেছিলেন, আর স্বয়ং আকবর যে কবি ‘আমি’ ‘তুমি’ মিল দিয়ে ‘কবিতা’ রচনা করতো তাঁকে পর্যন্ত নিরাশ করতে চাইতেন না।
ভারতবর্ষের ফার্সী নাম হিন্দ বা হিন্দুস্থান। ‘হিন্দ’ শব্দের অর্থ কালো। তাই এক কবি তাঁর দৈন্যের কালরাত্রি ইরানে ফেলে পূর্বাচল ভারতবর্ষ রওয়ানা হওয়ার সময় লিখলেন, ‘দুর্ভাবনার কালিমা ত্যজিয়া / চলিনু হিন্দুস্থান, / কালোর দেশেতে কালো আমি কেন / করিতে যাইব দান?’
তাই এক ইয়োরোপীয় ঐতিহাসিক হরানের ঐ যুগকে শব্দার্থে ‘ইণ্ডিয়ান সামার’ বলেছেন। কারণ এর পরই ইরানী সাহিত্যের পতন আরম্ভ হয়।
(ক্রমশ)
Advertisement