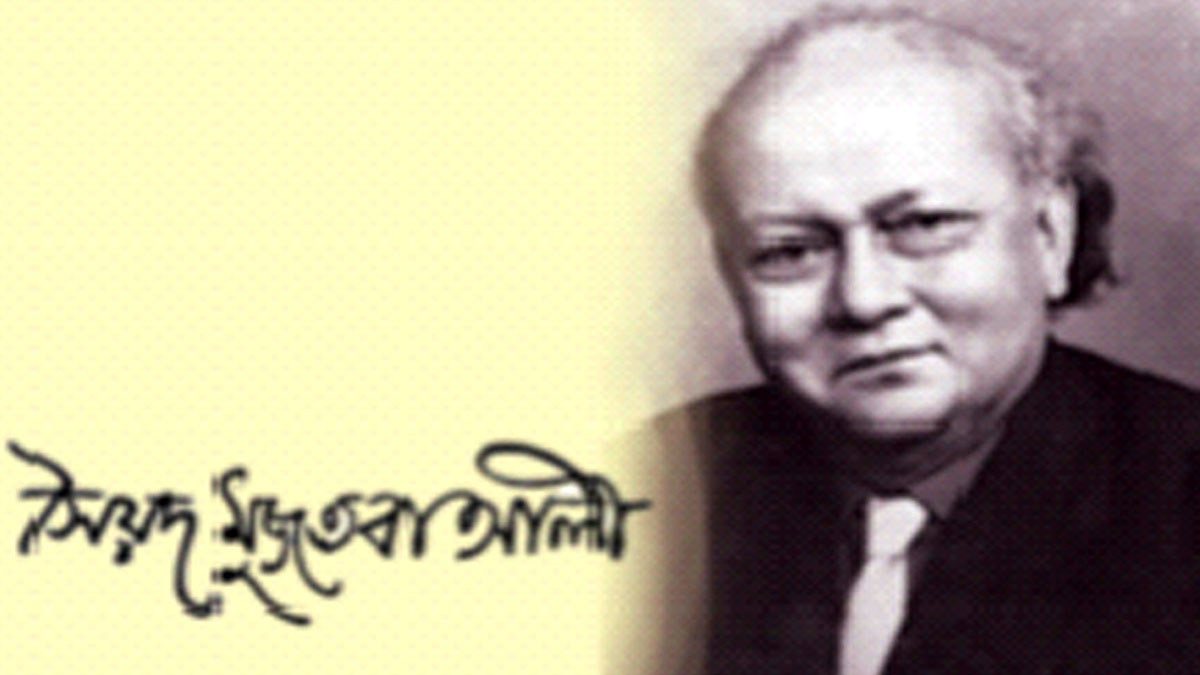পূর্ব প্রকাশিতর পর
উনবিংশ শতাব্দীর দ্বন্দ্ব প্রধানতঃ ইংরিজির সঙ্গে। এবং সেই দ্বন্দ্ব বিদ্রোহরূপ ধারণ করলো পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলনে ১৯৫১-৫২ খৃষ্টাব্দে। বাঙলা আবার জয়ী হল—কিন্তু এবারে তার জয়মূল্য দিতে হল বুকের রক্ত দিয়ে—কিন্তু আব্রু, ইজজৎ, ইমান দিয়ে নয়। পাকিস্তান হওয়া সত্ত্বেও পূব বাঙলার লোক বাঙলাতে আরেক দফে আরবী-ফার্সী শব্দ আমদানি করে ভাষাকে ‘পাক’ করতে প্রলোভিত হল না।
Advertisement
তাই এই প্রবন্ধের নাম দিয়েছি ‘মামদোর’ পুনর্জন্ম। ‘মামদোর’ই যখন কোন অস্তিত্ব নেই, তখন তার পূনর্জন্ম হবে কি প্রকারে? পূব বাঙলার লেখকদের স্কন্ধে আরবী-ফার্সী শব্দের মামদো ভর করবে, আর তারা বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে আরবী-ফার্সীতে অর্থাৎ ‘যাবনী মিশালে’ কিচিরমিচির করতে আরম্ভ করবে, বিজাতীয় সাহিত্য সৃষ্টি করবে—যার মাথামুণ্ডু পশ্চিম বাঙলার লোক বুঝতে পারবে না, সে ভয় ‘স্বপ্ন, মায়া, মতিভ্রম।।
Advertisement
দিল্লী স্থাপত্য
যাঁরা এই শীতে প্রথম দিল্লী যাচ্ছেন কিংবা যাঁরা পূর্বে গিয়েছেন কিন্তু পাঠান-মোগলের দালান-কোঠা, এমারত-দৌলত দেখবার সুযোগ ভালো করে পাননি, এ-লেখাটি তাঁদের জন্য। এবং বিশেষ করে তাঁদের জন্য যাঁদের স্থাপত্য দেখে অভ্যাস নেই বলে ঐ রস থেকে বঞ্চিত। লেখাটিকে কিঞ্চিৎ ‘মাস্টারি মাস্টারি’ ভাব থেকে যাবে বলে গুণিজনকে আগের থেকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি তাঁরা যেন এটি না পড়েন।
কোনো-কালে যে ব্যক্তি গান শোনেনি সে যদি হঠাৎ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শুনে উদ্বাহু হয়ে নৃত্য না করে তা হলে চট করে তাকে বেরসিক বলা অন্যায়। বাঙলা দেশে এখানে ওখানে ছিটেফোঁটা স্থাপত্য আছে বটে, কিন্তু একই জায়গায় যথেষ্ট পরিমাণে নেই বলে স্থাপত্যের যে ক্রমবিকাশ এবং সামগ্রিক রূপ তার রস বুঝতে সাহায্য করে তার সম্পূর্ণ অভাব। বিচ্ছিন্নভাবে যে বিশেষ একটি মন্দির, মসজিদ বা সমাধি রসসৃষ্টি করতে পারে না, তা নয়। তাই তুলনা দিয়ে বলতে পারি, জগতের কোনো সাহিত্যের সঙ্গে যদি আপনার কিছুমাত্র পরিচয় না থাকে, তবে সাধারণত ধরে নেওয়া যেতে পারে য়ে উটকো একখানা ফরাসী উপন্যাসের রস আপনি গ্রহণ করতে পারবেন না। রসবোধের জন্য ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ জ্ঞান অপরিহার্য কিনা এ প্রশ্ন নন্দনশাস্ত্রের অন্যতম কঠিন প্রশ্ন। সে গোলকধাঁধার ভিতর একবার ঢুকলে আর দিল্লী যাবার পথ পাবেন না, আর ‘দিল্লী দূর অস্ত’ তো বটেই।
কবিতা, সঙ্গীত, স্থাপত্য ভাস্কর্যের মূল রস একই—ইংরিজিতে যাকে বলে ইসথেটিক ডিলাইট। কিন্তু এক রসের চিন্মায়ারূপ (যথা কাব্যের) যদি অন্য রসের মৃন্ময়রূপে (যথা ভাস্কর্য, স্থাপত্যে) টায় টায় মিলছে না দেখেন তবে আশ্চর্য হবেন না। এদের প্রত্যেকেই মূল রস প্রকাশ করে আপন আপন ‘ভাষায়’, নিজস্ব শৈলীতে এবং আঙ্গিকে। একবার সেটি ধরতে পারলেই আর কোনো ভাবনা নেই। তার পর নিজের থেকেই আপনার গায়ে রসবোধের নূতন নূতন পাখা গজাতে থাকবে, আপনি উড়তে উড়তে হঠাৎ দেখবেন তাজমহলের গম্বুজটিও আপনার সঙ্গে আকাশ পানে ধাওয়া করেছে— নীচের দিকে তাকিয়ে দেখবেন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল যেন ক্রমেই পাতালের দিকে ডুবে যাচ্ছে।
স্থাপত্যের প্রধান রস—প্রধান কেন, একমাত্র বললেও ভুল বলা হয় না, অন্যগুলো থাকলে ভালো, না থাকলে আপত্তি নেই— তার কম্পজিশনে, অর্থাৎ তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, যেমন ধরুন, গম্বুজ, মিনার, আর্চ (দেউড়ি), ছত্রি (কিয়োসক্, পেভিলিয়ন), ভিত্তি এমনভাবে সাজানো যে দেখে আপনার মনে আনন্দের সঞ্চার হয়।
(ক্রমশ)
Advertisement