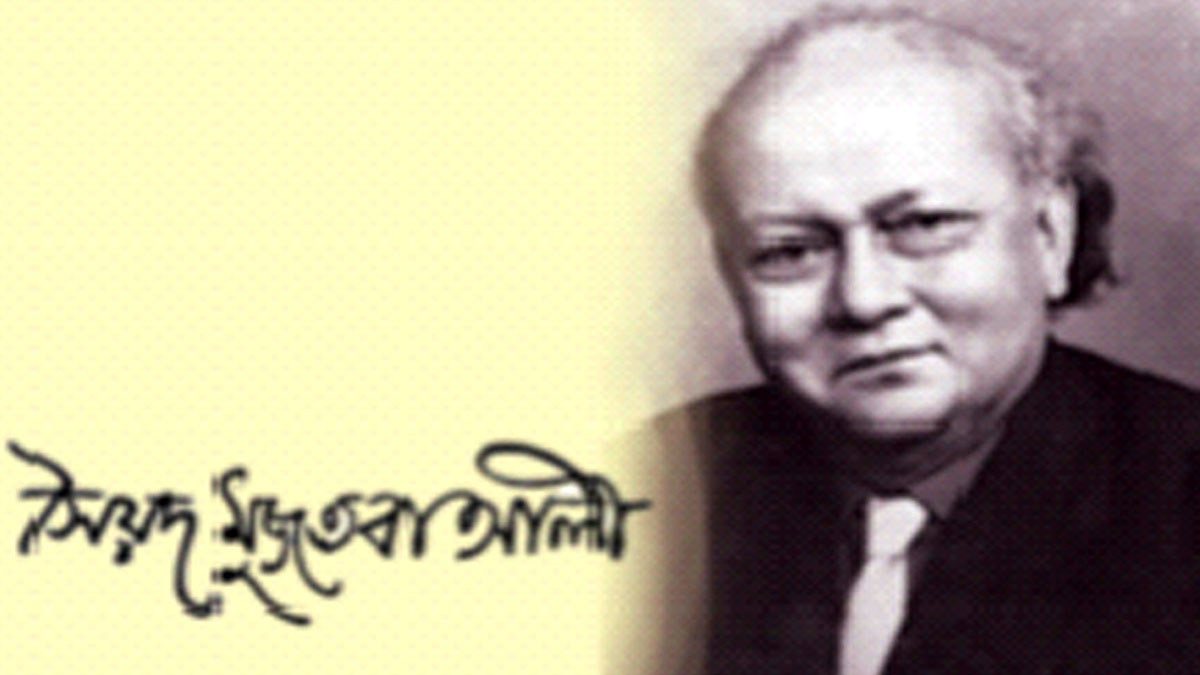পূর্ব প্রকাশিতর পর
এ সাহিত্যের প্রাণ এবং দেহ উভয়ই খাঁটি বাঙালী। এ সাহিত্যে শুধু যে মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ বাঙলায় খাঁটি কানুরূপ ধারণ করেছেন তাই নয়, শ্রীমতী শ্রীরাধাও য়ে একেবারে খাঁটি বাঙালী মেয়ে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ভাটিয়ালির নায়িকা, বাউলের ভক্ত, মুর্শীদীয়ার আশিক ও পদাবলীর শ্রীরাধা একই চরিত্র একই রূপে প্রকাশ পেয়েছেন।
Advertisement
বাঙালীর চরিত্রে বিদ্রোহ বিদ্যমান. তার অর্থ এই যে, কি রাজনীতি, কি ধর্ম, কি সাহিত্য, যখনই যেখানে সে সত্য শিব সুন্দরের সন্ধান পেয়েছে তখনই সেটা গ্রহণ করতে চেয়েছে; এবং তখন কেউ ‘গতানুগতিক পন্থা’ ‘প্রাচীন ঐতিহ্য’-এর দোহাই দিয়ে সে প্রচেষ্টায় বাধা দিতে গেলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। এবং তার চেয়েও বড় কথা—যখন সে বিদ্রোহ উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত হতে চেয়েছে, তখন তার বিরুদ্ধে আবার বিদ্রোহ করেছে।
Advertisement
এ বিদ্রোহ বাঙালী হিন্দুর ভিতরই সীমাবদ্ধ নয়। বাঙালী মুসলমানও এ কর্মে পরম তৎপর। ধর্ম বদলালেই জাতির চরিত্র বদলায় না।
পাঠান আমলে বাঙলাদেশে আরবী-ফার্সীর চর্চা ব্যাপকভাবে হয়নি। সে-যুগে বাঙলাতে লিখিত সরকারী দলিলপত্রে পর্যন্ত আরবী-ফার্সী টেকনিকল শব্দ প্রায় নেই। মহাপ্রভু এবং তাঁর শিষ্যদের কেউ কেউ মুসলমান ধর্মের সঙ্গে সুপরিচিত হওয়া সত্ত্বেও সে যুগের বাঙলা সাহিত্যে আরবী-ফার্সী শব্দ অতি অল্প।
খাস পাঠান যুগে তো কথাই নেই, মোগল যুগের প্রারম্ভেও কবি আলাওল যে বাক্য রচনা করেছেন তাতে সংস্কৃত ভাষার প্রাধান্যই লক্ষণীয়—
‘উপনীত হৈল আসি যৌবনের কাল।/ কিঞ্চিৎ ভূরুর-ভঙ্গে যৌবন রসাল।।/ আড় আঁকি বঙ্ক-দৃষ্টি ক্রমে ক্রমে হয়।/ ক্ষণে ক্ষণে লাজে তনু যেন শিহরয়।।/ সম্বরয় গিম হার, কটির বসন। / চঞ্চল হইল আঁখি, ধেরয-গমন।।/ চোররূপে অনঙ্গ অঙ্গেতে আসে যায়। / বিরহ বেদনা ক্ষণে ক্ষণে মনে ভায়।।’
এ ধরনের কাব্য তখন মুসলমানদের ভিতর কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল তার বর্ণনা পাই অন্য এক কবির কাছ থেকে। সৈয়দ সুলতান বলেন, ‘আপনা দীনের বোল্ এক না বুঝিল। / পরস্তব সকল লৈয়া সব রহিল।।’
(দীন=ধর্ম; পরস্তব=পরধর্ম কীর্তন। এর পূবেই মুসলমানরা পদাবলী কীর্তন রচনা আরম্ভ করেছেন এবং কাজী ফয়জউল্লার ‘গোরক্ষবিজয়’ মুসলমানদের ভিতর লোকপ্রিয় হয়ে গিয়েছে।)
মুসলমানরা আপন ধর্মচর্চা3 না করে ‘হিন্দুয়ানী’ কাব নিয়ে মেতে আছে দেখে মুসলমান মোল্লা-মৌলবীগণ তারস্বরে আপন প্রতিবাদে জানিয়েছেন এবং আরবী-ফার্সীতে ধর্মচর্চা করবার জন্য বার বার কড়া ফতোয়া জারী করেছেন।
তখন সৈয়দ সুলতান বললেন, ‘আমরা বাঙলা ছাড়বো না; কিন্তু মুসলমান শাস্ত্রচর্চাও করবো। তাই বাঙলাতেই মুসলমান শাস্ত্রচর্চা হবে।’
‘আরবী-ফার্সী ভাষে কিতাব বহুত।/ আলিমানে বুঝে, না বুঝে মূর্খসুত।।/ যে সবে আপন বুলি না পারে বুঝিতে।/ পাঁচালি রচিলাম করি আছয়ে দূষিতে।।/ আল্লায় বলিছে, ‘মুই যে-দেশে যে-ভাষ, সে-দেশে সে-ভাষে কইলুম রসূল প্রকাশ।’
(আলিমান=আলিমাগণ=পণ্ডিতগণ; রসূল=আল্লার প্রেরিত পুরুষ, পয়গম্বর।)
বাঙলা আর্যভূমি, কিন্তু এ ভূমির আর্যগণ উত্তর ভারতের অন্যান্য আর্যের মত নন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার স্থান এখানে নয়। তাই মাত্র কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি।
(১) বাঙলাদেশকে যখনই বাইরের কোনো শক্তি শাসন করতে চেষ্টা করছে তখনই বাঙালী বিদ্রোহ করেছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আপন স্বাধীনতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। পাঠান যুগে বাঙলা অতি অল্পকাল পরাধীন ছিল এবং মুঘল যুগেও মোটামুটি মাত্র জাহাঙ্গীর থেকে আওরঙ্গজেব পর্যন্ত বাঙলা দিল্লীর শাসন মেনেছে।
(২) অন্যান্য আর্যদের তুলনায় বাঙালী কিছুমাত্র কম সংস্কৃত চর্চা করেনি, কিন্তু সে-চর্চা সে করেছে আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে। আদিশূর থেকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সকলের বহু চেষ্টাতেও বাঙালী উত্তর ভারতের সঙ্গে স্ট্রীমলাইনড্ হয়ে সংস্কৃত পদ্ধতিতে সংস্কৃত বর্ণমালার উচ্চারণ করেনি এবং বাঙলাতে সংস্কৃত শব্দ উচ্চারণ করার সময় তো কথাই নেই।
(ক্রমশ)
Advertisement