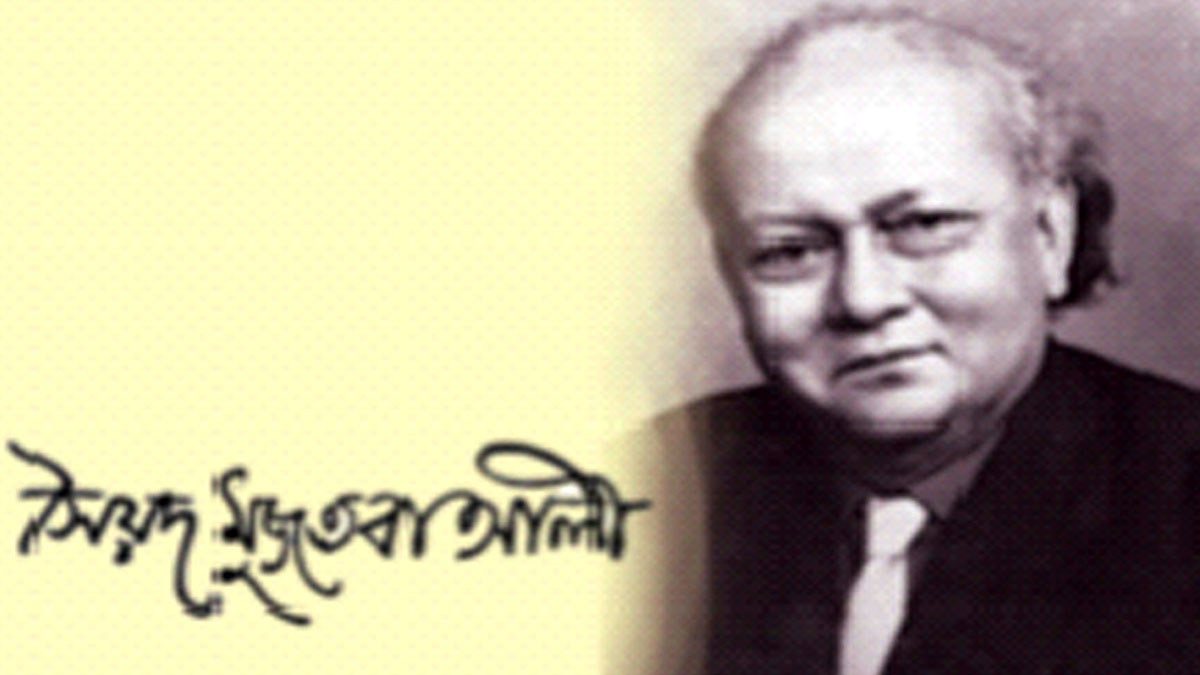পূর্ব প্রকাশিতর পর
তুর্কী-ভাষার কিছুটা চর্চাও এদেশে হয়েছিল, কারণ বাবুর, হুমায়ুন এঁদের সকলেরই মাতৃভাষা তুর্কী। শেষ মোগল বাদশা সালামৎ বাহাদুর শাহের হারেমের কথাবার্তা তুর্কী ভাষাতেই হত এবং তুর্কী সাহিত্যের সর্বোৎকৃষ্ট না হলেও অন্যতম অত্যুৎকৃষ্ট কেতাব বাবুর বাদশার আত্মজীবনী। কিন্তু এ-তুর্কী ভাষা মুস্তফা কামালের টার্কির ওসমানলী তুর্কী নয়, বাবুরের ভাষা চুগতাই (বা জগতাই) তুর্কী। কোরমা, দোলমা এবং লড়াই-হাতিয়ারের কিছু শব্দ চুগতাই তুর্কী থেকে বাঙলাতে এসেছে। ওদিকে মোগল দরবারে ফার্সীকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন বলে তাঁদের তুর্কী এদেশে প্রচার ও প্রসার লাভ করেনি—যদিও প্রাচীন বাঙলাতে ‘তুর্ক’ বলতে মুসলমান বোঝাতো এবং তামিল ভাষাতে মুসলমান বোঝাতে হলে এখনও ‘তুরষ্কম্’ শব্দ ব্যবহার করা হয়। বাঙালী বেকার এখনো চাকরির সন্ধানে ‘তুর্কী নাচন’ নাচে।
Advertisement
আমরা ইংরিজী ফারসী পড়ি, রাশান কথাসাহিত্যও আমাদের অজানা নয়, স্পেন পর্তুগাল দেনমার্কের লোক এদেশে এসেছিল এবং আরো অনেকেই,— কিন্তু আশ্চর্য, ওসমানলি তুর্কী ভাষা এবং সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের কণামাত্র পরিচয় নেই। আমার জানামতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে পাবনা জেলার কবি ইসমাঈল হুসেন শিরাজী (নজরুল ইসলাম এঁর কাছে একাধিক বিষয়ে ঋণী বলে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন) তুর্কীকে সাহায্য করার জন্য একটি মেডিকেল মিশন নিয়ে সেদেশে গিয়েছিলেন এবং তুর্কী রাজনীতি, সমাজ, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে বাঙলায় একাধিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তুর্কীর সভাকবি হামিদ পাশার সঙ্গে সে সময়ে তাঁর হৃদ্যতা হয়, কিন্তু তুর্কী সাহিত্যের সঙ্গে বাঙলার পরিচয় করিয়ে দেবার পূর্বেই ইংরেজের চাপে তাঁকে দেশে ফিরে আসতে হয়।
Advertisement
তুর্কীর বাইরে ইরান, আফগানিস্থান, উজবেকিস্তান, আজারবাইজান, তথা গ্রীস, বুলগারিয়া, রুমানিয়া ইত্যাদি দেশে নসরুদ্দীন খোজা সুপরিচিত। ইরানের স্বর্ণযুগের একাধিক সুরসিক কবির উপর তাঁর প্রভাব সুস্পষ্ট। বল্কানের বাইরে ইয়োরোপে তিনি জর্মনিতে সবচেয়ে বেশী ভক্ত পাঠক পেয়েছেন। ইংরিজী এনসাইক্লোপীডিয়াতে তাঁর নাম নেই, জর্মন সাইক্লোপীডিয়া আকারে ইংরিজীর অর্ধেক হওয়া সত্ত্বেও সেটাতে তাঁর সম্বন্ধে কয়েক ছত্র আছে। আর একাধিক অনুবাদ জর্মন ভাষাতে তো আছেই। অবশ্য আজকের দিনের রুচি দিয়ে বিচার করলে তাঁর বহু কুট্টনীরসাশ্রিত জিনিস শুধু লাতিনেই অনুবাদ করা যায়।
খোজার জীবনী নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করার উপায় নেই। কারণ তাঁর জীবন ও তাঁর হরেক রকমের রসিকতা এমনই জড়িয়ে গিয়েছে যে তার জট ছাড়ানো অসম্ভব। তাঁর সম্বন্ধে প্রচলিত দু’আনা পরিমাণ কিংবদন্তী বিশ্বাস করলে আমাদের কালিদাস সম্বন্ধে প্রচলিত সব ক’টাই বিশ্বাস করতে হয়। এমন কি তিনি পাঁচ শ’ না সাত শ’ বছর আগে জন্মেছিলেন সেই সমস্যারই চূড়ান্ত সমাধান এযাবৎ হয়নি। তবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে খোর্তো গ্রামে তাঁর জন্ম, সম্ভবত ত্রয়োদশ শতাব্দীতে, এবং আকশেহিরে তাঁর মকবরহ্ বা সমাধিসৌধ দেখানো হয়। ইনি যে সুপণ্ডিত এবং সুকবি ছিলেন সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই, কারণ ধর্মশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি না থাকলে ‘ইমাম’ (ইংরিজিতে অন্ততপক্ষে বিশপ) হওয়া যায় না। অন্যান্য একাধিক ব্যাপারেও তিনি সমাজের অগ্রণীরূপে তুর্কী এবং তুর্কীর বাইরে সুপরিচিত ছিলেন।
স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে তাঁর নামে প্রচলিত গল্পের ক’টি তাঁর নিজস্ব ও ক’টি উদোর শিরনি বুধোর দর্গায়, সে-বিচার অসম্ভব। দেশ-বিদেশের পণ্ডিতগণ হার মেনে বিক্রমাদিত্যের নামে প্রচলিত গল্প যে ‘বিক্রমাদিত্য সাইকল্’, খৈয়ামের নামে চলিত-অচলিত চতুষ্পদী ‘খৈয়াম চক্র’ নামে অভিহিত করেছেন ঠিক সেইরকম এখন খোজার নামে লিখিত পঠিত, শ্রুত গল্পকে ‘খোজা চক্র’ নাম দিয়ে দায়মুক্ত হন। কিন্তু গল্পগুলো বিশ্লেষণ করে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেঝন যে তার অনেকগুলোই আরবভূমি, প্রাচীন ইরান ও ভারতবর্ষ থেকে গিয়েছে। সিরিয়া এবং প্রাচীন বল্কানেও এর অনেকগুলো প্রচলিত ছিল।
(ক্রমশ)
Advertisement