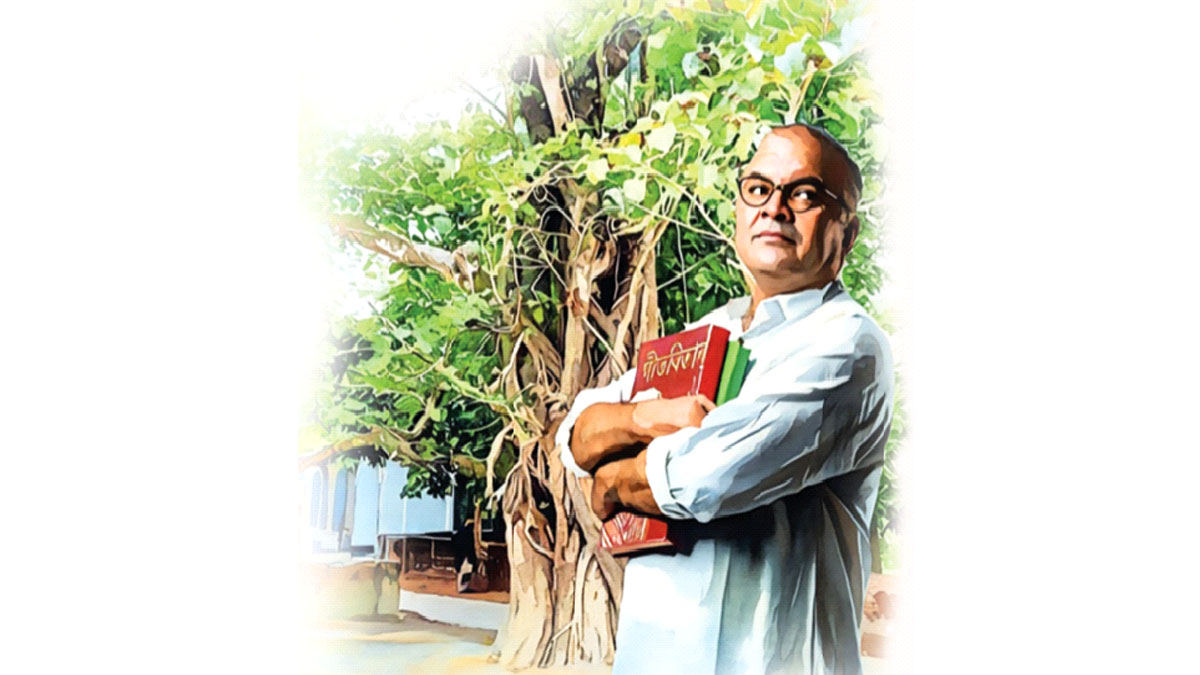অমিয় আদক
বাবা সরকারি চাকুরে। বদলির চাকরি। বদলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মহকুমা শহরে। বাবার পছন্দের অস্থায়ী আস্তানা গাঁয়ের ভাড়াবাড়ি। তাঁর গাঁয়ের প্রতি একটা ভিন্ন ধরণের টান। তখন পড়ি ক্লাস এইটে। বাবার বদলি আরামবাগে। ভাড়ার আস্তানা গৌরহাটিতে। বাবা জয়েন করার পর একমাস কাটে। আমি মা বোন এবং লটবহর সমেত হাজির গৌরহাটিতে। ভট্টাচার্য পরিবারের বাড়ির একটা অংশের আমরা বাসিন্দা। আমার স্কুল গৌরহাটি হরদয়াল ইনস্টিটিউশন। বোনের স্কুল লাগোয়া প্রাইমারি। ধীরে ধীরে আমাদের পরিচিতির গণ্ডি বাড়ে।
Advertisement
কয়েক মাসের মধ্যেই কাছাকাছি পরিবারগুলির সঙ্গে পরিচিত। তৈরি একটা প্রতিবেশী সুলভ মিষ্টি সম্পর্ক। মজবুত সম্পর্ক। সেখানে মায়ের চেয়ে বাবার ভূমিকাই বেশি। বাবার টুকটাক লেখালিখির অভ্যেস। ছোটদের নাটক লেখেন। পাড়ার ছেলেমেয়েদের দিয়ে অভিনয় করানোয় বেশ আনন্দ তাঁর। বাবা পড়ায় রবীন্দ্রজয়ন্তীর অনুষ্ঠান করান নিজের খরচে। সেখানে আমরা ভাইবোন অংশ নিই। সব মিলিয়ে বাবা প্রতিবেশিদের সমীহ পান। সম্মান পান।
Advertisement
সে বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছি। রেজাল্টের অপেক্ষায়। বিগত তিন বছরে আমিও বাবার জুতোয় খানিক পা গলানোর চেষ্টায়। ছোটছোট গল্প লিখি। ছড়া লিখি। বাবাকে দেখাই। প্রয়োজনীয় সংশোধনের ছোঁয়া পায়। ছড়া, গল্পগুলো বাবাই ডাকে পাঠান। মৌচাক, শুকতারা ইত্যাদি পত্রিকায়। দু’বছরে পাঁচটা গল্প, চারটে ছড়া প্রকাশিত। স্কুলের পত্রিকায় সেবার লিখি গল্প। একটা ছোট মেয়ের কষ্টের গল্প। গল্পের মেয়েটার নাম মণিমালা। গল্পটির প্রশংসা স্যারেদের মুখেও পাই। কিশোর আমি। একরাশ মুগ্ধতার অনুভব অন্তরে। আমি আরও ভালো গল্প লিখবো। এমন প্রেরণা নিজের মধ্যেই ঘুরপাক খায়।
সেবার পাড়ার রবীন্দ্রজয়ন্তী। ছোটদের নাটক ডাকঘর। তার আগে রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাটক কর্ণ-কুন্তী সংবাদ। কর্ণের ভূমিকায় আমি। কুন্তীর ভূমিকায় তনিমাদি। তনিমাদির ক্লাস টুয়েলভ। বাবার উপস্থিতিতে রিহার্সাল চলে। কোনোদিন বাবার অফিস ফেরৎ আসার আগেই আমরা দু’জন মহড়া চালাই। পঁচিশে বৈশাখ আমাদের কাব্যনাটকের পর দুই কুশীলব গ্রিনরুমে। তনিমাদি জানায়, ‘আবির, তোর একটা জিনিস আমার কাছে গচ্ছিত আছে। আমার সামনে পরীক্ষা। ট্যুইশনের চাপ আছে। তুই সময়করে আমাদের বাড়িতে যাবি। গিয়ে নিয়ে আসবি।’
‘কী এমন জিনিস আছে তোমার কাছে?’
‘হাতে পেলেই বুঝতে পারবি। আমি কিন্তু তোকে দিতে আসতে পারবোনা। এটা খেয়াল রাখিস। নিজে গিয়ে আনবি। অন্য কারও হাতে পাঠাতে বলবি না। তাছাড়া মা তোর প্রিয় খবার তিলের নাড়ু বানিয়ে রেখেছে। গিয়ে খেয়ে আসিস। মা বলেছে, অতি অবশ্যই যাবি। নইলে মা রাগ করবে।’
‘তা আজতো আনতে পারতে?’
‘তাড়াহুড়োয় খেয়াল ছিলো না রে। যাকগে, মনে করে আনিস। বিকেলের দিকে যাবি। নাড়ু খেয়ে আসবি।’ তনিমাদি ব্যাগ গুছিয়ে রেডি। তার বাবা বাইরে অপেক্ষমান। ‘আসছি রে…’ বলেই বেরিয়ে যায় তনিমাদি। তনিমাদির কাছে গচ্ছিত কিছু জিনিসের প্রতি তেমন আগ্রহও আমার অনুভবে নেই। ভেবে রাখি, সময় করে গিয়ে আনবো। আমিও বিষয়টা সাময়িক ভুলে যাই। যাওয়া হয়নি তনিমাদির বাড়ি। তনিমাদি হয়তো আমাকে বিষয়টা পুনরায় মনে করানোর তাগিদ অনুভব করেনি। যাইহোক গচ্ছিত জিনিসটার কথা বেমালুম ভুলে যাই।
রবীন্দ্রজয়ন্তীর দু’দিন পর। অফিসে বাবার শরীর খারাপ। সেই খবর আমাদের কাছে পৌঁছানোর আগেই তাঁর কলিগরাই ভর্তি করেন আরামবাগ হাসপাতালে। তিনদিন চিকিৎসা চলে সেখানে। তারপরেও বাবার অবস্থার সামান্য উন্নতিও নেই। বিমর্ষ মেডিসিনের বিখ্যাত ডাক্তার। তিনি আশার আলো দেখাতে অক্ষম। সে কথাই জানান। তিনিই পরামর্শ দেন কলকাতার বড়ো হাসপাতালে চিকিৎসা করানোর। সেই খবর বড়োমামাকে জানাই। বড়োমামা আসেন। তিনি এবং মা মিলে বাবাকে নিয়ে যান এসএসকেএমে। আমি বোন ভটচায জেঠিমার দায়িত্বে।
আমাদের থাকা খাওয়া-দাওয়ার কোনও অসুবিধা নেই। বোন ভটচাজ জেঠিমার কাছেই শোয়। প্রায় সারাদিন জেঠিমার কাছে কাছেই ঘোরে। গ্রীষ্মের ছুটি। স্কুল নেই। পড়তে বসতে চায় না। তার চোখে মুখে উদ্বেগের চিহ্ন। আমিও উদ্বিগ্ন। সেটা অপ্রকাশিত রাখার চেষ্টা করি।
মা রোজ টেলিফোন বুথ থেকে ফোন করে। প্রতিদিন সন্ধ্যার সামান্য পরে। আমাদের খোঁজ- খবর নেয়। পাশাপাশি বাবার শারীরিক অবস্থার খোঁজ পাই। তাই আমরা ভাইবোনে সন্ধ্যায় হাজির থাকি ভটচাজ জেঠিমাদের ঘরে। ল্যান্ডফোনের রিংটোন কানে আসে। রিসিভার তুলি। মায়ের সঙ্গে কথা বলি। কুড়ি বাইশ দিন এমনি ভাবেই কাটে। বোন মাঝে মাঝেই কান্নাকাটি করে। তাকে পরিস্থিতি বোঝানোর চেষ্টাকরি। ভটচাজ জেঠিমাও বোঝান তাকে। বাবামায়ের অনুপস্থিতিতে সে-ই বেশি কষ্ট পায়।
ক’দিন পরেই কষ্ট আমাদের জীবনে জগদ্দল পাথরের মতোই চেপে বসে। সেদিন দুপুরেই পাই বাবার মৃত্যু সংবাদ। ভটচাজ জেঠু স্কুল থেকে ছুটি নিয়ে বাড়ি ফেরেন। জেঠু একেবারে একটা মারুতি ভ্যান নিয়েই ফেরেন। সেই ভ্যানে চড়ে জেঠু, জেঠিমা, আমি এবং বোন। সন্ধ্যার সামান্য আগে পৌঁছাই হাসপাতালে। বাবার দেহ নিয়ে যাই কেওড়াতলা শ্মশানে। যথা নিয়মে দাহকার্য মেটে। ক’দিন পরে শ্রাদ্ধ। শ্রাদ্ধও নিতান্তই সংক্ষিপ্ত আয়োজনে।
আমাদের ঠিকানা বদলায়। আমরা চলে যাই বারাসত। মামার বাড়ি। আমরা থাকি মামাদের বাড়ির এক কামরায়। মা ভটচাজজেঠুকে ফোনে আমার ট্রান্সফার সার্টিফিকেটের কথা বলেন। ক’দিন পরেই ডাকযোগে টিসি হাজির। ভর্তি হই বারাসতের নবপল্লি হাইস্কুলে। ক’মাসের খরচ পাতি মেজোমামাই দেন। আমাদের আলাদা হাঁড়ি। বারান্দায় স্টোভের আগুনে রান্না। প্রায় পাঁচ মাসের মাথায় মায়ের চাকরি। ডায়েড ইন হারনেস গ্রাউন্ডে। ফোর্থ ক্লাস স্টাফের চাকরি।
বড়োমামা চেষ্টা করেন। মায়ের চাকরি স্থল বারাসত খাদ্য সরবরাহ অফিস। একটা থিতু অবস্থা পাই। আমার বোনের লেখাপড়া চলে। মা নিজেই আমা্দের পড়া দেখিয়ে দেন। ট্যুইশন ছাড়াই পড়াশোনা চলে। বিএসসি অনার্স করেই চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতি চালাই। পেয়ে যাই সরকারি চাকরি। ইউথ ওয়েলফেয়ার অফিসার হিসাবে। ফার্স্ট জয়েনিং হুগলি জেলার খানাকুল এক নম্বর ব্লকে। এক কামরা ঘর ভাড়া নিই খানাকুলে। খানাকুল থেকে গৌরহাটির দূরত্ব কয়েক কিমি।
এক রোববারে বেরিয়ে পড়ি গৌরহাটি। ভটচাজ জেঠুদের ল্যান্ডফোনের রিসিভার তখন চিলেকোঠায়। জেঠুর মোবাইল নম্বর জানি না। বিনা খবরেই হাজির। জেঠিমা বেজায় খুশি। জেঠুও তাই। জেঠিমা আমার চা জলখাবারের জন্য ব্যস্ত। সেই ফাঁকেই তনিমাদির খোঁজ নিই। জেঠিমা জানান, সে তো এখন প্যারিসে। ইঞ্জিনিয়ার বরের সঙ্গে যেতে বাধ্য। সে ভালোই আছে।’ তনিমাদির দেখা পাবো না ভেবেই মনটা বেজায় খারাপ। তবুও জেঠিমাকে জানাই, ‘যাবো ওদের বাড়ি।’ কাপের চা-টা শেষ করেই বলি, ‘আমি আসছি জেঠিমা, তনিমাদিদের বাড়ি যাবো।’
—দুপুরে খাবি না? জেঠু তো আবার বাজার গেলো।
—না জেঠিমা, আমি তনিমাদিদের বাড়ি থেকেই খানাকুল ফিরবো। অফিসের কিছু জরুরি কাজ আটকে আছে। সারতে
হবে। পরে আবার আসবো।
—ঠিক আছে। আবার আসিস। দুগ্গা, দুগ্গা। মাকে ফোন করতে বলিস।
‘আচ্ছা, বলবো। মাকে কয়েক মাস পরে আনবো এখানে…’ কথাটা বলেই পরিচিত রাস্তায় হাঁটতে থাকি। তনিমাদির ভাইয়ের সঙ্গে পথেই দেখা। গিয়ে পৌঁছাই। মনের মাঝে গচ্ছিত জিনিটার কথা নড়াচড়া করে। রাতচরা ইঁদুরের মতো। তনিমাদি নেই। পাবো কিনা, সন্দেহের দোলাচলে। পথেই নীহারকে বলি বিষয়টা নিয়ে। নীহার জানায়, দিদি যদি আপনাকে বলে থাকে, তাহলে সেটা থাকবেই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। পৌঁছাই নীহারদের বাড়ি। আমায় দেখেই অবাক। বলেন, ‘আবির, আর কোনদিন তোর দেখা পাবো ভাবিনি। কী ভাগ্য আমার! বোস বাবা বোস। বাড়ি থেকেই তো?’
—না জেঠিমা আমি খানাকুল থেকে আসছি।
—খানাকুল থেকে!
—খানাকুলেই আমার চাকরি।
—ওমা, তাহলে তো ভালোই। তা আমাদের বাড়ি থেকেই চাকরি কর। ঘরভাড়া করার দরকার নেই।
—আমি দিন পনেরো আগে জয়েন করেছি। খানাকুলেই এক কামরা ঘরভাড়া নিয়েছি।
—তোকে হাত পুড়িয়ে রান্না করতে হবে না। আমাদের এখানে চলে আয়।
—না জেঠিমা, তোমায় এই বয়সে আর এমন ঝক্কিতে ফেলতে চাই না। কাছে অফিস। কোনও অসুবিধে নেই।
—একটু চা করি?
—তোমাকে কিছুই এখন করতে হবে না। ভটচাজজেঠুদের বাড়িতে পেট ঠুষে খেতে বাধ্য। সে জেঠিমা একেবারে নাছোড়।
পরে অন্য একদিন এসে তিলের নাড়ু খেয়ে যাবো।
—ওঃ আমার কী ভাগ্য। আবির তিলের নাড়ুর কথা আজও মনে রেখেছে। নীহার খেতে চায় না। তাই আর করিনি। খবর দিয়ে আসিস। তোর জন্যে বনিয়ে রাখবো। তা একটু চাও খাবিনে?
—পরে বলছি। আমি তনিমাদির সঙ্গে একটু কথা বলবো। নীহার বলেছে একটু পরেই ভিডিও কল করবে। এখন তো তাদের সকালবেলা।
মোবাইলে ভিডিও কলে কথা বলতে থাকে নীহার। আমার হাতে মোবাইল ধরানোর আগে বলে, ‘দ্যাখ্ দিদি কে এসেছে?’ স্ক্রিনে আমাকে পেয়েই দিদির প্রশ্ন, ‘কিরে? অ্যাদ্দিনে মনে পড়লো?’
—মনে না থাকলে গৌরহাটি এলাম কীকরে? কেমন আছো? জামাইবাবুর সঙ্গে পরিচয় করাও।
—দাঁড়া, ডাকি অনিকে।
—তুমি জামাইবাবুর নাম ধরছো?
—তোর বৌও তোর নাম ধরবে। অ্যাই শুনতে পাচ্ছো? আমার আবিরভাইয়ের সঙ্গে আলাপ করাই। তোমাকে তো আবিরের গল্প বলেছি।
—বরের কাছে আমার গল্পও বলা হয়ে গেছে?
—বেশ করেছি বলেছি। তুই কি আমার নিজের ভাইয়ের চেয়ে কম কিছু?
—জামাইবাবু এখনও এলেন না। যাকগে, আমার কি একটা জরুরি জিনিস তোমার কাছে ছিল? সেটা তো নেওয়া হয়নি। সেটা কোথায় আছে?
নীহারকে বলে দাও। তাহলে আমি পাই।
—নীহারকে বল, পুরানো একটা ব্যাগ ঝুলছে আমার ঘরে। সেটার মধ্যে তিনটে সাদা খাম। একটা খামের কোনায় লেখা আছে ‘আবির’। সেই খামটা দিতে।
—ঠিক আছে। নীহারকে বলছি। জামাইবাবুর দেখা এখনও পাইনি।
—আসছে রে আসছে। অতো তাড়া কীসের? ঠাকুর দেবতা নয় রে ভাই মানুষটা। অতো দেখার তাড়া করে লাভ নেই।
জামাইবাবুর মুখ স্ক্রিনে ভাসে। পারস্পরিক পরিচয় সারি। নতুন চাকরির জন্য বাড়তি শুভেচ্ছা পাই। বেশ সুন্দর কথা বলেন তিনি। মনে মনে তনিমাদির সুখী দাম্পত্য জীবনের কামনা করি। মুখে বলতে লজ্জা পাই। তাঁদের ‘বাই’ জানিয়ে ভিডিও কলে ইতি টানি। মনের মাঝে আকুলি-বিকুলি খামটাকে ঘিরে। ইতিমধ্যেই সেটি আমার কোলে হাজির। নীহার ভিডিও কলের মাঝেই সেটিকে আমার কোলে রাখে। খামটি আর সাদা নেই। বেশ ধূসর আভাস তার শরীরে। কী আছে সেটির মধ্যে? তা একান্তই অনুমানের বাইরে। খানাকুল ফিরে খোলার সিদ্ধান্ত নিই। সেটিকে পকেটে পুরি। উঠে দাঁড়াই। জেঠিমার বাড়ি থেকে হেঁটেই হাজির বাসস্ট্যান্ডে।
সন্ধ্যায় কিছু লেখালিখি করি। রাতের রান্না সারি। খেয়ে নিই ন’টার আগেই। বিছানায় বসি। প্যান্টের পকেট থেকে আনি সেই ধূসর খাম। মুখটা কেটে বের করি। লম্বা কয়েক পাতার চিঠি। মনের মাঝে উৎকণ্ঠা মেশানো আগ্রহ। পড়তে শুরু করি। বেশ পরিচ্ছন্ন হাতের লেখা। আমার চেয়েও সুন্দর হস্তাক্ষর। তার অনুযোগ, আমার স্কুল পত্রিকায় লেখা গল্পের মণিমালা এবং ব্যক্তি মণিমালার মাঝে সে কোনও ফারাক খুঁজে পায়নি। তার প্রশ্ন এই অবাক করা সমাপতন নিয়ে। গল্পের মাণিমালার মা নেই। তারও মা নেই। গল্পের মণিমালা এবং পত্রলেখিকা মণিমালা দু’জনাই ক্লাস সিক্সের ছাত্রী। দু’জনেই শ্যামলা বরণী। দু’জনেই মিষ্টি দেখতে। গল্পে মণিমালার বেদনাকে আমি যেভাবে এঁকেছি, বাস্তবের মণিমালা তেমন বেদনাই অনুভব করে। তাই সে আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। আমার লিখিত অনুমোদন পেলেই তবে সে দেখা করতে আসবে।
এতো বছর পরে সেই চিঠি পেয়ে সত্যিই আমি দিশেহারা। এখন গৌরহাটি গাঁয়ের সেই মণিমালাকে খুঁজতে সামনে রোববারেই যাই গৌরহাটি। আমার সাহায্যকারী নীহার। মণিমালার খোঁজ পাই। পাই মণিমালার মোবাইল নম্বর। খানাকুল ফিরে বিকেলেই ফোন করি।
মণিমালার প্রথম প্রশ্ন, আপনি কে বলছেন?
—আমি গৌরহাটি হরদয়াল ইন্সটিটিউশনের এক সময়ের ছাত্র আবির বলছি। আমি স্কুলের পত্রিকায় মণিমালা নামে একটা গল্প লিখেছিলাম।
আপনি গৌরহাটির ভুবন মাজীর মেয়ে মণিমালা তো?
—হ্যাঁ, আমাকে আপনি আজ্ঞে করা আপনার ঠিক হচ্ছে না। যাই হোক, এখন আর মাজী নই, ভৌমিক। এতো দিন পরে আমার চিঠি পেলেন?
নাকি ইচ্ছা করেই দেরিতে উত্তর দিচ্ছেন?
—আমার জীবনেও অনেক বিপর্যয় ঘটেছে। বিশ্বাস করুন। আমি আপনার চিঠি মাত্র ক’দিন আগে পেয়েছি। আপনার কী বলার আছে? বলুন।
—যে সময় চিঠি লিখেছি, সেই সময় সত্যিই অনেক কিছু বলার ছিলো। তারপরে প্রায় বারো বছর বা একযুগ পেরিয়েছে। সেই মন, সেই আবেগ, সেই অনুভূতি কবেই হারিয়েছে হেমন্তের সিরোস্ট্র্যাটাস মেঘের মতো। এখন বলার মতো সত্যি কিছুই নেই। আপনার এখনকার ঠিকানা জানাবেন। একদিন গিয়ে প্রণাম করে আসবো।
মণিমালাকে বলি, ‘প্রণাম নিতে পারবো না, মণিমালা। খানাকুলে এসে দেখা করতেই পারেন।’ মণিমালার কথাই সত্যি। আমাদের জীবন থেকে অনেক কিছুই হারায় সিরোস্ট্র্যাটাস মেঘের মতো। কিংবা সময় কেড়ে নেয় অনেক কিছুই, যা চলে যায় ‘না ফেরার দেশে’।
Advertisement