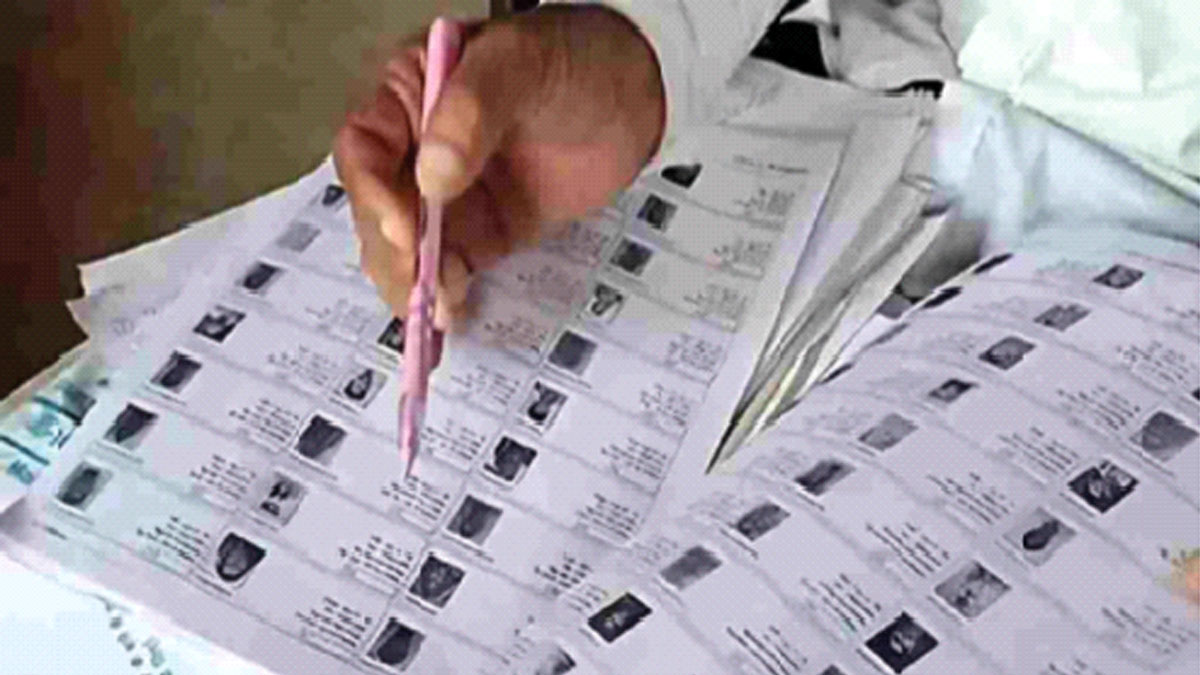আজ থেকে একশ বছর আগে প্রকাশিত ‘জেকবস রুম’ (১৯২২) সাহিত্য জগতে এক নতুন যুগের সূচনা করেছিল। এই সময় থেকেই ভার্জিনিয়া উলফ (১৮৮২-১৯৪১)কে আধুনিকতার মুখ হিসাবে চিহ্নিত করা হল। ভার্জিনিয়ার প্রথম উপন্যাস ‘দ্য ভয়েজ আউট’ প্রকাশিত হল ১৯১৫ তে এবং এর ঠিক চার বছর বাদে দ্বিতীয় উপন্যাস ‘নাইট অ্যান্ড ডে’ (১৯১৯)। তিনি লেখালেখি শুরু করেন ১৯০০ সাল থেকে। টাইমস লিটারারি সাপ্লিমেন্টে তাঁর প্রথম লেখা প্রকাশিত হয়েছিল।
ভার্জিনিয়ার জন্ম লন্ডনে। বাবা স্যার লেসলি স্টিফেন এবং মা জুলিয়া ডাকওয়ার্থ। স্টিফেন পরিবার কেনসিংটনের হাইড পার্কে বাস করত। এটা ছিল একটা সম্মানিত মধ্যবিত্ত পাড়া। বাবা লেসলি স্টিফেন ছিলেন একজন ভিক্টোরিয়ান লেখক। বাড়িতে ছিল বড় গ্রন্থাগার। তাই অল্প বয়স থেকে নানা ক্লাসিক সাহিত্য ও বিভিন্ন বিষয়ের বই পড়ার সুযোগ ঘটে। ভিক্টোরিয়ান যুগে জন্মানোর ফলে দুই ভাইকে কেমব্রিজে ভর্তি করলেও তাঁকে প্রথাগত শিক্ষার জন্যে স্কুলে না পাঠিয়ে গৃহশিক্ষকের কাছে পড়ানো হল। কিন্তু তাঁর পড়াশুনায় ঘাটতি ছিল না। সাহিত্য পরিমণ্ডলে তিনি বেড়ে উঠেছিলেন এবং প্রচুর বই পড়ার সুযোগ ঘটেছিল, যার ফলে গভীর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেন। যা পরবর্তীকালে সাহিত্য রচনায় কাজে লাগল। তিনি ছিলেন কবি, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক, জীবনীকার একজন নারীবাদী লেখক। তাঁর প্রতিটি উপন্যাসে নতুনভাবে ধরা পড়েছে আধুনিকতাবাদী ধরন। প্রতিটা রচনা সেই সময়কে প্রতিনিধিত্ব করছে।
Advertisement
মাত্র তেরো বছর বয়েসে তিনি মাতৃহারা হন। বাইশে বাবাকে হারান। এই দুই শোক তাঁকে অস্থির করে তোলে। সঙ্গে ছিল সৎ ভাইদের দ্বারা যৌন লাঞ্ছনা। ইত্যাদি নানাবিধ কারণে মানসিক ভারসাম্য হারান তিনি। চিকিৎসার পরে সুস্থ হলে ‘টাইমস লিটারারি সাপ্লিমেন্টে’ লিখতে শুরু করেন। ১৯০৫ থেকে আমৃত্যু সেই ধারা অক্ষুণ্ণ ছিল। এক বলিষ্ঠ এবং প্রতিভাশালী বন্ধুবৃত্ত ‘ব্লুমসবারি গ্রুপ’-এ পরিচয় হল লেনার্ড উলফের সঙ্গে। ১৯১২য় লেনার্ড বিয়ে করলেন ভার্জিনিয়াকে। ১৯১৭ এ লেনার্ড আর ভার্জিনিয়া ‘হগার্থ প্রেস’ নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা খুললেন। এখান থেকেই ১৯২২-এ টি এস এলিয়টের ‘দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড’ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ভার্জিনিয়া একের পর এক লিখে চলেছেন উপন্যাস, সাহিত্য সমালোচনা এবং জীবনী। তাঁর কলম গর্জে উঠেছে পুরুষশাসিত সমাজ এবং লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে। ১৯২৯ সালে তাঁর কলম থেকে বেরিয়ে এল অসাধারণ এক গ্রন্থ, ‘এ রুম অফ ওয়ানস ওন’। এই উপন্যাসটিকে বলা হয় নারীবাদী সাহিত্যের বাতিঘর। মহিলা সাহিত্যিকদের মনের উপরে পুরুষদের নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে শাণিত যুক্তিবাদী আক্রমণ এবং তীব্র প্রতিবাদী সুর শুনতে পাই এই উপন্যাসে। সাহিত্যে নারীদের ভুমিকা, তাঁদের যন্ত্রণার কথা তুলে ধরা হয়েছে। ভার্জিনিয়া বলেছেন মেয়েদের লেখার ইতিহাস হল বঞ্চনা, সমালোচনা আর বিরোধিতা পেরিয়ে আসার কাহিনী। তিনি বলেছেন, আমাদের দরকার এমন এক সভ্যতার যেখানে থাকবে না লিঙ্গ বৈষম্যের সুর। শেক্সপিয়ারের বোনের মর্মস্পর্শী কাহিনিতে শোনা যায় অজ্ঞাতনামা নারীদের কথা যাঁরা হয়তো সফল লেখিকা হতে পারতেন।
Advertisement
‘এ রুম অফ ওয়ান্স ওন’ প্রকাশিত হলে সমালোচকেরা তাঁকে বিভিন্নভাবে আক্রমণ করতে থাকেন। কেউ কেউ তাঁকে একই সঙ্গে ‘স্পিরিটেড অ্যান্ড গুড টেম্পারড’ বলে অভিহিত করেন।
ভার্জিনিয়া দেখিয়েছেন পুরুষশাসিত সমাজে শাসক যে মুহূর্তে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন, তখনি তাঁর ভিতরে ক্রোধের জন্ম হয়। তিনি অষ্টাদশ শতকের শেষের এক পরিবর্তনের কথা শোনালেন। সেই সময়ে কেবলমাত্র সম্ভ্রান্ত মহিলারাই নন সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মহিলারা লিখতে শুরু করেছেন। সাহিত্যের গুণমান কেমন ছিল সেটা বিচার্য নয়। তাঁর মতে এই সকল পূর্বসূরী ছাড়া জেন অস্টেন, এমিলি ব্রন্টি বা জর্জ এলিয়ট লিখতে পারতেন না। যেমন শেক্সপিয়ার ঋণী মার্লোর কাছে, চসারের কাছে মার্লো, চসার তাঁরও অগ্রজদের কাছে। কারণ মহত্তমসৃষ্টি তো কখনো এককভাবে জন্ম নেয় না। বহু বছরের সর্বজনীন চিন্তার ফসল। তাঁর কথায়, জেন অস্টেনের উচিত ফ্যানি বার্নির সমাধিতে ফুল দেওয়া, জর্জ এলিয়টের উচিত এলিসা কার্টারের আত্মাকে শ্রদ্ধা জানানো।
এলিসা কার্টার ছিলেন এমন একজন বৃদ্ধা যিনি তাঁর খাটে ঘন্টা বেঁধে রাখতেন ভোরবেলা উঠে গ্রিক ভাষা শেখার জন্যে। আর অ্যাফ্রো বেহন যিনি লন্ডনের ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবেতে ঘুমিয়ে আছেন তাঁকেও সকল লেখিকার উচিত ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো। কারণ, তিনিই প্রথম দেখিয়েছিলেন মেয়েদের লিখে উপার্জন করার পথ। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে এসে লক্ষ্য করলেন মহিলারা প্রায় সকলে উপন্যাস লিখতে শুরু করলেন। অথচ সাহিত্যের ইতিহাস বলে মানুষের আদিম ইচ্ছা হল কবিতা লেখা। চারটি বিখ্যাত নাম তাঁর মাথায় এলো। তিনি মিল খুঁজতে লাগলেন জর্জ এলিয়টের সঙ্গে এমিলি ব্রন্টির, শার্লট ব্রন্টি আর জেন অস্টেনের। কোন শক্তি তাদের উপন্যাস লেখায় বাধ্য করেছিল?
ভার্জিনিয়ার মনে হয়েছিল মধ্যবিত্ত পরিবারে মহিলাদের নিজস্ব একটা ঘর থাকাটা অসম্ভব। আর আলাদা ঘর ছাড়া কবিতা লেখা সম্ভব নয়। মহিলারা পরিবারকে সময় দেওয়ার জন্যে আধ ঘন্টার বেশি সময় পান না। সেই সময়ে মনঃসংযোগ করে গদ্য লেখা সম্ভব হলেও কবিতা নয়। জেন অস্টেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এভাবেই সংসার সামলে নীরবে লিখে গিয়েছেন। কখনো পান্ডুলিপি লুকিয়ে বা চাপা দিয়ে রাখতেন। বারোয়ারি বসার ঘরে বসেই রচনা করে গিয়েছেন সাহিত্য। তাঁর সামনে যে সব চরিত্র ঘোরাফেরা করত তাদেরকেই উপন্যাসের চরিত্রে রূপ দিতেন। এইভাবেই তিনি পুরুষশাসিত সমাজে সমস্তরকম বাধা সমালোচনা অতিক্রম করে লিখেছেন ‘প্রাইজ অ্যান্ড প্রেজুডিস’। সেই সময়ে মহিলারা মহিলাদের মত করেই লিখে গেছেন, পুরুষদের মতো নয়।
ভার্জিনিয়া উলফ সারাজীবন ধরে মহিলাদের হয়ে লিখে গেছেন বহু চিঠি এবং ডায়রি। তাঁর ডায়রিতে বর্ণিত ঘটনাগুলি সেই সময়ের এক বিশ্বস্ত দলিল। পনের বছর বয়েসে তিনি প্রথম ডায়রি লেখেন। আর শেষ লেখাটি লিখেছিলেন মৃত্যুর ঠিক চারদিন আগে অর্থাৎ ২৪ মার্চ। খুব যত্ন করে রঙিন কাগজের মলাটের ভিতরে গুছিয়ে রাখতেন। অতীতচারণা করার সময়ে ডায়রির সাহায্য নিতেন, পরবর্তীতে এই বিষয়ের উপরে বেশ কিছু ছবি এঁকেছিলেন।
এর ভিতর দিয়েই তিনি লন্ডনের একটা কলেজে ইংরাজি ও ইতিহাস পড়ানোর পাশাপাশি দ্য গার্ডিয়ান, দ্য টাইমস লিটারারি সাপ্লিমেন্ট এবং বিভিন্ন প্রকাশনার জন্যে নিবন্ধ, রিভিউ লেখেন সমসাময়িক এবং ধ্রুপদী সাহিত্য বিষয়ে। এই সময়ে তিনি এবং তাঁর স্বামীর কয়েকজন বন্ধু মিলে একটা বৌদ্ধিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলেন। লন্ডনের গর্ডন স্কোয়ারে ১৯০৬ সালে ‘থার্সডে ইভিনিং’ এবং পরে ‘ফ্রাইডে ক্লাব’-এ সাহিত্য, শিল্পকলা, বর্তমান সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা চলত। লেখার পাশাপাশি তিনি সাংবাদিকতাও করতেন।
‘বিটুইন দ্য অ্যাক্টস’ ভার্জিনিয়ার শেষ উপন্যাস। বেশ কিছুদিন ধরে তিনি বিষণ্ণতায় ভুগছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তাঁর বাড়িটা বোমার আঘাতে ধ্বংস হয়ে যায়। প্রচুর মূল্যবান বই, জিনিসপত্রের সঙ্গে তাঁর বেশ কিছু লেখাও পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তবু তিনি এগুলো উদ্ধারের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন এবং অনেক কিছুই বাঁচাতে পেরেছিলেন। অগ্নিদগ্ধ বাড়িটা যেন তাঁর দগ্ধ অতীতকে ফিরিয়ে আনল। এই ঘটনার পর থেকে তিনি মানসিক অবসাদে ভুগতে থাকেন।
জীবনের শেষ প্রান্তে এসে স্বামী লিওনার্ড উলফকে বলতেন তাঁর সমস্ত গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ এমনকি ডায়রিগুলো পুড়িয়ে ফেলতে। যদিও লিওনার্ড খুব যত্নে সেগুলো গুছিয়ে রাখেন। পরে এগুলো নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরির সংগ্রহে গিয়েছিল। কৈশোরে তিনি মানসিক অবসাদের শিকার হয়েছিলেন। অনেক বছর চিকিৎসার পরে স্বাভাবিক হন। তারপরে নানা ঘাত প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে এই জায়গায় এসে পৌঁছেছেন। তাঁর ডায়রি ছিল নানা যন্ত্রণাময় কাহিনিতে ঠাসা। শোক, হতাশা, অবসাদ, যন্ত্রণা, ভয় ইত্যাদি নানা ঘটনা এমনভাবে লিখে গেছেন যা পড়তে পড়তে মনে হয় ভেঙে পড়া জীবন নিয়ে তিনি কিভাবে এতটা পথ পাড়ি দিলেন। আবার এই লেখাগুলোই তাঁকে প্রেরণা জুগিয়েছে। এই ডায়রি তাঁর সময়ের এক মুল্যবান দলিল, ঐতিহাসিক প্রমাণ। প্রেম, জীবন, বন্ধুত্ব, হতাশা, নির্জনতা, মৃত্যু ইত্যাদি নানা বিষয়ের উপরে তিনি আলোকপাত করেছেন।
তাঁর জীবনের উপর দিয়ে যে ঝঞ্ঝা বয়ে গিয়েছে সেই বিষয়গুলো লিখতে গিয়ে বলেছেন, ‘এই ঘূর্ণিঝড়কে শান্ত করার জন্যেই আমি লিখি।’
তিনি এই সময়ে বেশ কয়েকবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রতিবারেই কেউ না কেউ তাঁকে উদ্ধার করেন। হয়তো জীবনের প্রতি ভালোবাসা হারিয়ে ফেলেছিলেন। বুঝতে পেরেছিলেন তিনি পাগল হয়ে যাচ্ছেন। এই যন্ত্রণা তিনি আর নিতে পারছেন না। স্বামী এবং বোনকে বলেওছিলেন, তিনি সবাইকে খুব যন্ত্রণা দিচ্ছেন। তাই কি এমন অবসাদ এবং আত্মহনন!
এক জীবনে তিনি অসংখ্যবার তাঁর প্রিয় মানুষদের মৃত্যু চোখের সামনে দেখেছেন। মা, বাবা, ছোট ভাই তারপরে দীর্ঘদিনের সঙ্গী ডোরা ক্যানিংটনের আত্মহত্যা তাঁকে বিচলিত করেছিল। তাঁর বন্ধুদের হারিয়ে মনে হয়েছিল আর বেঁচে থেকে কী লাভ।
একদিন গায়ে লং কোট চাপিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। চলে আসেন সাসেক্সে ওউজ নদীর ধারে। ওভার কোটের পকেটে ভর্তি করলেন বড় বড় ভারি পাথর দিয়ে। এরপরে নদীতে ঝাঁপ দিলেন। ১৯৫১ সালের ২৮ মার্চ তিনি আত্মহত্যা করেন। কিন্তু তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হল ১৮ এপ্রিল। গোটা শরীর নয়, দেহের কিছু অংশ। এতদিনে দেহের নানা অংশ পচে গলে গেছে। যেটুকু উদ্ধার করা গেছে সেটা নিয়ে এসে সমাধিস্থ করা হল একটা এলম গাছের নিচে। যেখানে ‘দ্য ওয়েভসের’ শেষ কথাগুলো লেখা হল, ‘তোমার বিরুদ্ধে আমি নিজেকে ছুঁড়ে ফেলব, অপ্রতিরোধ্য এবং অতল, হে মৃত্যু।’
মাত্র ৫৯ বছরে শেষ হয়ে গেল এমন সৃষ্টিশীল জীবন। সাহিত্যিক টি এস এলিয়ট ভার্জিনিয়ার শোকবার্তায় লেখেন, ‘ভার্জিনিয়া উলফকে কেন্দ্র করে না থাকলে, এটি নিরাকার বা প্রান্তিক থাকত… ভার্জিনিয়া উলফের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে, সংস্কৃতির একটি সম্পূর্ণ ধরন ভেঙে পড়ে।’
আসলে ভার্জিনিয়া শিক্ষা, গির্জা, চিকিৎসা, আইন ইত্যাদি নানা জায়গায় কাজের জন্যে শিক্ষিত নারীদের প্রবেশাধিকারের সমস্যা নিয়ে কলম ধরেছিলেন। অক্সফোর্ড এবং কেমব্রিজ থেকে নারীদের বহিষ্কারের ফলে তাঁর কলম গর্জে ওঠে। নারী পুরুষের সমতা নিয়েও তিনি লিখে ফেলেন উপন্যাস, ‘মিস্টার অ্যান্ড মিসেস রামসে’। আসলে তিনি শৈশব থেকে দেখেছেন সংসারে এবং বাইরের জগতে বাবা মায়ের কী ভূমিকা ছিল, কীভাবে তারা যাপন করতেন। তাঁর মতামত হল, যাকে তিনি বিয়ে করেছেন, তিনি তারই মতো যদি যোগ্য হবেন তবে সব ব্যাপারে সমান অংশীদার হবেন। বিবাহ, যৌনতা বিষয়ে খোলাখুলি লিখেছিলেন। এই কারণে তাঁকে নানা সমালচনার মুখে পড়তে হয়েছিল।
মৃত্যুর পরে ভার্জিনিয়ার বইয়ের ভিতর থেকে একটা নোট পাওয়া যায়। তাতে লেখা ছিল, স্বামী লিওনার্ডের প্রতি তাঁর গভীর প্রেমের কথা। তিনি স্বামীকে কষ্ট দিচ্ছেন সেটাও লিখে গেছেন। এর জন্যে তিনি খুবই দুঃখিত। তবে তাঁর লেখা শেষ কথাগুলো ছিল, ‘তুমি কি আমার সব লেখা ছিঁড়ে ধ্বংস করে ফেলবে?’
এরপরে কেটে গেছে অনেকগুলো বছর। দশ বছর বাদে ১৯৬২ সালে নাট্যকার এডওয়ার্ড অ্যালবি ভার্জিনিয়ার স্বামী লিওনার্ড উলফের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বলেন, তিনি একটি নাটকের পরিকল্পনা করেছেন। সেখানে ভার্জিনিয়ার নাম উল্লেখ করতে চান। নামটা বলেই দিলেন, ‘হুজ অ্যাফ্রেড অফ ভার্জিনিয়া উলফ?’
কাহিনি শুনে উলফ অবশ্য অনুমতি দিয়েছিলেন। পরে ১৯৬৬ সালে এটি চলচ্চিত্রায়িত হয়েছিল। এই চলচ্চিত্রটি একাদেমি পুরস্কারের জন্যে মনোনীত হয়েছিল। এলিজাবেথ টেলর, রিচার্ড বার্টন, স্যান্ডি ডেনিসের মতো বিখ্যাত ব্যক্তিরা এতে অভিনয় করেন। ২০১৩ সালে জাতীয় চলচ্চিত্র রেজিস্ট্রিতে এটি সংরক্ষণের জন্যে গ্রন্থাগার অফ কংগ্রেস দ্বারা নির্বাচিত হয়েছিল। কারণ হিসাবে বলা হল, এটি ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক এবং নান্দনিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ।
Advertisement