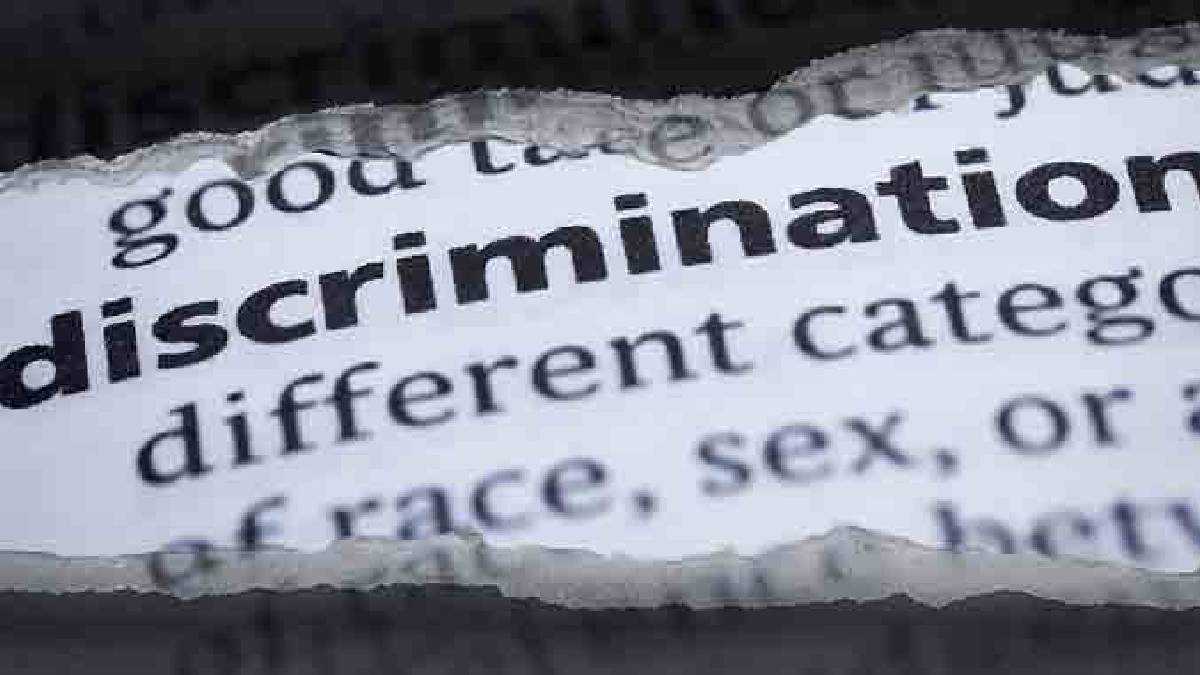শোভনলাল চক্রবর্তী
শিরোনামের কথাগুলি বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আবহে। কথা গুলি মনে পড়ে গেলো আজকের ভারতের এবং বিশ্ব জুড়ে হিংসার উন্মত্ততা দেখে। মুখে যতই ‘রাষ্ট্রবাদী’ হোন, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রতি গৈরিক জাতীয়তাবাদীদের গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে, এমন অভিযোগ কেউ কখনও করেনি। ফলে, সংবিধান যে প্রতিটি নাগরিককে মতপ্রকাশের অধিকার দিয়েছে, এই ‘রাষ্ট্রবাদী’রা সে কথার তোয়াক্কা করেন না। তাঁদের স্থানীয় নেতা অসম দাওয়াই প্রয়োগের হুমকি দিয়েছেন। অবশ্য, শুধু অসম কেন, উত্তরপ্রদেশ থেকে মহারাষ্ট্র, দেশের বহু বিজেপি-শাসিত রাজ্যেই এখন গণতান্ত্রিক বহুস্বরকে দমন করার সেই দাওয়াই সহজলভ্য। পশ্চিমবঙ্গে তাঁরা এখনও শাসনক্ষমতা থেকে বহু দূরে, ফলে আস্ফালনই সার। এই গৈরিক জাতীয়তাবাদীদের মনে করিয়ে দেওয়া দরকার, যে বিষাক্ত পৌরুষ-মণ্ডিত একশৈলিক কল্পনাকে তাঁরা ‘ভারত’ বলে চালাতে চান, দেশটি আসলে সে রকম নয়। সংবিধান দেশের নাগরিককে যে অধিকার দিয়েছে, তা প্রয়োগ করা, এবং তাকে রক্ষা করার কাজটিকে তাঁরা ‘দেশ-বিরোধিতা’ হিসাবে দেখাতে চান বটে— কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁদের রাজনীতিই ভারতের ধারণাটির বিরোধী।কলকাতায় যুদ্ধবিরোধী মিছিলের উপরে বিজেপির যে নেতা-কর্মী-সমর্থকরা চড়াও হলেন, তাঁদের আচরণ অসহনীয় রকম কদর্য না হলে বলা যেত যে, তাঁদের মধ্যে একটা শিশুসুলভ সারল্য রয়েছে। যুদ্ধের বিরোধিতায় মিছিল, তা হলে নিশ্চয়ই এই মিছিলকারীরা ভারতের শৌর্য আর বিক্রমের বিরোধী, অর্থাৎ নির্জলা পাকিস্তানপন্থী— এই ভাবনার মধ্যে কোথায় কোথায় ভুল থাকতে পারে, আর কোথায় বোধহীনতা, মিছিল আটকাতে পোড়া মোবিল হাতে রাস্তায় নামা ‘রাষ্ট্রবাদী’দের সে কথা বোঝার সামর্থ্য নেই। যে নেতা এই কদর্যতার সপক্ষে বাগ্বিস্তার করেছেন, দৃশ্যত তাঁর যুক্তিবোধও অত দূর নাগাল পায় না।
Advertisement
নাগপুরের পাঠশালায় বহুত্ববাদ শেখানোর চল নেই বটে, কিন্তু যিনি এই আক্রমণের সংগঠক, এবং যিনি তার তাত্ত্বিক পৃষ্ঠপোষক, দু’জনের কেউই আদিতে নাগপুরের পাঠশালার পড়ুয়া নন। রাজ্য রাজনীতির স্রোত-প্রতিস্রোত তাঁদের বিজেপির কূলে ভাসিয়ে এনেছে। অবশ্য, নিজের মতের বাইরেও যে কোনও মত থাকতে পারে, এবং সে মতটি ক্ষেত্রবিশেষে অধিকতর গ্রহণযোগ্য হতে পারে, এ কথাটি বুঝতে না পারার অক্ষমতা ভারতের গৈরিক জাতীয়তাবাদীদের একচেটিয়া নয়, দুনিয়া জুড়েই দক্ষিণপন্থার সমর্থকরা কথাটি বুঝতে নারাজ, এবং অপারগ। অতএব, সন্ত্রাসবাদের প্রতি সুগভীর ঘৃণা পোষণ করেও, সেই সন্ত্রাসবাদে মদত দেওয়ার জন্য পাকিস্তানের রাষ্ট্রশক্তির প্রতি সম্পূর্ণ বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও যে কেউ যুদ্ধের বিরোধী হতে পারেন, গৈরিক জাতীয়তাবাদী বীরপুঙ্গবেরা সে কথা বোঝেননি। এবং, নিজেদের না-বোঝা জাহির করতে রাস্তায় নেমেছেন। দুর্ভাগ্য, ইদানীং এই নির্বোধের আস্ফালনই রাজনীতি নামে পরিচিত।মিছিলে হামলা হওয়ার পর কলকাতা পুলিশ মিছিলকারী এবং হামলাকারী, দু’পক্ষকেই আটক করে, এবং পরে দু’পক্ষকেই ছেড়ে দেয়। সমদর্শিতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করার বাসনা ছিল কি? মিছিলকারীদের দাবি অনুসারে, তাঁরা পুলিশের অনুমতি নিয়েই মিছিল করছিলেন। তা যদি হয়, তবে নাগরিকের শান্তিপূর্ণ ভাবে মত প্রকাশের গণতান্ত্রিক অধিকারটিকে রক্ষা করাই পুলিশের একমাত্র কর্তব্য ছিল। হামলাকারীদের প্রতিহত করা প্রয়োজন ছিল। তাঁদেরও মত প্রকাশের অধিকার বিলক্ষণ রয়েছে। যাঁরা যুদ্ধবিরোধী মিছিল করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে যত ক্ষোভ আছে, সব উগরে দেওয়ার গণতান্ত্রিক অধিকার তাঁদেরও রয়েছে। কিন্তু, সেই প্রকাশের ভঙ্গিটিও গণতান্ত্রিক হওয়া অপরিহার্য। পুলিশের কর্তব্য ছিল হামলাকারীদের পান্ডাকে এই কথাগুলি বুঝিয়ে বলা। তার পরিবর্তে পুুলিশ যে ভূমিকা গ্রহণ করল, তাতে স্পষ্ট যে, নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার সম্বন্ধে আইনরক্ষা বাহিনীরও ধারণা বিশেষ স্পষ্ট নয়। এই ব্যর্থতার দায় বহন করবে কে?২০১৯ সালে ১৪ ফেব্রুয়ারি পুলওয়ামা কাণ্ড ঘটার দুই সপ্তাহের মধ্যে কন্যাকুমারীর জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদীর মুখে ধ্বনিত হয়— জাতীয় নিরাপত্তার সরকারি পদক্ষেপ বিষয়ে প্রশ্ন তোলার অর্থ দেশের সরকার তথা শাসকের বিরোধিতা। বলা হয় ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষে ভারতীয় নাগরিকের মুখে ভারত সরকারের সমালোচনা পাকিস্তান কাজে লাগাবে। প্রশ্নধ্বংসী জাতীয়তার প্রচারে ক্রমে ঢাকা পড়ে যায় একটি সত্য যে, জাতীয় সার্বভৌমতা ও সন্ত্রাস-সঙ্কট বিষয়গুলির গুরুত্ব গণতান্ত্রিক দেশের সকল নাগরিকের কাছেই গগনচুম্বী, আর সেই জন্যই তৈরি হতে পারে সংশয়, জিজ্ঞাসা, আপত্তি ও সমালোচনা।
Advertisement
প্রশ্নকারীকে শাসন-কর্তারা কথায় কথায় গ্রেফতার করলে, কিংবা বিচার-কর্তারা প্রশ্নকারীকে চুপ করিয়ে দিলে তাতে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি মান্য হয় না। অথচ ভারত-পাকিস্তান সমস্যা এত গভীর ও ব্যাপক যে আদৌ কোন পথে তার সমাধান কত দূর সম্ভব— তা নিয়ে সকলেই গভীর অজ্ঞানতায়। গত আট দশকে সমাধানের বহু প্রচেষ্টা দেখা গিয়েছে, তার মধ্যে বিশেষ স্মরণীয় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর নামটি, যিনি বহুবিধ সঙ্কটের মধ্যেও দ্বিপাক্ষিক মৈত্রীর গুরুত্ব অনুধাবন করতে ভোলেননি। জাতীয়তাবাদ বা জাতীয়তাবোধ বিষয়টি যে একশৈলিক কিংবা একস্বরবিশিষ্ট হওয়া অসম্ভব, সেই কথাটি বিস্মৃত হওয়াতেই হয়তো জাতীয় স্বার্থের সর্বাধিক ক্ষতি।” ঠিক যেমন ভারতে আছে ভারতীয় অতি-জাতীয়তাবাদীরা, চিনে আছে চিনা অতি-জাতীয়তাবাদীরা। এ এক এমন জাতীয়তাবাদের কাচ (‘লেন্স’) যা বাস্তবকে বিকৃত করে দেখায়। অথচ এই গোত্রের জাতীয়তাবাদের পক্ষে অনেক বেশি পরস্পরসংযুক্ত, পরস্পরনির্ভর হয়ে গিয়েছে আজকের দুনিয়া।” কথাগুলি উচ্চারিত হয়েছিল ১৯৬২ সালে, চিন-ভারত যুদ্ধের প্রেক্ষিতে। বলেছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ— প্রধানমন্ত্রী নেহরুর বিরোধী, পূর্বতন গান্ধীবাদী জাতীয়তাবাদী, কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির নেতা, পরবর্তী কালে কংগ্রেস-বিরোধী জনতা পার্টির মুখ্য ব্যক্তিত্ব হওয়ার সুবাদে যিনি বিজেপির কাছে দেবমহিমান্বিত। চিন-ভারত যুদ্ধের আকস্মিকতা বড় ধাক্কা দিয়েছিল তৎকালীন সরকারপক্ষ বিরোধীপক্ষ সমেত সমগ্র দেশকে। সেই সময়ে ভারতের স্বার্থরক্ষার্থে কী কী পদক্ষেপ করা জরুরি, তার বিস্তারিত আলোচনা-সমেত ‘জে পি’ একটি বক্তৃতা দেন সর্বোদয় আন্দোলনের সভায়। সেখানে তিনি বলেছিলেন বিদেশি শক্তির সঙ্গে ক্ষমতাসঙ্কটের নিরসনে আলোচনা (‘আরবিট্রেশন’) এবং দ্বিপাক্ষিক কথোপকথন (‘বাইল্যাটারাল টকস’) জরুরি। প্রশ্ন তুলেছিলেন, “আর দেয়ার আদার পিসফুল ওয়েজ় অব সেটলিং ডিসপিউটস?” অন্য কোনও পথ কি আছে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে অশান্তি মেটানোর? যুযুধান দুই প্রতিবেশী দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে যাতে ভুল বোঝাবুঝি কমে, সেই লক্ষ্যে ওই বছরের পয়লা মার্চ ‘ফ্রেন্ডশিপ মার্চ’ শুরু করেছিলেন তিনি ও তাঁর সহচারী নেতারা, নয়া দিল্লির মহাত্মা গান্ধী স্মারক মঞ্চ থেকে। কথোপকথনের কূটনীতি দিয়ে সব সঙ্কটের মীমাংসা সম্ভব নয়— যাঁরা এ যুক্তি দিয়েছিলেন, তাঁদের দিকে তীক্ষ্ণ প্রতিপ্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছিলেন জয়প্রকাশ: তবে কি জাতীয়তাবাদের স্লোগানে ও শত্রুতা প্রচারেই সমস্যার সমাধান নিশ্চিত? সামরিক ক্ষমতার উপর অত্যধিক নির্ভরতা দিয়ে কত দূর এগোনো যায়, গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন তিনি।
লক্ষণীয়, একটি অপ্রত্যাশিত কঠিন যুদ্ধের আবহেও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী নেতাদের মধ্যে তর্কবিতর্কর পরিবেশটি মোটেই ক্ষুণ্ণ হয়নি। প্রশ্ন, তর্ক বা সমালোচনার পরিবেশ ক্ষুণ্ণ হয়নি ২০০৮ সালের মুম্বই হামলার পরও। সে কথা জানেন তৎকালীন ভারতের বিরোধী রাজনীতিকরা, যাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান নরেন্দ্র মোদী স্বয়ং। হামলার মাত্র দুই দিন পর, ২৮ নভেম্বর, ইউপিএ সরকারের বিরুদ্ধে মুম্বইয়ে বিজেপির সমাবেশ আহূত হয়, সন্ত্রাসের প্রেক্ষিতে জনক্ষোভকে কাজে লাগানোর জন্য সরকারবিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে গুজরাতের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী দ্রুত মুম্বই চলে আসেন। দিল্লি ও রাজস্থানে ভোট তখন দোরগোড়ায়, ২৯ নভেম্বর ও ৪ ডিসেম্বর। বিজেপির নির্বাচনী প্রচারে মুম্বই হামলার ছবি ব্যবহৃত হয়, ‘সন্ত্রাস হানা: দুর্বল সরকার, অনিচ্ছুক ও অক্ষম’ মর্মে। জাতীয় সঙ্কটের সময় এ ভাবে কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করা উচিত কি না, সেই সংশয় সত্ত্বেও সমালোচনা ও আক্রমণের পরিবেশ তখনকার ভারতে বিরাজমান ছিল।এত দিনে সেই ভারত দূর দিগন্তে অস্তমিত।
১৯০৬ সালে শান্তিনিকেতনে এক অভিভাষণে বেদনাহত রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, “এ কি হল ধর্মের চেহারা? এই মোহযুদ্ধ ধর্মবিভীষিকার চেয়ে সোজাসুজি নাস্তিকতা অনেক ভালো৷ ঈশ্বরদ্রোহী পাশবিকতাকে ধর্মের নামাবলী পরালে যে কী বীভৎস হয়ে ওঠে তা চোখ খুলে একটু দেখলেই বেশ বোঝা যায়৷” কিংবা ২৬ আগস্ট, ১৯১৪ শান্তিনিকেতনে উপাসনাকালে রবীন্দ্রনাথ বললেন, “আমাদের প্রার্থনা সকল সময়ে সত্য হয় না, অনেক সময় মুখের কথা হয়; কারণ, চারিদিকে অসত্যের দ্বারা পরিবৃত হয়ে থাকি বলে আমাদের বাণীতে সত্যের তেজ পৌঁছয় না। কিন্তু, ইতিহাসের মধ্যে, জীবনের মধ্যে, এমন এক-একটি দিন আসে যখন সমস্ত মিথ্যা এক মুহূর্তে দগ্ধ হয়ে গিয়ে এমনি একটি আলোক জেগে ওঠে যার সামনে সত্যকে অস্বীকার করবার উপায় থাকবে না। তখনই এই কথাটি বার বার জাগ্রত হয়, বিশ্বানি দেব সবিতার দুরিতানি পরাসুব। হে দেব, হে পিতা, বিশ্বপাপ মার্জনা করো।…আজ এই যে যুদ্ধের আগুন জ্বলছে এর ভিতরে সমস্ত মানুষের প্রার্থনাই কেঁদে উঠেছে: বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব। বিশ্বপাপ মার্জনা করো। আজ যে রক্তস্রোত প্রবাহিত হয়েছে সে যেন ব্যর্থ না হয়। রক্তের বন্যায় যেন পুঞ্জীভূত পাপ ভাসিয়ে নিয়ে যায়। যখনই পৃথিবীর পাপ স্তূপাকার হয়ে উঠে তখনই তো তাঁর মার্জনার দিন আসে। আজ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যে দহনযজ্ঞ হচ্ছে তার রুদ্র আলোকে এই প্রার্থনা সত্য হোক: বিশ্বানি দূরিতানি পরাসুব। আমাদের প্রত্যেকের জীবনের মধ্যে আজ এই প্রার্থনা সত্য হয়ে উঠুক।” আমরা নিশ্চিত এই প্রার্থনা মিথ্যা হতে পারে না।
Advertisement