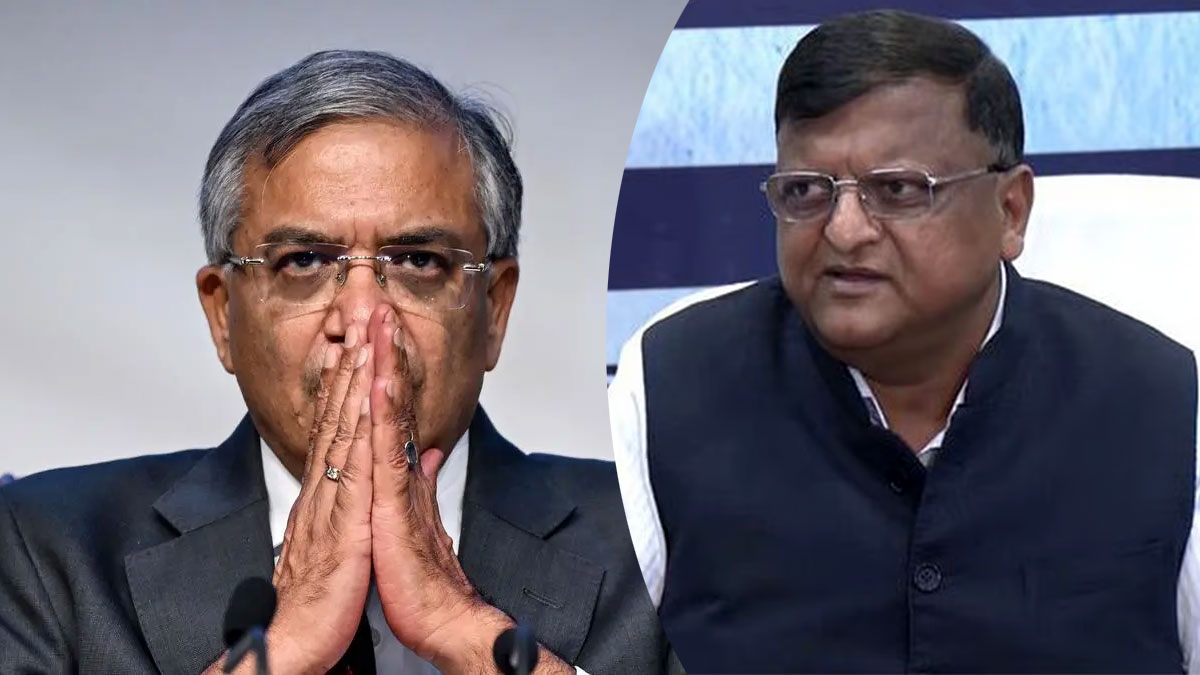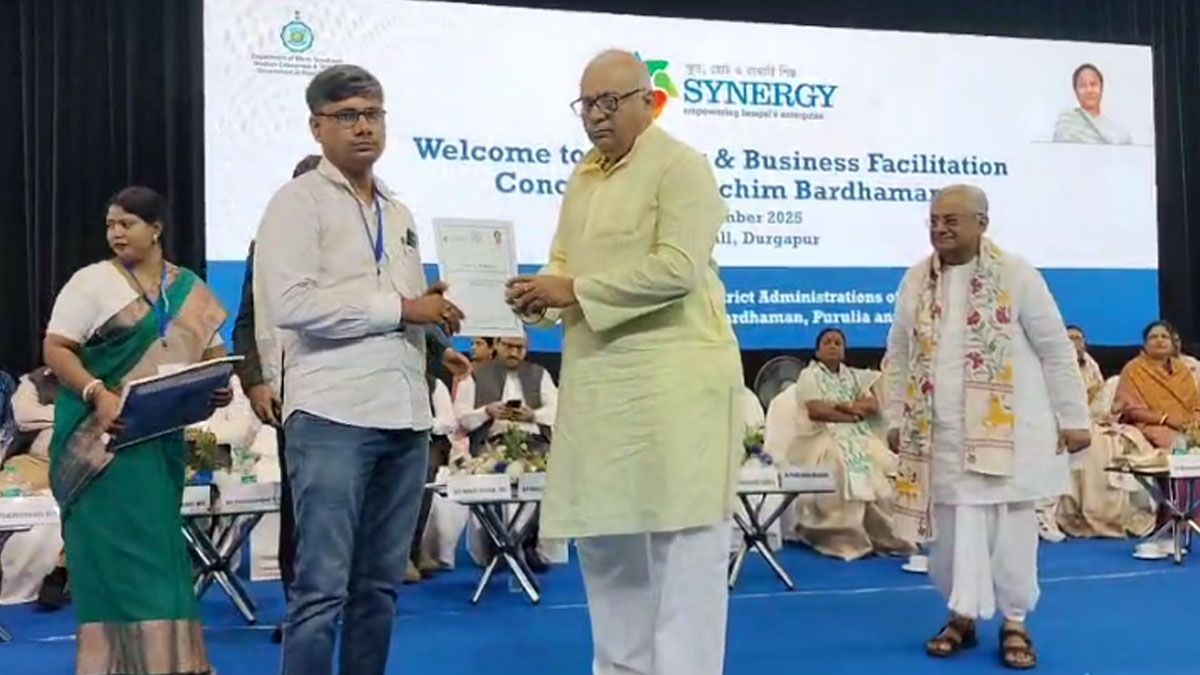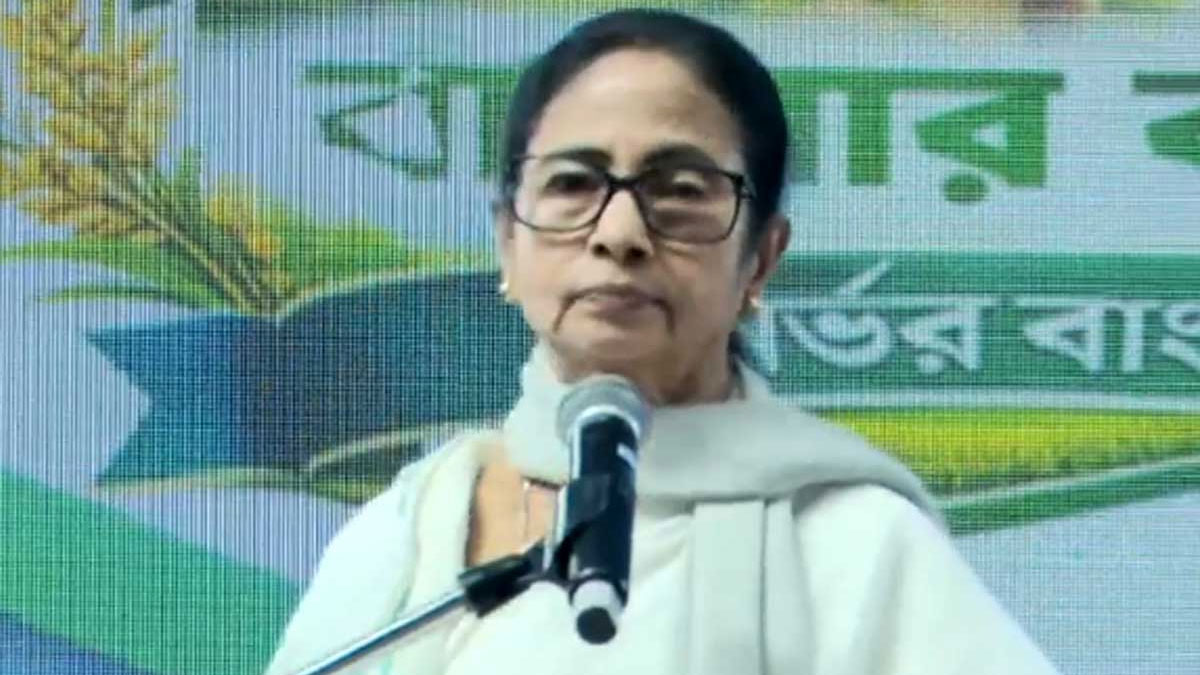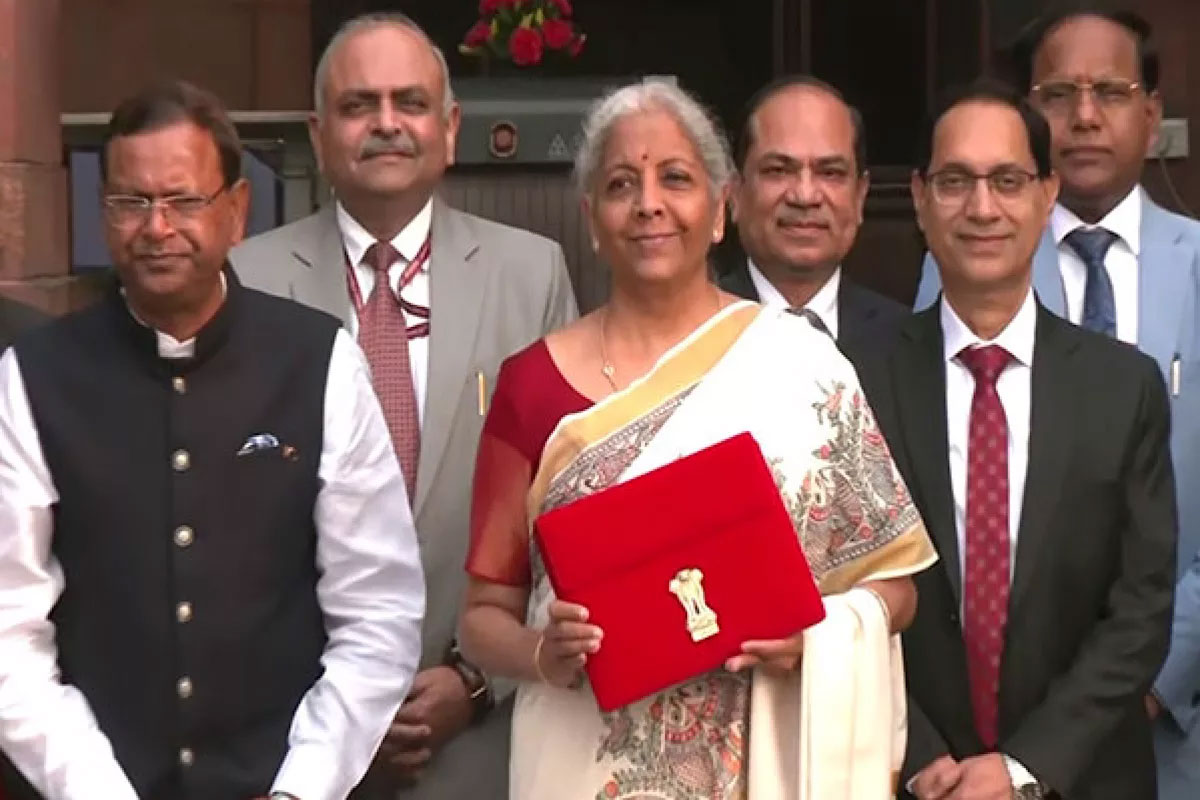চন্দন দাস
‘মাজরামুড়া’ – পুরুলিয়া জেলার কাশীপুর ব্লকের একটি সুন্দর ছোট গ্রাম। ১৮০টা সাঁওতাল পরিবার এবং ৬৫টি চিত্রকর পরিবার নিয়ে এই গ্রাম তৈরি। হাওড়া থেকে আদ্রা জংশনের তিনটে স্টেশন আগে ‘ইন্দ্রবিল’ একটা সুন্দর ছোট স্টেশন। এই ইন্দ্রবিল স্টেশন থেকে মাজরামুড়া গ্রামের দূরত্ব ৫ কিলোমিটার। টোটো করে এই গ্রামে আসতে মিনিট ১৫ সময় লাগে। এই গ্রামের ৪৬টি পরিবার পট চিত্র আঁকেন। এই চিত্রকর পরিবারগুলো গরীব হলেও ভালো মনের মানুষ। ভীষণ অতিথিপরায়ণ। অভাব এদের চিত্রকলা কে হার মানাতে পারেনি, নতুন নতুন পটচিত্র এদের ভাবনায় বাস্তবায়িত হয়। এই গ্রামের একজন সুপরিচিত শিল্পী ক্ষেমানন্দ চিত্রকরের মুখেই শুনলাম, “আমার দাদু শ্রীনাথ চিত্রকর এবং আমার বাবা লালমোহন চিত্রকর পটশিল্পী ছিলেন, এনাদের পটচিত্র ছোটবেলা থেকেই দেখে এসেছি এবং কাজ শিখেছি, এটা আমাদের বংশপরম্পরায় চলে আসছে” – সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে এই শিল্পকে আঁকড়ে ধরেই এরা বেঁচে আছেন। শক্তিকাপুর চিত্রকর, বাউল চিত্রকর, হেনাধন চিত্রকর, সুভাষ চিত্রকর, মানিক চিত্রকরের মতন বেশ কিছু পটশিল্পীর সাথে আলাপ হয়ে ভীষণ ভালো লেগেছে। অতীব চমৎকার ব্যবহার এবং হাতের কাজও বেশ উঁচু মানের এবং নিখুঁত। যে কাগজে পটচিত্র আঁকা হয় সেই কাগজটার পেছন দিকে আঠা দিয়ে সুতির কাপড় মাপ মতন লাগানো হয়। এতে কাগজটা বেশ শক্ত-পোক্ত হয়। পটচিত্রের রং-গুলো একেবারেই প্রাকৃতিক। বিভিন্ন গাছের পাতা ও ফুল এবং নানান পাথর থেকে প্রাকৃতিক রঙের নির্যাস বের করে রঙে বাবলা কিংবা তেঁতুলের আঠা মেশানো হয়।
Advertisement
যেমন সিমপাতা থেকে সবুজ, পুঁই বীজ থেকে লাল, কাঁচা হলুদ থেকে হলুদ রঙ, অপরাজিতা ফুল থেকে নীল রঙ, সেগুন পাতা থেকে লাল রঙ, গেরু পাথর থেকে খয়েরি রঙ, কনক পাথর থেকে সাদা রঙ, লণ্ঠনের কালি থেকে কালো রঙ নিয়ে চিত্র অঙ্কন করা হয়। বাঁশের সরু কঞ্চি এবং ছাগলের লেজের থেকে লোম নিয়ে তুলি বানানো হয়। সম্পূর্ণটাই প্রাকৃতিক। রঙগুলো টেকসই বহু বছর পর্যন্ত ভালো থাকে। বর্তমানে পাঞ্জাবী ও জামাতে অ্যাক্রেলিক রঙ ব্যবহার করা হয় পটচিত্র আঁকতে। মাটির ভার কিংবা প্লাস্টিকের ছোট ছোট কৌটোতে রঙ বানানো হয়।
Advertisement
মাজরামুড়ার পটচিত্র
এই মাজরামুড়ার পটচিত্রে আদিবাসীদের জীবনযাত্রা এবং জন্মবৃত্তান্ত ভীষণভাবে গুরুত্ব পায়। দেশ-বিদেশের বহু মানুষ এদের এই আদিবাসী পটগুলো পছন্দ করেন এবং কিনে নিয়ে যান। এছাড়াও রামলীলা, মদনমোহন পট, দশ অবতার পট, রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী, কৃষ্ণলীলা, দাতা-কর্ণ পট, মনসামঙ্গল কাহিনীর পটগুলোও সুন্দর। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের ফুল, পাখি, সুন্দর সুন্দর নকশার ছবিও পটে ফুটে ওঠে। আবার বাঁশের পেনদানি ও ফুলদানিতেও সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকা। এগুলোর চাহিদা বেশ ভালো। এই মাজরামুড়া গ্রামে বাংলা নাটক ডট কম্-এর সহযোগিতায় প্রতি বছর অক্টোবর মাসের শেষের দিকে পটচিত্র মেলা হয়। শিল্পীরা নিজেদের তৈরি পটচিত্র প্রদর্শিত করেন। ঝুমুর গানের তালে নাচ এবং সাঁওতাল নাচও তখন বিশেষ আকর্ষণ হয়ে ওঠে গ্রামের মানুষের। এই বছর (২০২৪), ২৫ – ২৭ অক্টোবর তিন দিন এই পটচিত্র মেলা হয়েছে। যদিও প্রাকৃতিক দুর্যোগে অনেকটাই ক্ষতি হয়েছে। এই সময় বহু মানুষ এই মেলা দেখতে আসেন এবং পটচিত্র কিনে নিয়েও যান। এই মেলাতেই আলাপ হল ষাটোর্ধ্ব শিল্পী বাউল চিত্রকর এবং শক্তিকাপুর চিত্রকরের সাথে। বাউল চিত্রকর ১২ বছর বয়স থেকেই পটচিত্র আঁকছেন। দিল্লিতেও পট শিল্প নিয়ে কর্মশালা করেছেন। গ্রামের অনেককেই পট আঁকা শিখিয়েছেন। ক্ষেমানন্দ চিত্রকরের মুখেই শোনা গেল আদিবাসী বা সাঁওতার জীবন বৃত্তান্তের কাহিনীগুলো কীভাবে পটে উঠে আসে। মানুষ সৃষ্টির ইতিহাসে আদিবাসীদের যে গল্প সেগুলো খন্ড খন্ড চিত্রে পটে ভেসে ওঠে। এগুলোর চাহিদা বেশ ভালো। মানুষ এসে এই পটচিত্রগুলিই খোঁজেন।
কাল্পনিক গল্পটা হল এমনই যে, যখন পৃথিবী সৃষ্টি হয়নি তখন সর্বত্র জলমগ্ন ছিল। এমনই এক অবস্থায় দুটো গাই স্বর্গ থেকে নীচে নেমে এল। ওই জলের ওপর গাই দুটো দাঁড়িয়ে ছিল। প্রচুর পরিমাণ জল গাই দুটো পান করতে করতে মুখ থেকে ফেনা উঠল। সেই ফেনা ভাসতে ভাসতে দুটো পোকার সৃষ্টি হল। সেই পোকা দুটো জলে ভাসতে ভাসতে দেখছে একটা হাঁস ও একটা হাঁসির জন্ম হল। এরা দুটো ডিম পাড়ল। সেই ডিম থেকে একটা মেয়ে এবং একটা ছেলের জন্ম হল। জন্ম নেবার পর শিব, আদিবাসীদের ভাষায় মারাঙ্গবুড়ো দেখলেন পৃথিবীতে মানুষ জন্মে গেল। এই মানুষদের কোথায় রাখা যায়? শিব এই চিন্তাতে ব্রহ্মাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, এই পৃথিবী আমরা বানাব।
ব্রহ্মা বললেন তাহলে পঞ্চনাগ, কচ্ছপ, কেঁচো, বোয়াল মাছকে ডাকা হোক। কচ্ছপকে বলা হল তোমাকে পৃথিবী ধরে রাখতে হবে। কচ্ছপ বলল, আমি একা এই কঠিন কাজ করতে পারব না। তখনই পঞ্চনাগ নীচে রইল তার ওপর কচ্ছপ থাকল। ব্রহ্মা শিবকে বলল কচ্ছপ নড়ানড়ি করবে। এই কারণে কচ্ছপের তিনটে পায়ে শেকল বাঁধা হল। এবার মাটি তোলার দায়িত্ব পড়ল কেঁচোর ওপর। কেঁচো জলের নীচ থেকে মাটি তুলে কচ্ছপের পিঠে রাখল। পদ্মের ডাঁটা বেয়ে কেঁচো এই মাটি বহন করে আনত। এই পৃথিবী সৃষ্টি হল। যে মানুষ দুটো প্রথম সৃষ্টি হয়ে ছিল তাদের নাম পিলচুহারাম এবং পিলচুবুড়ি। এরাই পৃথিবীর প্রথম মানুষ। এরা নেশার তাগিদে বনে বনে ঘুরে গাছের ঔষধ খুঁজতে লাগল। এবার ঔষধ না পেয়ে চিৎকার শুরু করল। তখন রানু নামের এক গাছের ঔষধ চিৎকার শুনে বলল – “এখানে এসো আমি এখানে আছি।” এরা সেই গাছের শেকড় তুলে বাড়িতে নিয়ে আসল। সেটাকে কোটাকুটি করে বেঁটে হারিয়া তৈরি হল। এবার হারিয়া খেয়ে প্রথমে মজা তারপর শুরু হয় ভীষণ ঝগড়া পিলচুহারাম ও পিলচুবুড়ি নামের মানুষ দুটোর সাথে। সেই সময় মারাঙ্গবুড়ো (শিব) এখানে এসে হাজির হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, “মারপিট করছ কেন?” ছেলে মেয়ে ভাগ করে দিল দেবতা শিব। পিলচুহারাম সাতটি ছেলে পেল এবং পিলচুবুড়ি সাতটি মেয়ে পেল। ছেলেরা শিকারে গেল, মেয়েরা শাক, লতাপাতা গাছ থেকে তুলে আনত। ছোটবেলাতেই ছেলেমেয়েদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।
একদিন বহু বছর বাদে ছেলেরা হরিণ শিকার করে মেয়েদের পাশ দিয়ে চলে যায়। তখন মেয়েরা গান গাইতে লাগল – “বারো মাসের জিলবাবু পারমিনা” আদিবাসীদের ভাষায় জিল অর্থ মাংস এবং পারমিনা অর্থ পার হয়ে গেল। এই গান শুনে ছেলেরা এসে কথাবার্তা বলে মেয়েদের সাথে বিয়ে করল। এটা হল ভাই-বোনের মধ্যে বিয়ে। গ্রামের মানুষ এটা মানল না। আদিবাসীদের ভাষায় কুলিদূরুপ অর্থাৎ গ্রামের সভা বসল। বিচার হল এই বিয়ে নিয়ে। কাজের কাজ কিছুই হল না।
মাজরামুড়ার শিল্পীদের কিছু পটচিত্র
তাহলে কী হবে? তখন সিদ্ধান্ত হল পদ্ম পাতায় বসে বিচার করতে হবে। সেই বিচার মানা হবে। তখন থেকে তাদের বিচার হল। আদিবাসী ভাষায় ‘পারিসে-পারিসে’ – অর্থাৎ একই জাতিতে বিয়ে চলবে না। অর্থাৎ না জেনে এই যে ভাইবোনের বিয়ে হল, এমন আর করা চলবে না। এরপর থেকে স্বাভাবিকভাবে গ্রামের জীবনযাত্রা শুরু হল। মন্দির তৈরি হয়ে পুজো শুরু হল। বাজার তৈরি, স্কুল তৈরি করে লেখাপড়া শেখা, বিচার ব্যবস্থা স্থাপিত হওয়া অর্থাৎ আস্তে আস্তে এই পৃথিবীতে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা শুরু হল। এইসব ঘটনা পটে খন্ড খন্ড চিত্রে উঠে আসে এই মাজরামুড়ার পট শিল্পীদের চিত্রে।
আবার পিলচুহারামের মৃত্যুর পর পিলচুবুড়ি কাঁদতে শুরু করে। তখন ব্রহ্মা একজনকে ডেকে বলেন, “তুমি শালপাতাতে পিলচুহারামের ছবি উনানের আগুনের শিখার কালো রঙে আঁকো।” উনান কাঠ কয়লা দিয়ে জ্বালানো হত। তখন সেই চিত্রকর বলে পিলচুহারাম মারা গেছে ও ভূত হয়ে গেছে, ওর কথা চিন্তা করে কাঁদবে না। তার নাম করে চক্ষু দান কর। পিলচুবুড়ি বলল, দানে কী কী লাগে? তখন দানে দিতে হল – সোনার থালা, টাকা, গাই। এইসব দিয়ে এই চিত্রকরকে বিদায় করা হল। এই চিত্রকর বংশধররাই আস্তে আস্তে চিত্রকর হয়ে উঠল। আজও চিত্রকররা মানুষ মারা গেলে সেই মৃত ব্যক্তির বাড়িতে গিয়ে চক্ষু দান করেন এবং তাদের আত্মীয়-স্বজনদের কাছে গিয়ে মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তি কামনা করেন। বিনিময়ে টাকা পয়সা, চাল, সবজি মেলে। এই চিত্রকররা আজও এই প্রথা মেনে চলেছেন। এই ঘটনাগুলোও পটশিল্পীদের আঁকায় ফুটে ওঠে।
এই পটচিত্রগুলো বিশ্ব বাংলার হাত ধরে অনেক জায়গায় চলে যায়। আবার জার্মান, গোয়া, বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন জায়গায় এই পটের চাহিদা আছে। আদিবাসী পট ১৫ থেকে ১৬ ফুটের একটার দাম পাঁচ থেকে ছয় হাজার টাকা। আবার দৈর্ঘ্য-প্রস্থে তিন ফুটের পটগুলোর দাম ২০০০ টাকা থেকে ৩০০০ টাকা। আবার দৈর্ঘ্য প্রস্থে এক ফুটের পটগুলোর দাম ৩০০ টাকা। পেনদানি ও ফুলদানিগুলো ৩০০ থেকে ৫০০ টাকার মধ্যে প্রতি পিস। আজও বয়স্ক পটশিল্পীরা আদিবাসীদের পটগুলো নিয়ে বিভিন্ন গ্রামে যেমন গৌরাঙ্গডি, বাঁশতাডি, পচাগড়া, কুমোডি, ঘোড়া কাটা, দুয়ার মৌলী, আদ্রাসহ বিভিন্ন গ্রামের বাড়ি বাড়ি গিয়ে গান গেয়ে পটের বিষয়বস্তু বোঝান। মানুষরা শোনেন, বিনিময়ে মেলে চাল, ডাল, সবজি। এছাড়াও বিভিন্ন মেলায় এই শিল্পীরা পটচিত্র নিয়ে বসেন। কিছু মঞ্জুষা, খাদিতেও এদের পট শিল্প শোভা পায়। খুব যে একটা ভালো বিক্রি বাট্টা হয় সেটা দেখলাম না। এরা ভীষণ গরীব। এক এক সময় কিছু বিক্রি হয় না, তখন খড়ের ছাউনিও মাটির ঘরে বসবাসকারী এই পটশিল্পীদের খুবই অসুবিধে হয় ছেলেমেয়েদের নিয়ে এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বাজারে সংসার চালাতে। এমন গরীব শিল্পীদের কথা কিন্তু আরও যত্ন সহকারে ভাবা উচিত।
Advertisement