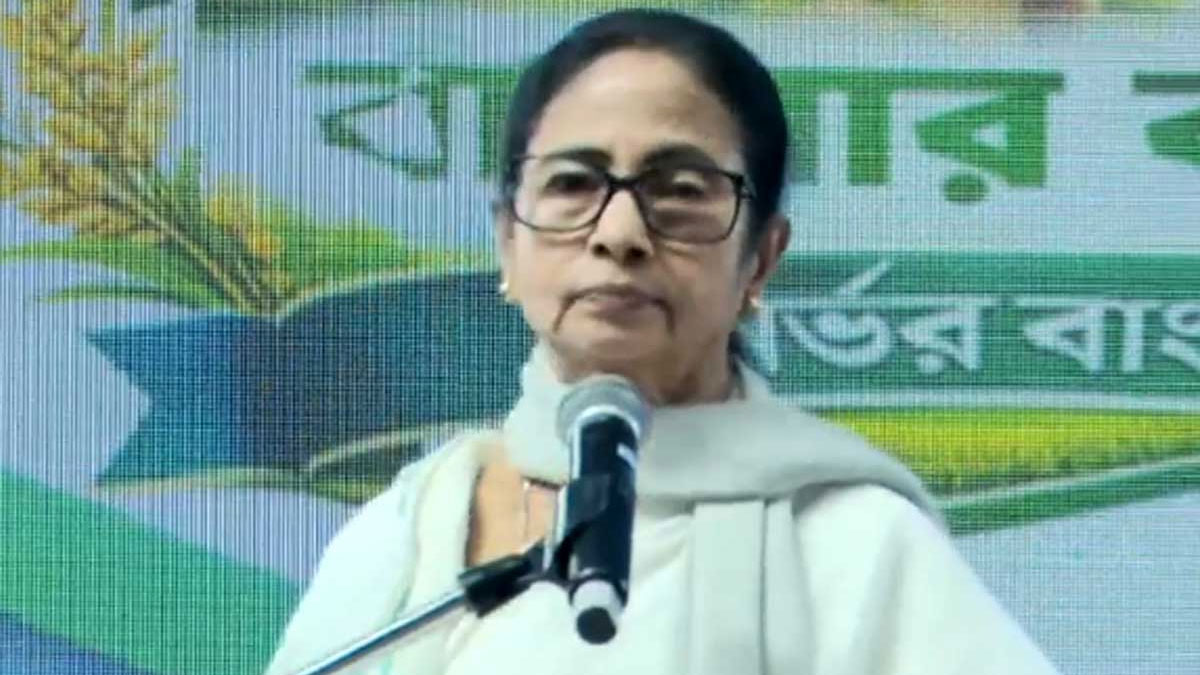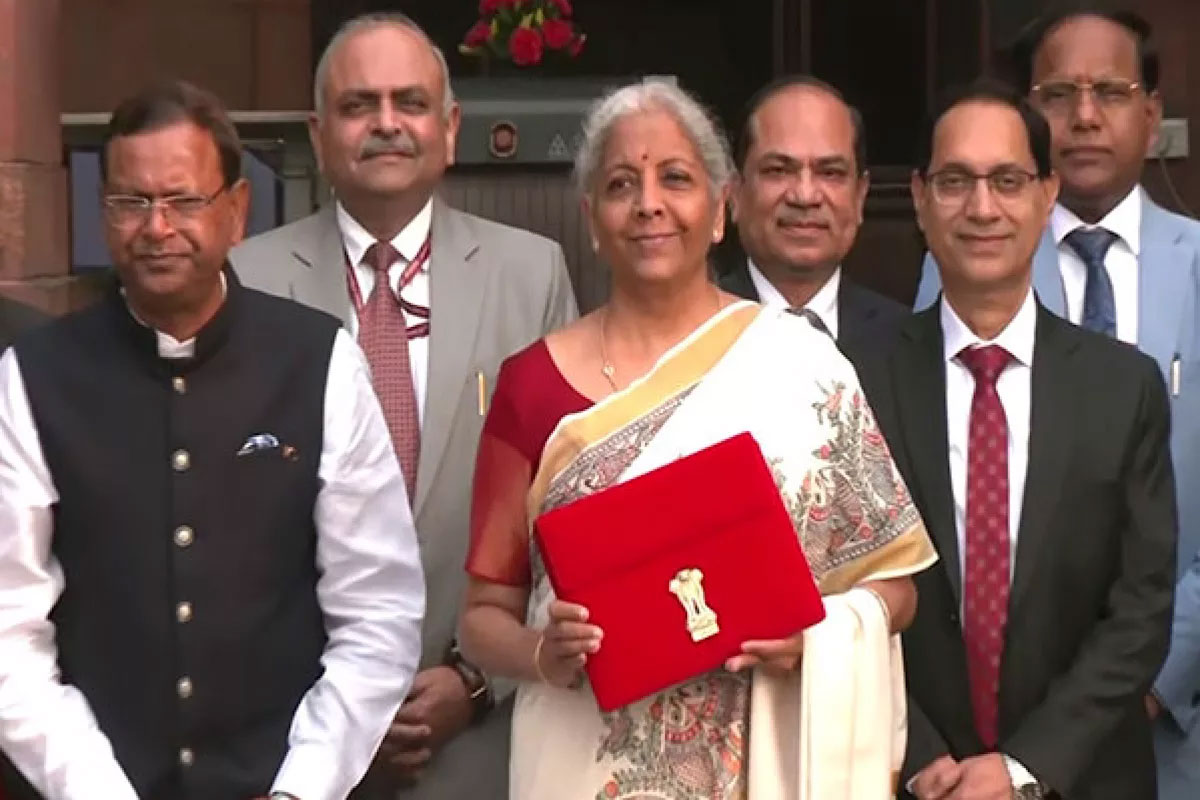মৃণালেন্দু দাশ
শ্রীচৈতন্যদেব ৫৪০ বছর আগে নবদ্বীপে ১৪০৭ শকাব্দের শুভ ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথির সন্ধ্যায় জন্মগ্রহন করেন পিতা জগন্নাথ মিশ্র মাতা শচীদেবীর কোল আলো করে। তখন চন্দ্রগ্রহণ হচ্ছে। চারিদিকে হরি হরি ধ্বনি। প্রতিবেশীগণ নবজাতক শিশুকে নানা উপহার দিয়ে আর্শীবাদ করেন। শ্রীচৈতন্য মিশ্র পরিবারের ছোট পুত্র বিশ্বম্ভর। বড় বিশ্বরূপ যৌবনেই সন্ন্যাস নিয়ে গৃহত্যাগী হন। দুই ভাইয়ের পূর্বে পরপর আট মেয়ে জন্ম নিয়েই মারা যান। সেই নিমাই ২৪ বৎসর বয়সে মাঘ মাসের পূর্ণিমা রাতে ঘুমে অচৈতন্য স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে ঘরে রেখে ভোর রাতে বেরিয়ে যান। সেই রাতে নিমাই স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে নিজহস্তে এত যত্নে সুন্দর করে সাজিয়েছিলেন যে মনেই হবে না নিমাই গৃহত্যাগ করবেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার নিজেকে পতিপ্রেমে খুব সোহাগিনী মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, নারী জীবন তার সার্থক। নিমাইয়ের প্রথমা স্ত্রী ছিলেন লক্ষ্মীপ্রিয়া। তাঁর সাপের কামড়ের মৃত্যু ঘটে। এদিকে নিমাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন মাতা শচীদেবীক চুপিচুপি প্রণাম করে গৃহত্যাগ করলেন। কাটোয়ার ভারতী গোঁসাইয়ের কাছে সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষা নেন। এরপর তাঁর সুন্দর কুঞ্চিত কেশরাশি মধু নাপিত কেটে ফেললে গঙ্গার তীরে উপস্থিত শতশত নিমাই অনুরক্ত ভক্তবৃন্দ হাউহাউ করে ক্রন্দন শুরু করেন। সে এক মর্মন্তুদ দৃশ্য। অথচ নিমাই ছিলেন নবদ্বীপের সেরা পণ্ডিত। তাঁর টোলে ছিল শত শত ছাত্র।
Advertisement
এসময় তিনি পিতা জগন্নাথ মিশ্রর তর্পণ করতে গয়াধামে যান। সেখানে তিনি ঈশ্বরপুরীর কাছে গুরুমন্ত্র নিয়ে নবদ্বীপে ফিরে আসেন। তখন থেকেই তাঁর অন্যরূপ। নিত্যানন্দ এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। শুরু হলো নদীয়া জুড়ে খোল করতাল নিয়ে হরিনাম সংকীর্তন। সেই দলে যুক্ত গৌরহরির একান্ত প্রিয় শ্রীবাস, অদ্বৈত আচার্য পার্ষদগণ। সন্ন্যাস নিয়েই নিমাই মায়ের আদেশে নীলাচলে চললেন। নীলাচল হলো উড়িষ্যার শ্রীক্ষেত্র পুরীধাম। সঙ্গে শতশত ভক্ত পার্ষদগণ। কারণ, সেসময় হেঁটেই পুরীতে জগন্নাথ দর্শন ও রথযাত্রা দেখতে যেতে হত। এই যাত্রাপথ ছিল খুব র্দুগম কষ্টসাধ্য তেমনি তস্কর দস্যুদের অর্তকিত হানায় ভীত সন্ত্রস্ত থাকতে হয় পুণ্যার্থীদের। তাই সবাই সদলবলে শুকনো খাবার চিড়ে খই মুড়ি গুড় বাতাসা ছাতু চাল ডাল সঙ্গে নিয়ে যেত। পথে নিরাপদ স্থান দেখে শুকনো গাছের ডালে আগুন জ্বেলে ক্ষুধা নিবৃত্তির সংস্থান করতে হতো। এই যাত্রাপথ ছিল প্রায় তিনমাসের মতো। বৈশাখ থেকে আষাঢ় মাস পর্যন্ত। এখনকার মতো সহজ সুলভ রেলপথ ছিল না। সন্ধে সাতটায় হাওড়া থেকে পুরী এক্সপ্রেস বা জগন্নাথ ধরে পরদিন সকাল নয়টার মধ্যে পুরী স্টেশনে পৌঁছে যাওয়া যায়। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার যাত্রাপথ। ভারতীয় রেলের ইতিহাস তো দেড়শো বছরের কিছু বেশি।
Advertisement
পুরীর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা অত্যন্ত সুপ্রাচীন ও সুবিখ্যাত৷ স্কন্দপুরাণের উৎকল খণ্ডে উল্লেখ আছে যে, উড়িষ্যার শঙ্খক্ষেত্র হল পুরী৷ এই শঙ্খক্ষেত্রের পশ্চিম কোণে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব মন্দির৷ পুরীর মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদেব তিনি নিজে যেমন লোকপ্রিয়, তাঁর রথযাত্রাও তেমনি জনমোহিনী। লক্ষ লক্ষ জনসংযোগপূর্ণ মহাআড়ম্বরময় ধর্মীয় সাংস্কৃতিক উৎসব৷ যেখানে উঁচুনিচু ধনীদরিদ্র জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে এই পৃথিবীর সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ একসঙ্গে সসম্মানে রথযাত্রায় অংশগ্রহণ করতে পারেন৷ মহাপ্রভু শ্রীশ্রীজগন্নাথ সত্যি সত্যিই যে জগতের নাথ৷ এ তার উজ্জ্বল প্রমাণ৷ শ্রীচৈতন্য যথার্থই জগন্নাথাস্টকং শ্লোকে বলেছেন— ‘জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে’৷ আসলে প্রভু শ্রীজগন্নাথ তিনি মানুষ বড় ভালোবাসেন৷ তাই তিনি উৎসবপ্রিয় লোকদেবতা৷ আর তাই তাঁর দুই বাহু বাড়িয়ে রেখেছেন সর্বদাই৷ চণ্ডাল অচণ্ডালে নির্দ্বিধায় কোল দেবেন বলে, যার জীবন্ত রূপবিগ্রহ দেখি এই কলিতে শ্রীচৈতন্যের মধ্যে৷ এ-এক আশ্চর্য সংযোগ৷
পুরীর শ্রীমন্দিরে দারুব্রহ্ম বিগ্রহত্রয় হলেন জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রা দেবী৷ এঁরা সম্পর্কে ভাইবোন৷ এই তিন দারুবিগ্রহই মন্দিরের গর্ভগৃহে একাসনে উপবিষ্ট আছেন৷ মাঝখানে দেবী সুভদ্রা, ভগ্নি সুভদ্রার ডানপাশে আছেন দাদা বলভদ্র আর বামপাশে আছেন স্বয়ং ভগবান শ্রীজগন্নাথদেব৷ এঁরা তিনজন আলাদা আলাদা হলেও আসলে এঁরা এক এবং অভিন্ন৷ পুরীর মন্দিরসহ পৃথিবীর যেখানে যত শ্রীজগন্নাথ মন্দির আছে সর্বত্রই এইভাবে দারুব্রহ্ম বিগ্রহত্রয় অবস্থান করেন, মধ্যে সুভদ্রা তাঁর ডানে বলভদ্র ও বামে প্রভু জগন্নাথ৷
এছাড়া প্রভু জগন্নাথের ডান পাশে আছেন তাঁর সুদর্শন আর আছেন নীলমাধব সোনার লক্ষ্মী ও রূপার সরস্বতী৷ স্কন্দপুরাণের বিষ্ণুখণ্ডে বলা আছে, ‘এক এব জগন্নাথস্ত্রিধা তত্র স্থিতো দ্বিজাঃ৷’ অর্থাৎ একই জগন্নাথ তিন রূপে বিভক্ত হয়ে সেই স্থানে বিরাজমান৷ সুবিশাল শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের প্রবেশদ্বার চারটি৷ পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ এই চারদিকেই রয়েছে মন্দিরের প্রবেশদ্বার৷ মন্দির প্রাঙ্গণে রয়েছে অসংখ্য দেবদেবীর ছোট বড় মন্দির৷ প্রতিটি মন্দিরের আলাদা আলাদা সেবায়েত পাণ্ডাগণ বংশ পরম্পরায় শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সেবাকাজের সঙ্গে যুক্ত৷ আর মন্দির প্রাঙ্গণে রয়েছে আনন্দবাজার৷ এই আনন্দবাজারেই বিক্রি হয় প্রভু জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ সহ অন্যান্য বিভিন্ন রকমের প্রসাদ৷ শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে বছরের প্রতিটি দিনই কোনো না কোনো উৎসব লেগে রয়েছে, যা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা হয়৷ সেইসঙ্গে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের ২১৪ ফুট ৮ ইঞ্চি সুউচ্চ চূড়ায় প্রতিদিন সন্ধ্যার পূর্বাহ্নে গরুড় সেবক উপরে উঠে নূতন নূতন ছোট বড় পতাকা ধ্বজা বাঁধেন৷ তাঁর নাম ‘পতিত পাবন বানা৷’
আরও আশ্চর্যের ব্যাপার, প্রতি একাদশী তিথিতে সেই চূড়ার নীচে একফুট লম্বা চওড়া মাটির প্রদীপে আড়াই কেজি ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালানো হয়, যা ঝড় জলেও নেবে না৷ একে ‘মহাদীপ’ বলে৷ পুরীর শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে একাদশীর উপবাস নিষিদ্ধ৷ কারণ শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে একটি ছোট্ট মন্দির একাদশীকে তালাবন্ধ করে রাখা হয়েছে৷ পুরীধাম হল ভোগক্ষেত্র৷ তাই শ্রীজগন্নাথকে প্রতিদিন ছাপান্ন ধরনের ভোগ নিবেদন করা হয়৷ প্রভু জগন্নাথদেবের রান্নাঘর সুবিশাল ১০০ ফুট বাই ১৫০ ফুট আর ৪৫০টি উনুন এবং রন্ধন প্রণালীও আশ্চর্যরকম কৌতুহলোদ্দীপক৷ এই রান্নাঘরে প্রতিটি ৪ ফুট বাই আড়াই ফুট উনুনে মাটির হাঁড়ির উপর পরপর ৯টি মাটির হাঁড়ি বসিয়ে রান্না করা হয়৷ হাঁড়িগুলির মুখ নারকেল কোরা দিয়ে বন্ধ করা থাকে৷ সর্বপ্রথম সবার উপরের হাঁড়িটিই আগে রান্না হয়ে যায় এবং তারপরে পরপর নীচের হাঁড়িগুলির রান্না সমাপ্ত হয়৷ এ বড় আশ্চর্য রান্নাঘর এবং তাঁর রান্নার কৃৎকৌশল আর এইসব রান্নার সমস্ত সবজি চাল ডাল সবই জগন্নাথদেবের নিজস্ব জমির উৎপাদিত ফসল৷ বাইরের কোনো কেনা জিনিস দিয়ে প্রভুর ভোগরান্না হয় না৷
স্কন্দপুরাণের উৎকল খণ্ড থেকে আমরা জানতে পারি মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদেব স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে বলেন, ‘প্রতিবছর আষাঢ় মাসের শুক্লা তিথিতে বলরাম সুভদ্রা সহ আমাকে রথে করে সহস্র অশ্বমেধ যঞ্জের বেদী মূলে অর্থাৎ গুন্ডিচা মন্দিরে নিয়ে যাবে৷’ সেই থেকেই পুরীতে শুরু হয় রথযাত্রা মহোৎসব৷ নীলাচল থেকে গুণ্ডিচা মন্দিরে যাওয়া এবং নয়দিন পর আবার জগন্নাথবিগ্রহত্রয়ের নীলাচলে মন্দিরে ফিরে আসা৷ এই রথযাত্রা উৎসবের জন্য কাষ্ঠদ্বারা নির্মিত তিনটি আলাদা আলাদা রথ প্রতিবছর নির্মাণ করা হয় সেই রথযাত্রার শুরুর সময় থেকেই একটি বিশেষ নিয়মে৷ যা আজ অবধি একচুলও নড়চড় হয়নি৷ রথযাত্রার এই তিনটি রথ নির্মাণের জন্য প্রতিবছর মাঘ মাসের বসন্ত পঞ্চমীর দিন থেকে কাঠ সংগ্রহের কাজ শুরু হয়৷ তারপর বৈশাখ মাসের অক্ষয় তৃতীয়ার অমৃতযোগে রথের নির্মাণকার্য শুরু হয়৷ জগন্নাথ মন্দিরের কাছের রাজপথের ধারে রথ নির্মাণের কাজটি চলতে থাকে৷ এই রথনির্মাণ কাজটি সম্পন্ন হয় জগন্নাথ-বিগ্রহত্রয়ের চক্ষু দান পর্বে৷ এরজন্য বংশপরম্পরায় নির্দিষ্ট সূত্রধর, শিল্পী ও কারিগর আছেন, যাঁরা নিষ্ঠাসহকারে প্রভুর এই রথনির্মাণ কাজটি সুসম্পন্ন করেন৷
এবারে বলি, প্রভু শ্রীজগন্নাথদেবের রথের নাম ‘নন্দীঘোষ’৷ ৪৫ফুট উঁচু এই রথ নির্মাণে ৮৩২টি কাঠের টুকরো লাগে৷ এর ১৬টি চাকা৷ ষোড়শ কলার প্রতীক৷ চাকার ব্যাস ৭ফুট, পাটাতন ৩৫বর্গফুট৷ নৃসিংহদেব হলেন রথের রক্ষক, সারথি মাতলি৷ রথের ৪টি সাদা ঘোড়া হল রেচিকা, মোচিকা, সূক্ষ্মা আর অমৃতা৷ এরপর বলি, শ্রীবলভদ্র দেবের রথের নাম হল ‘তালধ্বজ’৷ ৪৭ফুট উঁচু এই রথ নির্মাণে লেগেছে ৭৬৩টি কাঠের টুকরো৷ এ বছর ১৫টি কাঠের টুকরো কম লাগবে। কারণ গতবছর ১৫টি কাঠের টুকরো বেশি ছিল। এই প্রথম এমন ঘটল। এর আগে কোনদিন এমন হয়নি। চাকার ব্যাস ৬ফূট৷ পাটাতন ৩৪ বর্গফুঠ৷ ১৪টি চাকা রথের চতুর্দশ মন্বন্তর বা ব্রহ্মার আয়ুস্কাল বা চতুর্দশ ভুবনেরও প্রতীক এই তালধ্বজ রথ৷ এর রক্ষক হলেন শেষাবতার৷
সারথি সুদ্যুম্ন৷ কৃষ্ণবর্ণ ৪টি ঘোড়ার নাম যথাক্রমে স্থিরা, স্থিতি, ধৃতি এবং সিদ্ধা৷ এরপর বলি, শ্রীসুভদ্রা দেবীর রথের নাম হল ‘দর্পদলন’৷ ৪৩ ফুট এই রথের নির্মাণে লাগে ৫৯৩টি কাঠের টুকরো৷ চাকার ব্যাস ৬ ফুট৷ পাটাতন ৩৩ বর্গফুট৷ সুভদ্রা দেবীর রথের ১২টি চাকার অর্থ বারোমাসের কার্যচক্র৷ বনদুর্গা হলেন রথের রক্ষক৷ এর ৪টি অশ্বের নাম হল অধর্ম, অঞ্জান, অপরাজিতা ও জ্যোতিনী৷ এরপর এই তিনটি রথকেই নানা বর্ণের মনোহর বস্ত্র দিয়ে সাজানো ও রথের চূড়ায় বিচিত্র রঙের পতাকা দিয়ে সুন্দর করে সাজানো হয়৷ যজ্ঞ শেষে রথত্রয়ের প্রধান পাণ্ডাগণ নন্দীঘোষ রথে হনুমান, তালধ্বজ রথে নৃসিংহ ও দর্পদলন রথে পদ্মফুল রথের শীর্ষে বসান৷ পুরীর রাজা সোনার ঝাঁটা দিয়ে রথের সামনে ঝাড়ু দেওয়ার পর রথে উপবিষ্ট বিগ্রহত্রয় সহ অন্যান্য দেববিগ্রহদের পূজা ও ভোগ নিবেদন করা হয়।
রথযাত্রার প্রাক্কালে গোপালভোগের পরিবর্তে ষোড়শ উপাচারে উৎকৃষ্ট অন্নব্যঞ্জন ভোগ, খিচুড়ি ও টাকুয়া নামের বিশেষ ধরনের মিষ্টান্ন ভোগ নিবেদন করা হয়৷ সঙ্গে চন্দন, সুগন্ধ পুষ্প ও প্রদীপ সহ নানা মাঙ্গলিক অর্পণ করা হলে, দয়িতাপতি পাণ্ডার নির্দেশে সুদর্শনকে বন্ধন মুক্ত করলেই রথের পাহান্ডি বিজয় যাত্রা শুরু হয়৷ এরপর একে একে জাতিধর্মনির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ নরনারী প্রথমে বলভদ্রদেব, সুভদ্রাদেবী ও শেষে জগন্নাথদেবের রথের রশিতে টান দিয়ে রথযাত্রার শুভ সূচনা করেন৷
এই রথযাত্রা বিভন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পরে। লক্ষ লক্ষ মানুষের টানাটানিতে কিছুতেই রথ একচুলও নড়ানো যায় না। এখানে অনেক ঘটনার মধ্যে শুধু মুসলমান কবি সালবেগের কথা উল্লেখ করি। সালবেগ মুসলমান বলে মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ। কিন্ত প্রভু জগন্নাথদেব তিনি নিজেই তো রথযাত্রায় বেরিয়েছেন জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকলকে রথের রশি টান দেওয়ার অছিলায় কাছে টেনে নিতে। সালবেগ দাঁড়িয়ে আছে বড়দাণ্ডর কাছে। প্রভু জগন্নাথকে দর্শন করবেন আর গান শোনাবেন। রথ সেখানে আসতেই দাঁড়িয়ে পড়ে। প্রথমে বলভদ্র পরে সুভদ্রা দেবী আর শেষে জগন্নাথ দেবের রথ একঘন্টা স্তব্ধ হয়ে যায়। সালবেগ জগন্নাথকে ভাববিহ্বল কন্ঠে গান শোনান। সালবেগের প্রভুকে দর্শন ও গান শোনানো হলে রথ আপনিই চলতে শুরু করে। জগন্নাথদেব ও তাঁর রথযাত্রা নিয়ে এমন অজস্র ঘটনা আছে, যা বলে শেষ করা যাবে না। আজও ঘটে চলেছে জগন্নাথদেব ও রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে অলৌকিক সব ঘটনা।
Advertisement